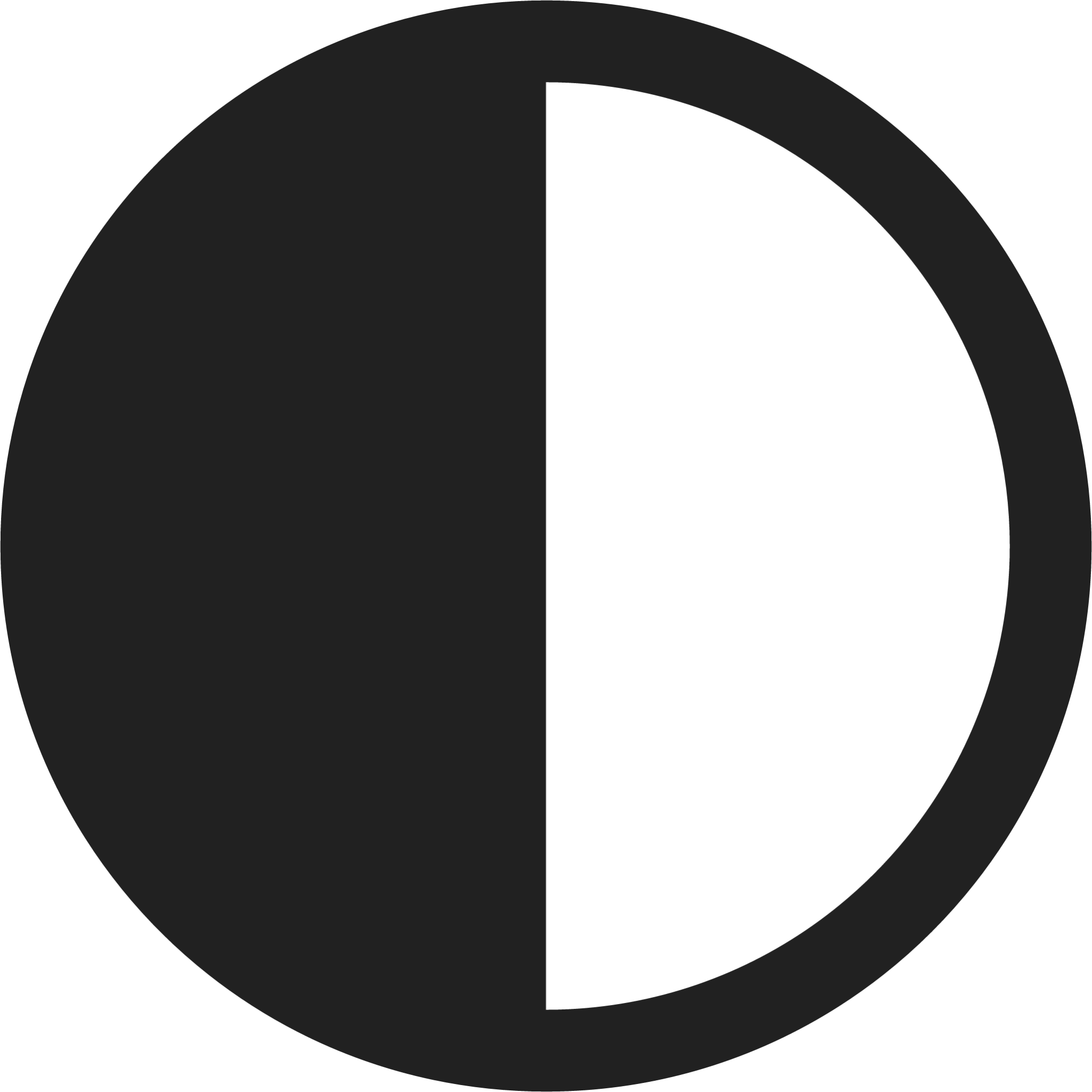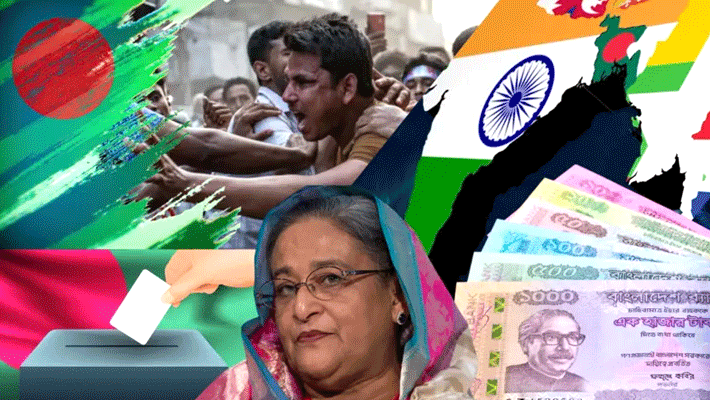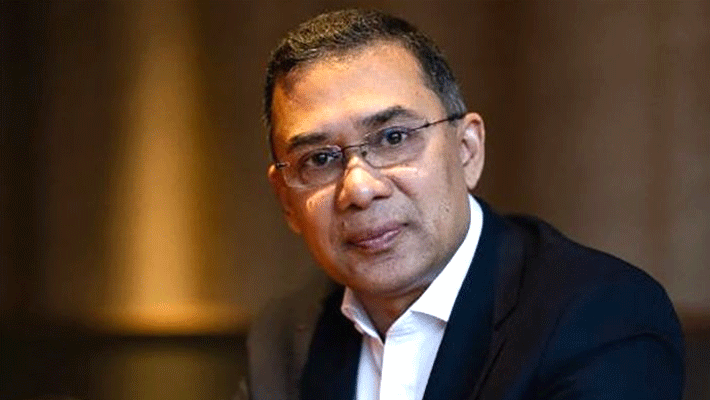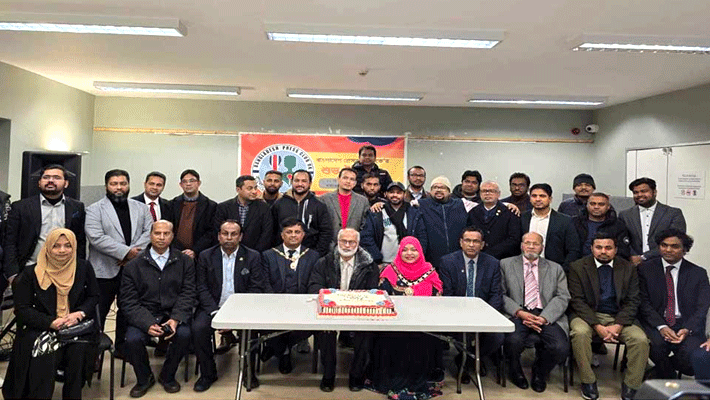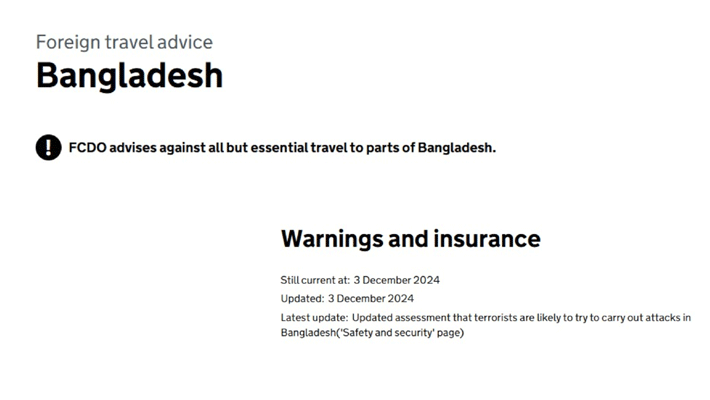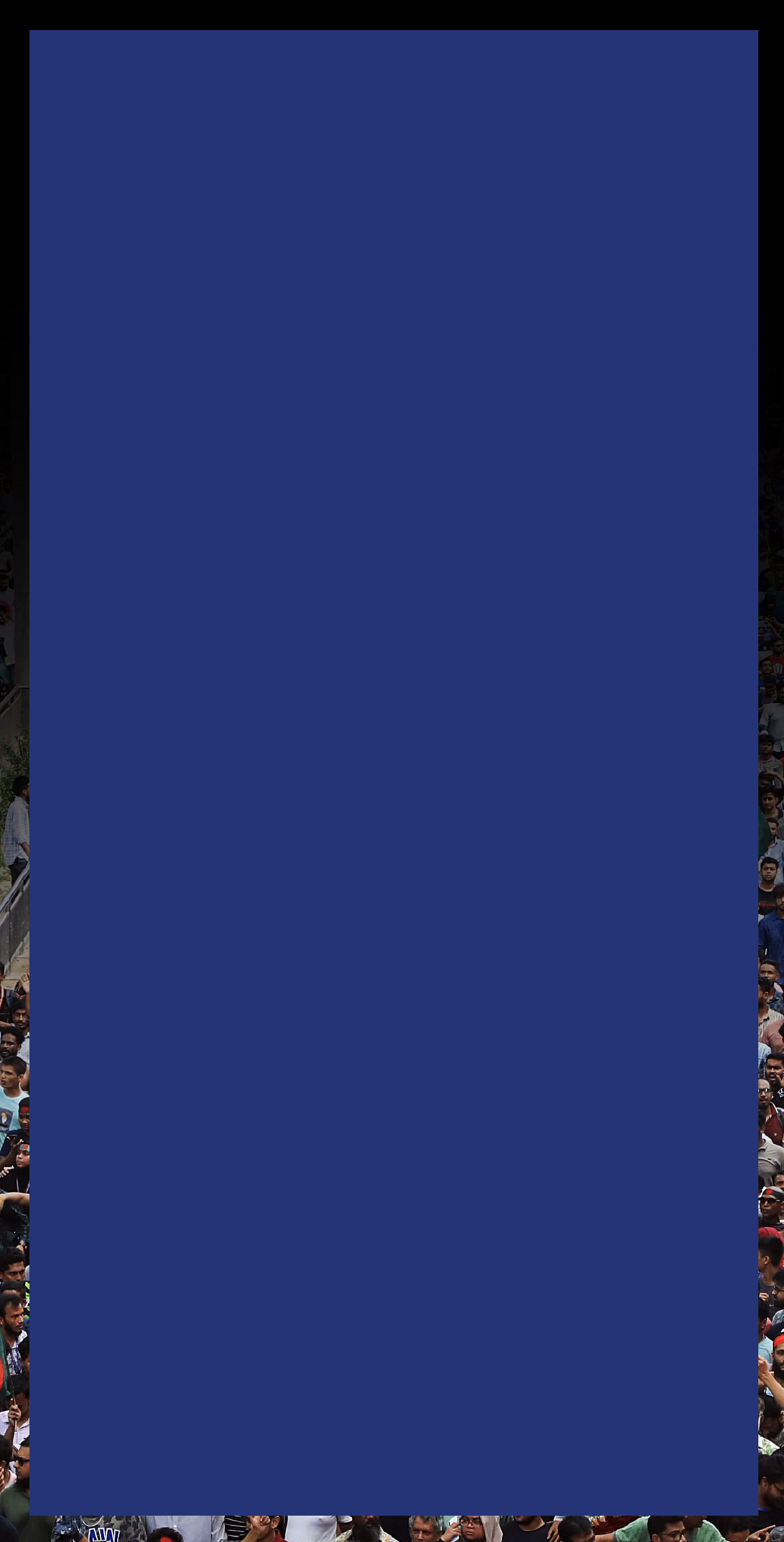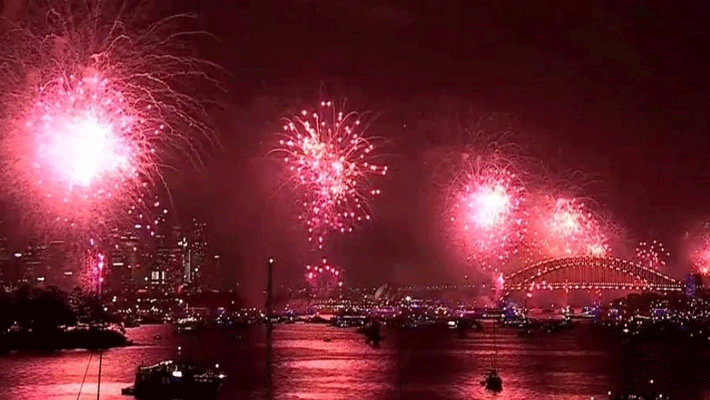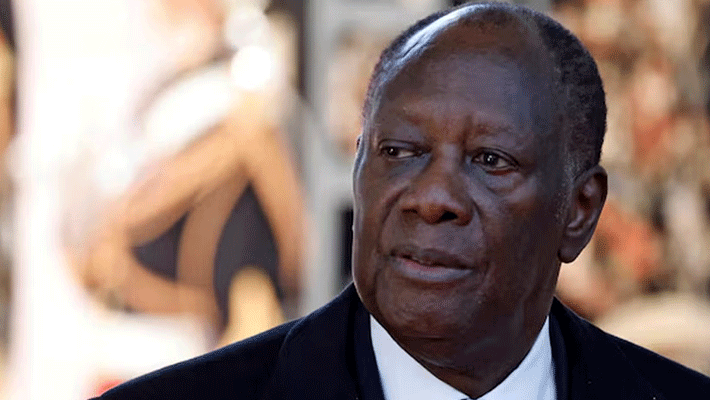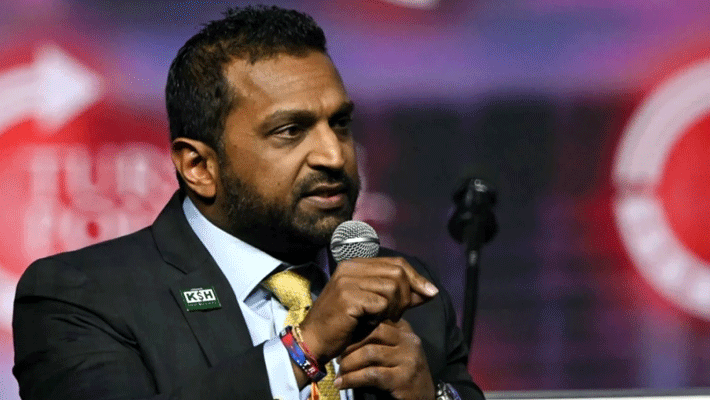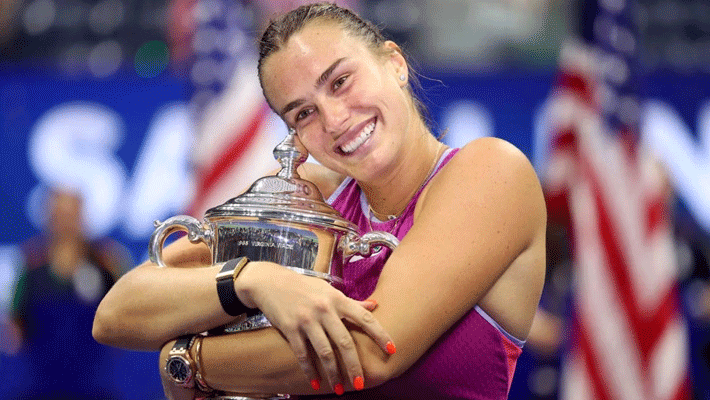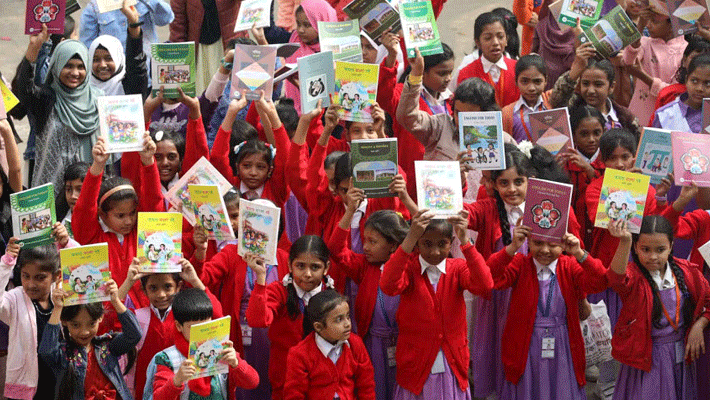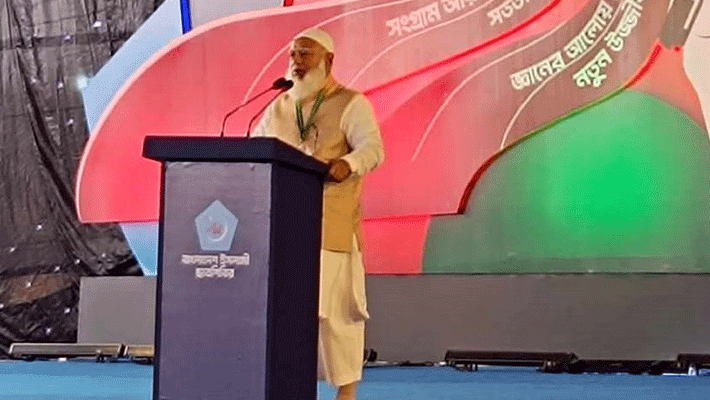যুক্তরাজ্য
যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইউকে’র যাত্রা শুরু
যুক্তরাজ্যে প্রবাসী গণমাধ্যম কর্মীদের নিয়ে বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইউকে নামে নতুন একটি সংগঠনের যাত্রা শুরু হয়েছে।
মঙ্গলবার (৩১ ডিসেম্বর) পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস পার্কের কমিউনিটি হলে কেক কেটে এর শুভ উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতির সাবেক উপদেষ্টা, বাংলাদেশ ওয়ার্ডওয়াইল্ডের প্রধান সম্পাদক ও ক্লাবের চীফ পেট্রোন মোখলেসুর রহমান চৌধুরী। এ সময় ক্লাবের ওয়েবসাইটও উন্মোচন করেন তিনি।
অনুষ্ঠানে লন্ডন নিউহ্যাম কাউন্সিলের চেয়ার ও কাউন্সিল রহিমা রহমান, এনফিল্ড কাউন্সিলের মেয়র আমিরুল ইসলাম, টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি মেয়র মতিন উজ জামান, টাওয়ার হেমলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার আহবাব হোসেন, কাউন্সিলর মজিবুর রহমান, সাপ্তাহিক জনমত পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মুসলেহ উদ্দিন, সেন্টার ফর ডেমোক্রেসি এন্ড গুড গভর্নেন্সের চেয়ারম্যান সোয়ালেহীন করীম চৌধুরী, বেস্ট চারিটির চেয়ারম্যান ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এডভোকেট আব্দুল হালিম হাওলাদার, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মোয়াজ্জেম হোসেন সোহরাব, ব্যারিস্টার ও সলিসিটর মাহাবুবুর রহমান, চার্টার্ড একাউটেন্ট মো. কায়কোবাদ, কমনওয়েলথ সলিসিটর লিমিটেডের প্রিন্সিপাল ব্যারিস্টার মুফতি নাফিস, একাউটেন্ট অ্যান্ড ট্যাক্স এডভাইজর এমডি এমএ খান, লন্ডন লায়ন্স স্পোর্টস ক্লাবের প্রেসিডেন্ট এনামুল হক, ক্লাব ফাউন্ডার জুবায়ের আহমেদসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আজমীর হাসান কনকের উপস্থাপনায় ক্লাব মেম্বার আব্দুল বাসিত, মাহবুব তোহা, সোহেল সাদ, কামরুল আই রাসেল, আশরাফুর রহমান, জাহাঙ্গীর হোসেন, আবু বকর সিদ্দিক, শাকিল আহমেদ সোহাগ, সোহেল আহমেদ পাপ্পু, শাহ শরীফ উদ্দিন, এমকে জিলানী, মনির উদ্দিন, জাহান চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।
অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে শাকির হোসাইনকে আহ্বায়ক ও জুনায়েত রিয়াজকে সদস্য সচিব করে ৩১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।
হারিয়ে যাওয়ার ৫২ বছর পর যুক্তরাজ্যে খোঁজ মিলল নারীর
বহু বছরের পুরোনো একটি ছবি, দাগ পড়ে অনেকটাই আবছা হয়ে গেছে, ছবির মানুষটির চেহারা তেমন একটা বোঝা যায় না। সেই ছবি দিয়েই নিখোঁজ সংবাদ প্রকাশ করে ৫২ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া এক নারীর সন্ধান পেয়েছে পুলিশ।
ওই নারীর নাম শিলা ফক্স। এখন তাঁর বয়স ৬৮ বছর। ১৯৭২ সালে কভেন্ট্রি থেকে তিনি নিখোঁজ হন। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর।
সে সময় তিনি বাবা-মায়ের সঙ্গে বসবাস করতেন। এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস পুলিশ। কর্মকর্তারা বলেছেন, ওই নারীর বিষয়ে সব সময়ই তাঁরা খোঁজখবর রেখেছিলেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, তিনি হয়তো নিজের এলাকা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছেন।
গত রোববার ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস পুলিশ ফক্সকে খুঁজে পেতে সাহায্য করার জন্য নতুন করে আবেদন করে। পুলিশের ওয়েবসাইটে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফক্সের একটি ছবি দিয়ে তাঁর সন্ধান পেতে সাহায্যের আবেদন করা হয়। ছবিটি ফক্স যে সময় নিখোঁজ হয়েছিলেন, তার কাছাকাছি সময়ে তোলা।
আবেদনটি পোস্ট করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সাড়া মেলে। সাধারণ মানুষদের মধ্যে কয়েকজন ফক্সের তথ্য নিয়ে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গতকাল বুধবার পুলিশ কর্মকর্তারা ফক্স বেঁচে থাকার এবং সুস্থ থাকার খবর নিশ্চিত করেন। তাঁরা বলেন, ফক্স ইংল্যান্ডেরই অন্য একটি প্রান্তে বসবাস করছেন।
পুলিশের একজন মুখপাত্র বলেছেন, ‘আমরা আনন্দের সঙ্গে ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস পুলিশের সবচেয়ে পুরোনো নিখোঁজ তদন্তগুলোর একটির সমাপ্তি ঘোষণা করছি।’
দীর্ঘ সময় ধরে সমাধান করতে না পারা মামলা নিয়ে তদন্তকারী দলের সদস্য ডিএস জেন শ বলেছেন, ‘আমরা যেসব প্রমাণ পেয়েছিলাম, তার প্রতিটি ধরে ধরে অনুসন্ধান করে শেষ পর্যন্ত শিলার একটি ছবি জোগাড় করতে সক্ষম হই। নিখোঁজ হওয়া প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের একটি গল্প থাকে। তাঁদের সঙ্গে কী ঘটেছে, সেটা জানার অধিকার তাঁদের পরিবার এবং স্বজনদের রয়েছে। তাদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়ার অধিকারও।’
বাংলাদেশ
হাসিনা সরকারের সব বিদ্যুৎ-জ্বালানি চুক্তি জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি বিএনপির
শেখ হাসিনা সরকারের আমলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে যেসব চুক্তি হয়েছে, সেগুলো জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।
আজ বৃহস্পতিবার গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু এ দাবি জানান।
'গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ আমলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ লুটপাট ও পাচার' শীর্ষক বিশ্লেষণ তুলে ধরতে এই সংবাদ সম্মেলন ডাকেন বিএনপি মহাসচিব।
বিগত সরকারের আমলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে দুর্নীতি-অনিয়মের চিত্র তুলে ধরেন চার দলীয় জোট সরকারের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী টুকু।
তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ সরকার বিদ্যুৎখাতে যে ম্যাজিক দেখাতে চেয়েছিল, ম্যাজিক করতে গিয়ে বাংলাদেশের মানুষের পকেট কেটে নিয়ে গেছে। আপনারা প্রত্যেকে বিদ্যুতে বিল পরিশোধ করেন, সবাই ভুক্তভোগী। আসলে তারা এটা একটা ব্যবসার খাত বানিয়ে ছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, এই খাত থেকে কুইক মানি বানানো যায় কোনো হিসাব না দিয়ে। কারণ বিদ্যুৎ তো "হাওয়া", এটা দেখা যায় না।'
তিনি আরও বলেন, 'ক্যাপাসিটি চার্জ। এই ক্যাপাসিটি চার্জে কোন মেশিনে কত ক্যাপাসিটি? কে এটা আইডেন্টিফাই করেছে এবং সেই মেশিনগুলোর এফিসিয়েন্সি কি? এগুলো কেউ বিশ্লেষণ করেও না, দেখেও না। এই ক্যাপাসিটি চার্জের নামে তারা ১৫ বছরে অনেক টাকা নিয়ে গেছে—প্রায় এক লাখ কোটি টাকা।'
টুকু বলেন, 'আমি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে দাবি জানাই, বিদ্যুৎখাতের প্রত্যেকটা চুক্তি প্রকাশ করুন। তারা তো কোনো পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুল মানেনি। আইন করে নিয়মনীতি বন্ধ করে দিয়ে ইচ্ছামতো ক্লোজ টেন্ডারে এসব চুক্তি করেছে। জনগণের অধিকার আছে এসব বিষয় জানার।'
'উই মাস্ট সি দ্যা কন্ট্রাক্ট। তারা কীভাবে কন্ট্রাক্টগুলো করেছে, এটা পাবলিক হওয়া উচিত। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রথম কাজ হলো জনগণের সামনে এই কন্ট্রাক্টগুলো উন্মুক্ত করে দেওয়া,' যোগ করেন তিনি।
বিদ্যুৎখাতের দুর্নীতি-লুটপাট
দুর্নীতির পরিসংখ্যান তুলে ধরে টুকু বলেন, 'বিদ্যুৎখাতে ১৫ বছরে মোট খরচ হয়েছে ২ হাজার ৮৩০ কোটি মার্কিন ডলার। বর্তমান বিনিময় হারে সেটা ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা। ক্যাপাসিটি চার্জের নামে লুটপাট হয়েছে প্রায় এক লাখ কোটি টাকা।'
তিনি বলেন, '২০০৮-০৯ অর্থবছরে ১ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা, ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৫ হাজার কোটি টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮ হাজার ৯০০ কোটি টাকা এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৭ হাজার ১৫৫ কোটি টাকা ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়েছে। তার অর্থ হলো, বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো চলেনি এবং এই টাকাগুলো তাদেরকে পেমেন্ট করেছে। এভাবে দেশের মানুষের কাছ থেকে লুট করে দিয়ে গেছে।'
সাবেক এই বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর দাবি করেন, 'ক্যাপাসিটি চার্জ পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশিরভাগের মেশিন খারাপ। খারাপ মেশিন এনে টাকা কামাই করে চলে গেছে।'
তিনি প্রশ্ন রেখে বলেন, 'এই লুটপাটের অংশ কারা ছিল? ক্যাপাসিটি চার্জের শীর্ষ পাঁচ কোম্পানির কথা আমি বলছি। সামিট নিয়েছে ১০ হাজার ৬৩০ কোটি টাকা, এ্যাগ্ররো ইন্টারন্যাশনাল নিয়েছে ৭ হাজার ৯৩২ কোটি টাকা, আল্ট্রা পাওয়ার হোল্ডিংস নিয়েছে ৭ হাজার ৫২৩ কোটি টাকা, ইউনাইটেড গ্রুপ নিয়েছে ৬ হাজার ৫৭৫ কোটি টাকা, আরপিসিএল নিয়েছে ৫ হাজার ১১৭ কোটি টাকা।'
তিনি বলেন, 'কুইক রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট করা হয় সাধারণত আপদকালীন বিদ্যুৎ সংকট নিরসনের জন্য। যে প্ল্যান্ট দুই বছরের, সেটা ১৫ বছর পর্যন্ত চালাচ্ছে এবং এসব কুইক রেন্টালে ৭৫ শতাংশ বিনিয়োগ করেছে উইথ আউট রিটার্ন। বুঝেন কি অবস্থা!'
'ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানির নামে নয় বছরে ক্যাপাসিটি চার্জ দিয়েছে ১১ হাজার ১৫ কোটি টাকা,' বলেন তিনি।
'সব কিছু রিভিউ করা হবে'
টুকু বলেন, 'আমরা পুরো বিষয়গুলো রিভিউ করব। মনে রাখতে হবে, রিভিউ মানে বাতিল না। আমরা দেখবো, কোন কোন জায়গায় দুর্বলতা ছিল।'
'যেকোনো সময় মুখ থুবড়ে পড়বে'
সাবেক এই বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর দাবি, 'আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিদ্যুতে যেসব উন্নয়ন করা হয়েছে, সেটা টেকসই না। যেকোনো সময় মুখ থুবড়ে পড়বে।'
'বিদ্যুৎখাতে দুর্নীতির ধরণ দেখার পর বোঝা যায়, তারা বিদ্যুৎখাতকে ফোকলা করে দিয়েছে। আর কিছু নেই। একটা উদাহরণ বলি। প্রতিটি মিটারের জন্য গড়ে অতিরিক্ত খরচ করেছে ৪ হাজার ৫০০ টাকা। কিনেছে ৬ হাজার ২০০ টাকা দিয়ে। তাহলে অতিরিক্ত ১ হাজার ৭২০ টাকা প্রতি মিটারে। তাহলে দেখেন কত টাকা নিয়ে গেছে। এনআইসি কার্ডের দাম ২ হাজার টাকা। তারা ধরেছে ৫ হাজার ২১৫ টাকা। এভাবে এই খাতের সর্বত্র দুর্নীতি। দুর্নীতির কোনো শেষ নেই।'
তিনি আরও বলেন, 'উনারা তো বিল পেমেন্ট করছেন। আমি যতটুকু জানি বকেয়া বেশি নেই। সবই তো পেমেন্ট করছে এই সরকার এসে। কিন্তু আলমেটলি ২০২৭ সালে এসে ধরা খাবে। আমরা মনে করি, এখন যদি টাইট না করি, তাহলে ২০২৭ সালে আমরা বিপদে পড়ে যাবো। ফরেন এক্সচেঞ্জ ঘাটতি হয়ে যাবে। টাকা ছাপানো হবে। এতে মুল্যস্ফীতি বাড়বে।'
'রূপপুর প্রকল্পের দুর্নীতি'
টুকু বলেন, 'রূপপুরে পারমাণবিক প্রকল্পের ৫০০ বিলিয়ন ডলার তারা (শেখ হাসিনাসহ তার পরিবার) নিয়ে গেছে। সেটা নিয়ে আরও তদন্ত হচ্ছে লন্ডনে টিউলিপের (ব্রিটিশ সংসদ সদস্য টিউলিপ সিদ্দিকী। যিনি শেখ রেহানার মেয়ে) ব্যাপারে এবং আরও দুর্নীতি আছে।'
'প্রিপেইড মিটার বাণিজ্যে সিন্ডিকেট'
সাবেক এই বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এটা তাদের একটা সিন্ডিকেট। ৭১ লাখ ২০ হাজার গ্রাহকের কাছে তারা মিটার পৌঁছাবে এবং সেখানে বিরাট অংকের একটা দুর্নীতি—প্রায় ৩৬ কোটি টাকা পাচার করেছে। ১ হাজার ২৩৫ কোটি অতিরিক্ত খরচ করেছে এর মধ্যে দুর্নীতি করেছে ৬১৭ কোটি টাকা। মিটার সরবরাহ ও স্থাপনে ছিল ৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। সেটা ১২ হাজার কোটি টাকা করেছে।'
তিনি বলেন, 'স্মার্ট প্রিপেইড মিটার প্রকল্পের যে নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে, সেটা কিছু ব্যক্তির নেটওয়ার্ক। যেখানে পতিত সরকারের প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়-স্বজনরা আছে। তারা কোটি কোটি টাকা লাভবান হবে এই প্রকল্পে।'
এলএনজি প্রকল্পের নামে সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুর কোম্পানিসহ 'একটি চক্র' কোটি কোটি টাকা লুটপাট করেছে বলে অভিযোগ করেন ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু।
বিদ্যুতখাতে দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিরোধে এই খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ানো, দুর্নীতি রোধে কঠোর আইন প্রণয়ন, বিদ্যুৎখাতের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, নিয়মিত বিদ্যুৎ পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি বলে মনে করেন তিনি।
বিএনপি-জামায়াত বাড়ছে দূরত্ব
আন্তর্জাতিক
২০২৫ সালকে স্বাগত জানলো বিশ্ব
নতুন বছর ২০২৫ সালকে স্বগত জানাতে শুরু করেছে বিশ্ব।বিশ্বে সবার আগে ২০২৫ সালকে স্বাগত জানিয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্বীপদেশ কিরিবাতি। সবার আগে দেশটি নতুন বছরে পা দিয়েছে। এরপর নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ড নতুন বছর বরণ করেছে। সেখানে আতশবাজিতে স্বাগত জানানো হয় নতুন বছরকে।
প্রায় একই সময়ে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে ঝলমলে আতশবাজির মধ্য দিয়ে স্বাগত জানানো হয় ২০২৫ সালকে। ঘড়ির কাঁটা রাত ১২ টা ছুঁতেই আকাশ আলোকিত হয়ে ওঠে আতশবাজির ঝলকানিতে। অস্ট্রেলিয়ার নর্দার্ন টেরিটোরিও নতুন বছরে পা দিয়েছে।
এরপর নতুন বছরে পা দিয়েছে জাপান। রাজধানী টোকিওর তোদাই-জি মন্দিরে ঘন্টাধ্বনি বাজানোর ঐতিহ্য মেনেই বর্ষবরণ করেছে দেশটি।
জাপানের পর দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত ও শ্রীলংকা একে একে ২০২৫ সালে পদার্পণ করবে। তারপর যুক্তরাজ্যসহ ২৫ টি দেশ স্বাগত জানাবে নতুন বছরকে।
চীনজুড়ে মানুষ নতুন বছরকে স্বগত জানাতে প্রস্তুত হয়ে আছে। চীনের শ্যানডং প্রদেশে নতুন বছরে শুভ ভাগ্য কামনা করে লেখা ব্যানার নিয়ে ২০২৫ সালকে বরণ করে নিতে প্রস্তুত একদল নারী।
ওদিকে, চীনের কংজিয়াং কাউন্টিতে একটি গ্রামের বাসিন্দারা প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে স্বাগত জানাচ্ছে নতুন বছরকে। রাজধানী বেইজিংয়ে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং নতুন বছরের আগমনীতে দিচ্ছেন ভাষণ।
গোটা বিশ্বজুড়েই বিভিন্ন দেশ নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর নানা প্রস্তুতি নিয়েছে।
তবে যুক্তরাজ্য আবহাওয়াজনিত কারণে নতুন বছর উদযাপানের কিছু অনুষ্ঠান বাতিল হয়েছে। ওদিকে, দক্ষিণ কোরিয়াও বছরের শেষের ভয়াবহ উড়োজাহাজ দুর্ঘটনার পর অনেটা নীরবেই পালন করছে নতুন বছর বরণের উৎসব।
অন্যান্য দেশগুলোতে ঐতিহ্য ও প্রচলিত প্রথা মেনে নতুন বছরকে স্বাগত জানানোর তোড়জোড় চলছে বলে জানিয়েছে বিবিসি। স্পেনে নতুন বছরের কাউন্টডাউনের প্রতি মুহূর্তে একটি করে আঙুর খাওয়াই প্রথা। ১৯০৯ সাল থেকে চলে আসছে এভাবে নতুন বছর বরণের রীতি।
আবার ডেনমার্কে থালা ছুড়ে স্বাগত জানানো হয়ে আসছে নতুন বছরকে। নতুন বছরের আগমনীতে যত বেশি থালা ছুড়া যাবে ততই শুভ ভাগ্য বয়ে আনবে নতুন সাল- এমনটিই বিশ্বাস করা হয় সেখানে।
ল্যাটিন আমেরিকার প্রথা হচ্ছে রঙচঙে অন্তর্বাস পরিধান করে নতুন বছরকে স্বাগত জানানো। অন্তর্বাসের রঙের ওপর নির্ভর করে নতুন বছর একেক জনের জন্য একেক রকম ভাগ্য বয়ে আনবে বলে সেখানে বিশ্বাস করা হয়- যেমন: হলুদ রঙ ধনসম্পদ আনে, লাল রঙ আনে ভালোবাসা।
ফিলিপিন্সের মানুষ আবার নতুন বছরের আগমনীতে কয়েনের প্রতীক হিসাবে গোল জিনিস দিয়ে নিজেদের ঘিরে রাখে। এছাড়াও পোলকা ডটের কাপড় পরা এবং আঙুর খাওয়াও রীতি দেশটিতে।
বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের পর অনেকটা দেরিতেই নতুন বছরে পা দেবে ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা। সবশেষে ২০২৫ সালকে বরণ করবে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলীয় এলাকাগুলো।
ফরাসি সেনাদের দেশ ছাড়ার নির্দেশ দিলো আইভরি কোস্ট
ফরাসি সেনাদের আইভরি কোস্ট ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে আফ্রিকান দেশটি। গতকাল মঙ্গলবার আইভরি কোস্ট সরকার এই নির্দেশ দিয়েছে বলে এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
এপি বলছে, আইভরি কোস্ট হলো সর্বশেষ আফ্রিকান দেশ যারা তাদের পুরনো ঔপনিবেশিক শক্তির সঙ্গে সামরিক সম্পর্ক কমাল।
আইভরি কোস্টের প্রেসিডেন্ট আলাসানে ওয়াত্তারা বলেছেন, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে সেনা প্রত্যাহার শুরু হবে। আইভরি কোস্টে ফ্রান্সের ৬০০ সেনা রয়েছে।
'আমরা আইভরি কোস্ট থেকে ফরাসি বাহিনীকে সমন্বিত ও সংগঠিতভাবে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি,' বলেন তিনি।
তিনি জানান, ফরাসি সেনাবাহিনী পরিচালিত পোর্ট বোয়েটের সামরিক পদাতিক ব্যাটালিয়ন আইভরিয়ান সেনাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
পশ্চিম আফ্রিকার অন্যান্য দেশকে অনুসরণ করে এই ঘোষণা দিয়েছেন আইভরি কোস্টের প্রেসিডেন্ট আলাসানে ওয়াত্তারা। পশ্চিম আফ্রিকার অন্যান্য দেশ থেকেও ফ্রান্সের সামরিক বাহিনীকে চলে যেতে বলা হচ্ছে।
ফরাসি সেনাদের আফ্রিকা ছাড়ার অনুরোধকে প্যারিসের সঙ্গে এই অঞ্চলের সম্পর্কের কাঠামোগত পরিবর্তনের অংশ হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চাঁদ, নাইজার ও বুরকিনা ফাসোসহ পশ্চিম আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশে ফ্রান্স একই ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। যেখানে বহু বছর ধরে থাকা ফরাসি সেনাদের বের করে দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া অভ্যুত্থানপীড়িত মালি, বুরকিনা ফাসো ও নাইজারসহ পশ্চিম আফ্রিকার বেশ কয়েকটি দেশ সম্প্রতি ফরাসি সেনাদের চলে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। তাদের মধ্যে সাম্প্রতিককালে সেনেগাল ও চাঁদ যোগ হয়েছে।
এপি বলছে, ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর থেকে এখন পর্যন্ত আফ্রিকার ৭০ শতাংশের বেশি দেশ ছাড়তে হয়েছে ফরাসি সেনাদের।
বাংলাদেশিদের জন্য থাইল্যান্ডের ই-ভিসা চালু ২ জানুয়ারি থেকে
বাংলাদেশিদের জন্য ভ্রমণ সহজ করার লক্ষ্যে ই-ভিসা সেবা চালু করছে থাইল্যান্ড। এর ফলে দেশটিতে ভ্রমণের জন্য ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া আরও সহজ ও কার্যকর হবে।
রোববার রয়াল থাই এম্বাসি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলেও সোমবার গণমাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে।
আগামী বছরের ২ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশিদের জন্য ই-ভিসা সেবা চালু করা হবে বলে দূতাবাসের এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা গেছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিকরা আগামী ২ জানুয়ারি থেকে ই-ভিসা সেবা পেলেও সরকারি পাসপোর্টধারীদের আগামী ১৯ ডিসেম্বর থেকে এ সুবিধা দেবে দেশটির সরকার।
আবেদনের ১০ দিনের মধ্যে ইমেইলে এ ভিসা দেওয়া হবে। আবেদনকারীদের https://www.thaievisa.go.th ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আবেদন করতে হবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে আবেদনকারীরা ই-মেইলের মাধ্যমে অনুমোদিত ভিসা পাবেন। এরপর এটি প্রিন্ট করে থাই ইমিগ্রেশন সেন্টারে উপস্থাপন করতে পারবেন তারা।
আবেদনকারীরা https://www.combank.net.bd/thaievisa ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দূতাবাসের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আবেদন ফি জমা দিতে পারবেন। এরপর দূতাবাসের ফি যাচাইকরণের জন্য প্রণীত সিস্টেম পেমেন্ট ইনফো সামারিতে তার তথ্য দিতে হবে।
ই-ভিসা চালুর ফলে আগামী ২৪ ডিসেম্বর থেকে ঢাকার থাইল্যান্ডের ভিসা সেন্টারটি বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে দূতাবাস।
ইউরোপীয় ইউনিয়নে রাশিয়ার গ্যাস ট্রানজিট বন্ধ করেছে ইউক্রেন
ইউক্রেনের গ্যাস ট্রানজিট অপারেটর নাফটোগাজ ও রাশিয়ার গ্যাজপ্রমের মধ্যে পাঁচ বছরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে রাশিয়ার গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করেছে ইউক্রেন। আজ বুধবার বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছিলেন, তার দেশ রাশিয়াকে 'আমাদের রক্তের ওপর দিয়ে অতিরিক্ত বিলিয়ন ডলার আয় করতে' দেবে না।
এজন্য ইইউকে প্রস্তুতি নিতে এক বছর সময় দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছিলেন তিনি।
পরে ইউরোপীয় কমিশন জানিয়েছিল, মহাদেশটির গ্যাস ব্যবস্থা 'স্বাভাবিক ও স্থিতিশীল' অবস্থায় আছে। তাই ইউক্রেনের মধ্য দিয়ে ট্রানজিট শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার পর্যাপ্ত সক্ষমতা তাদের রয়েছে।
তবে রাশিয়া এখনো কৃষ্ণ সাগর দিয়ে তুর্কস্ট্রিম পাইপলাইনের মাধ্যমে হাঙ্গেরির পাশাপাশি তুরস্ক ও সার্বিয়ায় গ্যাস পাঠাতে পারবে।
ইউক্রেনের মধ্য দিয়ে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়নে রুশ গ্যাসের যুগের আপাতত অবসান হয়েছে বলে বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
রুশ গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় স্লোভাকিয়া সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে ইউরোপীয় কমিশন বলেছে, ভিন্ন পরিকল্পনা ও বিকল্প সরবরাহের কারণে এর প্রভাব মারাত্মক হবে না।
অবশ্য বিবিসি বলছে, রুশ গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় সমগ্র ইউরোপে বড় ধরনের কৌশলগত প্রভাব পড়বে।
রাশিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজার হারালেও দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, ইইউ দেশগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
এর আগে, ২০২২ সালে ইউক্রেনে হামলা শুরুর পর থেকে রাশিয়া থেকে গ্যাস আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়েছিল ইইউ। তবে পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি সদস্য দেশ রাশিয়ার সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে, গ্যাস রপ্তানি করে রাশিয়া বছরে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ইউরো (পাঁচ দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার বা চার দশমিক দুই বিলিয়ন পাউন্ড) আয় করেছে।
ইইউয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৩ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের গ্যাস আমদানির ১০ শতাংশের কম ছিল রাশিয়ান গ্যাস, যা ২০২১ সালে ছিল ৪০ শতাংশ।
তবে স্লোভাকিয়া ও অস্ট্রিয়াসহ ইইউভুক্ত বেশ কয়েকটি দেশ রাশিয়া থেকে গ্যাস আমদানি অব্যাহত রেখেছিল।
অস্ট্রিয়ার জ্বালানি নিয়ন্ত্রক সংস্থা জানিয়েছে, গ্যাসের অন্যান্য উৎস ও পর্যাপ্ত মজুত থাকায় তারা সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার পূর্বাভাস দেয়নি।
ইউক্রেনের সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে স্লোভাকিয়ার ওপর প্রভাব ফেলেছে। কারণ দেশটি ইইউতে রাশিয়ার গ্যাসের প্রধান প্রবেশদ্বার এবং অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি ও ইতালিতে গ্যাস পাইপ ব্যবহার করে ট্রানজিট ফি আয় করে।
গত শুক্রবার স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকো ইউক্রেনে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধের হুমকি দিয়েছিলেন। রবার্ট ফিকো সম্প্রতি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আলোচনার জন্য মস্কো সফর করেন।
রবার্ট ফিকোর মস্কো সফরের পর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি অভিযোগ করেন, স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী পুতিনকে 'যুদ্ধে অর্থায়ন ও ইউক্রেনকে দুর্বল করতে' সহায়তা করতে চাচ্ছেন।
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ফিকো ইউক্রেনীয়দের জন্য আরও দুর্ভোগ ডেকে আনতে রাশিয়ার সঙ্গে স্লোভাকিয়াকে জড়াচ্ছেন।'
এদিকে পোল্যান্ড কিয়েভকে বৈদ্যুতিক সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে। তারা বলেছে, স্লোভাকিয়া বিদ্যুৎ রপ্তানি বন্ধ করলে তারা বিদ্যুৎ সহায়তা দেবে। বিদ্যুৎ সমস্যা ইউক্রেনের জন্য বড় একটি সমস্যা, কারণ দেশটির বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো রাশিয়ার নিয়মিত আক্রমণের শিকার হয়।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের অংশ না হলেও মলদোভা এই ট্রানজিট চুক্তি শেষ হওয়ায় সমস্যায় পড়তে পারে। কারণ দেশটির একটি বিদ্যুৎকেন্দ্রের জ্বালানি রাশিয়ার গ্যাসের ওপর নির্ভরশীল।
মলদোভার জ্বালানিমন্ত্রী কনস্ট্যান্টিন বোরোসান বলেছেন, সরকার স্থিতিশীল বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে নাগরিকদের মানসিকভাবে শক্ত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি থেকে মলদোভায় জ্বালানি খাতে ৬০ দিনের জরুরি অবস্থা জারি রয়েছে।
রাশিয়া ১৯৯১ সাল থেকে ইউক্রেন হয়ে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ করে আসছিল।
ইইউ রাশিয়ার গ্যাসের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনার পর কাতার ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) পাশাপাশি নরওয়ে থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাসের বিকল্প উৎস খুঁজে পেয়েছে মহাদেশটি।
ডিসেম্বরে ইউরোপীয় কমিশন একটি পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিল। ওই পরিকল্পনা অনুযায়ী, ইইউ সদস্য দেশগুলোতে গ্যাস ট্রানজিট ব্যবস্থা পুরোপুরিভাবে প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হবে।
ইউরোপীয় ইউনিয়নের আপৎকালীন পরিকল্পনার আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোতে ট্রান্স-বলকান রুট থেকে গ্রিস, তুর্কি ও রোমানিয়া থেকে গ্যাস সরবরাহ করা হবে। অন্যদিকে পোল্যান্ডের মধ্য দিয়ে পাইপের মাধ্যমে নরওয়ের গ্যাস সরবরাহ করা হবে। এছাড়া জার্মানির মধ্য দিয়ে অন্যান্য সরবরাহ মধ্য ইউরোপে পৌঁছাবে।
ধর্ষণ নিয়ে ফ্রান্সের মনোভাব বদলে দিয়েছেন জিসেল পেলিকট
প্রতিদিন ভোরের আলো ফোটার আগেই লাইন শুরু হয়ে যেত। অ্যাভিগননের কাচ আর কংক্রিটের তৈরি কোর্টহাউসের বাইরে ব্যস্ত রিং রোডের পাশে ফুটপাথে শরতের ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে থাকতেন একদল নারী। সব সময় নারীদেরই দেখা মেলে ওই লাইনে।
তারা কিন্তু দিনের পর দিন এসেছেন। কেউ কেউ সঙ্গে ফুলও নিয়ে এসেছেন। এরা সকলেই জিসেল পেলিকটকে প্রশংসা জানাতে জড়ো হন।
তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে, কাচের দরজা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন মিজ পেলিকট, তখন জড়ো হওয়া নারীদের মধ্যে কেউ কেউ আবার সাহস করে তার কাছে গিয়েছেন।
কেউ আবার চিৎকার করে বলেছেন, "আমরা তোমার সঙ্গে আছি, জিসেল।"
"সাহস রাখো।"
জিসেল পেলিকটকে সমর্থন জানাতে আসা বেশিরভাগ নারীই আদালতে থেকে গিয়েছিলেন জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে নিজেদের আসন সুরক্ষিত করার আশায়। ওই কক্ষের টেলিভিশনের পর্দায় তারা মামলার বিচার প্রক্রিয়া দেখতে পারেন।
এদের সবার উদ্দেশ্য ছিল একটাই, জিসেল পেলিকটের সাহসিকতার সাক্ষী থাকা।
আদালতে চুপচাপ বসেছিলেন এই নারী, যিনি ব্যক্তিগত জীবনে একজন দাদীও। আর বিচার চলাকালীন তার চারপাশে উপস্থিত ছিলেন তারই ধর্ষকরা।
আদালত চত্বরে যারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে একজন বছর ৫৪-র ইসাবেল মুনিয়ার। তিনি বলছিলেন, "আমি ওর (জিসেল পেলিকট) মধ্যে নিজেকে দেখতে পাই।"
"অভিযুক্তদের ব্যক্তিদের মধ্যে একজন এক সময় আমার বন্ধু ছিল। ন্যাক্কারজনক ব্যাপার।"
ওই চত্বরে উপস্থিত আর এক নারী সাদজিয়া জিমলি বলেন, "নারীবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছেন তিনি (জিসেল পেলিকট)।"
আদালতে জড়ো হওয়ার নেপথ্যে আরও একটা কারণ ছিল। সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে মনে হচ্ছিল, তারা যেন উত্তর খুঁজছেন।
ফরাসি নারীরা (যাদের সংখ্যা শুধুমাত্র অ্যাভিগননের আদালত প্রাঙ্গণে থেমে থেকেছে এমনটা নয়) মূলত দুটো প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন।
প্রথম প্রশ্ন হলো এই মামলা ফরাসি পুরুষদের সম্পর্কে কী ইঙ্গিত দেয়? ওই ৫০জন পুরুষদের মধ্যে সবাই একটা ছোট, গ্রামীণ পাড়ায়, অপরিচিত ব্যক্তির শয়নকক্ষে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকা এক নারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নৈমিত্তিক আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন?
দ্বিতীয় প্রশ্নটা কিন্তু প্রথম প্রশ্ন থেকেই উঠে আসে- যৌন সহিংসতা এবং মাদক ব্যবহার করে অচেতন করার পর ধর্ষণের যে মহামারি, তার মোকাবিলা করতে এবং 'লজ্জা' ও 'সম্মতি' সম্পর্কে থাকা সংস্কার এবং অজ্ঞতাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে কোনওভাবে সাহায্য করতে পারবে কি এই মামলা?
"লজ্জার পক্ষ বদল করা উচিত" (অর্থাৎ লজ্জা ভুক্তভোগীর নয় ধর্ষকের) বলার মধ্যে দিয়ে জিসেল পেলিকট নিজের সাহসী অবস্থান এবং তার দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিয়েছেন। তাই প্রশ্নটা হলো সেই বদল সত্যিই আসবে কি?
প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার তার মামলার সাজা ঘোষণার দিন ছিল। মাদক ব্যবহার করে অচেতন অবস্থায় তাকে ধর্ষণ করার জন্য অন্য পুরুষদের উৎসাহিত করা এবং ঘটনার ভিডিও করার অভিযোগ-সহ একাধিক অভিযোগ ছিল তার স্বামী (এখন প্রাক্তন) ডমিনিক পেলিকটের বিরুদ্ধে।
আদালত ডমিনিক পেলিকটের ২০ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে। এর পাশাপাশি অন্যান্য দোষী ব্যক্তিদেরও সাজা ঘোষণা করা হয়েছে।
অভিযুক্তের মুখোশের আড়ালে
একটা দীর্ঘ বিচারপর্ব তার নিজস্ব একটা বাতাবরণ তৈরি করে এবং গত কয়েক সপ্তাহ ধরে, অ্যাভিগননের 'প্যালেস দ্য জাস্টিস'- ভবনের ভিতরে একটা অদ্ভুত ধরণের স্বাভাবিকতা তৈরি হতে দেখা গিয়েছে। টিভি
ক্যামেরা আর আইনজীবীদের কোলাহলের মাঝেও ধর্ষণে অভিযুক্তদের ঝলক মিলেছে। তাদের চেহারা যে সব সময় মুখোশের আড়ালে ঢাকা ছিল তেমনটা নয়।
মামলার বিচারের শুরুর দিকে তাদের দেখতে পেলে যেমন 'শক' (অভিঘাত) লাগত, তেমন অনুভূতি আর হয় না।
অভিযুক্তদের ঘুরে বেড়াতে, আড্ডা দিতে, রসিকতা করতে, মেশিন থেকে কফি নিতে বা রাস্তার ওপারের ক্যাফে থেকে ফিরতে দেখা গিয়েছে। আর এই দৃশ্যগুলো কোনও না কোনওভাবে তাদের (অভিযুক্তদের) বিভিন্ন প্রতিরক্ষা কৌশলগুলোর মূল যুক্তিকেই খাড়া করতে চায় যে, "এরা একেবারে সাধারণ লোক, ফরাসি সমাজের একটা 'ক্রস-সেকশন', যারা অনলাইনে 'সুইঙ্গিং' অ্যাডভেঞ্চারের (যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বিভিন্ন উপায়) সন্ধানে ছিলেন এবং অপ্রত্যাশিত একটা অবস্থার মাঝে পড়ে গিয়েছেন।"
"এটাই (এই যুক্তিই) এই মামলার সবচেয়ে মর্মান্তিক বিষয়। ভাবতে কষ্ট হয়," বলেছেন এলসা লাবোহে, যিনি 'ডেয়ার টু বি ফেমিনিস্ট' নামে একট ফরাসি অ্যাক্টিভিস্ট গ্রুপে কাজ করেন।
তিনি বলেছেন, "পুরুষদের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক রয়েছে এমন মানুষের মধ্যে বেশির ভাগই নিজের সঙ্গীকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবেন। তবে এখন, অনেক নারীই তার (জিসেল পেলিকটের সঙ্গে) মতোই অনুভব করেছেন। তাদের মনে হয়েছে-আচ্ছা, এমনটা তো আমার সঙ্গেও ঘটতে পারে।"
"এরা অপরাধী মাস্টারমাইন্ড নয়। ওরা শুধুমাত্র ইন্টারনেটের সাহায্য নিয়েছিল... তাই আশঙ্কা করা হচ্ছে সব জায়গাতেই একই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে।"
এই একই দৃষ্টিভঙ্গি ফ্রান্সে ব্যাপকভাবে রয়েছে, তবে ব্যতিক্রমও আছে।
ফ্রান্সের 'ইনস্টিটিউট অব পাবলিক পলিসি'-র ২০২৪ সালে প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে ২০১২ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে গড়ে ৮৬% যৌন নির্যাতনের অভিযোগ এবং ৯৪% ধর্ষণের অভিযোগের ক্ষেত্রে হয় বিচার হয়নি বা মামলাগুলো কখনও বিচারের জন্য আসেইনি।
এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মিজ লাবোহে যুক্তি দিয়েছেন যে যৌন সহিংসতার ঘটনা ঘটলে যখন কিছু পুরুষ জানে যে তারা "পার পেয়ে যেতে পারে। এবং তাই এটা (এ জাতীয় ঘটনা) ফ্রান্সে এত বেশি ছড়িয়ে পড়েছে বলে আমি মনে করি।"
'দানবও নয়, সাধারণ মানুষও নয়'
চার মাসের বিচার চলাকালীন, আদালতে বিরতির সময় অভিযুক্তদের বেশিরভাগই 'প্রেস কোর'-এর (গণমাধ্যমের) নারী সাংবাদিকদের পেরিয়ে যাওয়ার আগে মেটাল ডিটেক্টর দ্বারা পরীক্ষার জন্য জড়ো হতেন। সাংবাদিকরা অপেক্ষায় থাকতেন চেম্বারে প্রবেশের। ভিতরে ঢুকে অভিযুক্তরা নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে থাকতেন।
আদালত নিযুক্ত মনোরোগ বিশেষজ্ঞ লরেন্ট লায়েট সাক্ষ্য দিয়েছেন যে অভিযুক্তরা না "দানব" বা না "সাধারণ মানুষ"। তাদের কেউ কেউ কেঁদেছেন। কয়েকজন স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।
কিন্তু বেশির ভাগই নানা অজুহাত দেখিয়েছেন। অনেকে বলেছেন যে তারা কেবল "লিবার্টাইনস" (যৌন তৃপ্তির বিষয়ে যাদের কোনও ছুৎমার্গ নেই)।
ফরাসিরা বলে যেমন থাকেন যে অনেক দম্পতিরই নানান 'ফ্যান্টাসি' (কল্পনা) রয়েছে এবং এক্ষেত্রে তাদের জানার কোনও উপায় ছিল না যে মিজ পেলিকট মিলনের জন্য সম্মতি দেননি।
অন্যরা আবার দাবি করেছেন যে মিজ পেলিকটের স্বামী ডমিনিক পেলিকট তাদের ভয় দেখিয়েছেন।
অভিযুক্তদের চারিত্রিক দিক থেকে স্পষ্টভাবে কোনও বৈশিষ্ট্য বা মিল দেখা যায়নি। তারা সমাজে একটা বিস্তৃত অংশের প্রতিনিধিত্ব করেন।
অভিযুক্তদের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ ব্যক্তির সন্তান আছে। অভিযুক্তদের অর্ধেক বিবাহিত অথবা তাদের কোনও সম্পর্ক রয়েছে। এক চতুর্থাংশের কিছু বেশি জানিয়েছেন, তারা শৈশবে নির্যাতন বা ধর্ষণের শিকার হয়েছেন।
এদের মধ্যে বয়স, চাকরি, সামাজিক শ্রেণিগত দিক থেকে শ্রেণিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। যে দুই বৈশিষ্ট্য তারা ভাগ করে নেন তা হলো, তারা পুরুষ এবং 'কোকো' নামে একটা অবৈধ অনলাইন চ্যাট ফোরাম মারফত যোগাযোগ করেছিলেন।
'সুইঙ্গারদের' পাশাপাশি শিশুদের যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং ড্রাগ ডিলারদের আকর্ষণ করে থাকে এই চ্যাট ফোরাম।
ফরাসি প্রসিকিউটরদের মতে, চলতি বছরের শুরুতে বন্ধ করে দেওয়া এই অনলাইন সাইটের সঙ্গে ২৩,০০০ এরও বেশি অপরাধমূলক কার্যকলাপের যোগ রয়েছে।
বিবিসি জানতে পেরেছে, বিচারাধীন ব্যক্তিদের মধ্যে ২৩ জন বা ৪৫% পূর্ব অপরাধের মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। যদিও কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে না, তাও এই সংখ্যা ফ্রান্সের জাতীয় অপরাধমূলক ঘটনার গড়ের প্রায় চারগুণ।
এই সমস্ত মিলিয়ে মিজ লাবোহে যে উপসংহারে পৌঁছেছেন তা হলো, "যৌন সহিংসতায় লিপ্ত পুরুষদের কোনও সাধারণ প্রোফাইল থাকে না।"
এই মামলা বেশ কাছ থেকে অনুসরণ করেছেন যারা তাদের মধ্যে একজন হলেন ফরাসি সাংবাদিক জুলিয়েট ক্যাম্পিয়ন। তিনি পাবলিক ব্রডকাস্টার 'ফ্রান্স ইনফোর-এ কর্মরত। সংবাদ প্রতিবেদনের জন্য আদালতের বিচার-প্রক্রিয়া নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তিনি।
তার মতে, "আমি মনে করি এই মামলা অন্য দেশেও হতে পারত। তবে এটা (এই মামলা) ফ্রান্সের পুরুষরা নারীদের কীভাবে দেখেন সে সম্পর্কে অনেক কিছু বলে... বিশেষত সম্মতির ধারণা সম্পর্কে।"
"অনেক পুরুষই জানেন না যে সম্মতি আসলে কী। তাই দুঃখজনকভাবে (এই মামলাটি) আমাদের দেশ সম্পর্কে অনেক কিছুই বলছে।"
'আ ম্যাটার অব মিস্টার এভরিম্যান'
ফ্রান্স জুড়ে ধর্ষণের বিষয়ে মানুষের মনোভাবের রূপরেখা গঠনে অবশ্যই সাহায্য করছে পেলিকট মামলা।
গত ২১ শে সেপ্টেম্বর অভিনেতা, গায়ক, সংগীতজ্ঞ এবং সাংবাদিক-সহ একদল বিশিষ্ট ফরাসি পুরুষ গণ চিঠি লিখেছিলেন যা 'লিবারেশন' সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।
সেখানে তারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে পেলিকট মামলা প্রমাণ করেছে যে সহিংসতার ঘটনা যেখানে অভিযুক্ত একজন পুরুষ কিন্তু আদপে কোনও "দানবের বিষয় নয়।" চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, "এটা পুরুষদের ব্যাপার, মিস্টার এভরিম্যানের ব্যাপার। ব্যতিক্রম ছাড়া সব পুরুষই এমন একটা ব্যবস্থা থেকে উপকৃত হয় যা নারীদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে।"
চিঠিতে পিতৃতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চাওয়া পুরুষদের জন্য একটা "রোড ম্যাপ"-ও তৈরি করা ছিল। পত্রে উল্লেখ করা ছিল, "আসুন আমরা এটা মনে করা বন্ধ করি যে আমাদের আচরণকে ন্যায়সঙ্গত বলে দাবি করে এমন একটা পুরুষালি প্রকৃতি রয়েছে।"
বিশেষজ্ঞদের অনেকে মনে করেন এই মামলার সঙ্গে জনস্বার্থও জড়িয়ে রয়েছে।
যেমন আইনজীবী কারেন নোবলিনস্কি বলেছেন, "এই পুরো মামলা সবার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকল প্রজন্ম- তরুণ, অল্প বয়সী মেয়ে, প্রাপ্তবয়স্ক সবার জন্য দরকারি।" এই আইনজীবী প্যারিস-ভিত্তিক যৌন নিপীড়নের মামলা বিশেষজ্ঞ।
তার মতে, "এটা তরুণদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করেছে যে ধর্ষণ সব সময় বারে হয় না, ক্লাবে হয় না। এটা আমাদের বাড়িতেও ঘটতে পারে।"
#নটঅলমেন
তবে স্পষ্টতই আরও অনেক কিছু করার আছে। এই মামলার শুরুর দিকে আমি লুই বোনেটের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি পেলিকট দম্পতির আদি নিবাসস্থল মাজানের মেয়র।
যদিও তিনি এই ধর্ষণের অভিযোগের নিন্দা করার ক্ষেত্রে দ্ব্যর্থহীন ছিলেন, তবুও তাকে একটা বিষয় নিয়ে দুইবার মন্তব্য করতে শোনা গিয়েছিল।
তার মতে, "পেলিকটের অভিজ্ঞতা অতিরঞ্জিত হয়েছে" এবং তিনি (লুই বোনেট) যুক্তি দিয়েছিলেন যে যেহেতু মিজ পেলিকট ঘটনার সময় অচৈতন্য অবস্থায় ছিলেন, তাই তিনি ধর্ষণের শিকার অন্যান্যদের তুলনায় কম কষ্ট অনুভব করেছেন।
তার কথায়, "হ্যাঁ, আমি কম হওয়ার কথা বলছি তার কারণ আমার মনে হয় এটা (ঘটনা) আরও খারাপ হতে পারত।"
"যখন (ধর্ষণ বা যৌন হেনস্থার ঘটনায়) শিশুরা ভুক্তভুগী হয় বা নারীদের মেরে ফেলা হয়, তখন সেটা খুবই গুরুতর হয়ে যায়। কারণ ফিরে যাওয়ার সুযোগ নেই।"
"এক্ষেত্রে পরিবারকে পুনর্গঠন করতে হবে। কষ্ট হবে, কিন্তু এখানে কারও মৃত্যু হয়নি। সুতরাং, তারা এটা (পুনর্গঠন) করতে পারবেন।"
লুই বোনেটের এই মন্তব্য ফ্রান্সজুড়ে ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। পরে মেয়র একটা বিবৃতি জারি করে "আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।"
'সমস্ত পুরুষই ধর্ষণ করতে সক্ষম'-এই যুক্তির উপর পেলিকট মামলা ফোকাস করছে বলে প্রচুর বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এই জাতীয় দাবির সমর্থনে কোনও প্রমাণ নেই।
অনলাইন মাধ্যমে #NotAllMen (সব পুরুষরা না) হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে যুক্তির বিরোধিতা করেছেন পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক ব্যক্তি প্রশ্ন তুলেছেন, "আমরা অন্য নারীদের খারাপ আচরণের জন্য বাকি নারীদের 'লজ্জা' বয়ে বেড়াতে বলি না, তাই শুধুমাত্র পুরুষ হওয়ার কারণেই আমাদের অন্য কারও লজ্জা বয়ে যেতে হবে?"
এর বিরুদ্ধে দ্রুত প্রতিক্রিয়া মিলেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে #NotAllMen -এর প্রতিবাদ জানিয়ে নারীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এবং কখনও কখনও নিজেদের নির্যাতনের বিবরণ জানিয়ে জবাব দিয়েছেন।
সাংবাদিক ম্যানন মারিয়ানি লিখেছেন, "এই হ্যাশট্যাগ পুরুষরাই তৈরি করেছেন এবং তা ব্যবহারও করছেন পুরুষরাই। এটা নারীদের দুর্ভোগকে চুপ করানোর একটা উপায়মাত্র।"
পরে, একজন পুরুষ সংগীতশিল্পী এবং ইনফ্লুয়েন্সার ওয়াক্স এই হ্যাশট্যাগের সমালোচনা করেছেন। হ্যাশট্যাগ ব্যবহারকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "চিরতরের জন্য চুপ করুন। এটা আপনার বিষয় নয়, এটা আমাদের বিষয়। পুরুষরা খুন করে। পুরুষরা আক্রমণ করে। ব্যাস।"
এলসা লাবোহে মনে করেন, ফরাসিদের মনোভাব পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে। "আমি মনে করি অনেক লোক এখনও মনে করে যে যৌন সহিংসতা রোমান্টিক বিষয় বা এমন কিছু যা আমরা এখানে (ফ্রান্সে) যেভাবে চলি তারই একটা অংশ," তিনি যুক্তি দেন।
"এই জাতীয় যুক্তি মোটেই গ্রহণ না করে তার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণও।"
'রাসায়নিক আত্মসমর্পণ' এবং প্রমাণ
ফরাসি সাংসদ সান্দ্রিন জোসোর দফতর সেন নদীর তীরে ফরাসি পার্লামেন্ট ভবনের ঠিক পেছনে। সেই ছোট্ট দফতরে একটা ডেস্কের পাশে থাকা পোস্টারে দুই শব্দের শপথ বাক্য লিখে রেখেছেন তিনি।
সেখানে লেখা রয়েছে 'কেমিক্যাল সাবমিশন' (রাসায়নিক আত্মসমর্পণ) যা ইঙ্গিত করে ধর্ষণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত মাদকদ্রব্যকে। এরই বিরুদ্ধে মিজ জোসোর লড়াই।
এক বছর আগে, ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে, জোয়েল গুয়েরিয়াউ নামে এক সিনেটরের পার্টিতে গিয়েছিলেন তিনি। প্যারিসস্থিত অ্যাপার্টমেন্টে ছিল ওই পার্টি।
মিজ জোসোর অভিযোগ যে ধর্ষণের উদ্দেশ্যে তার শ্যাম্পেনে মাদক মিশিয়ে দিয়েছিলেন ওই সিনেটর। মি. গুয়েরিয়াউ অবশ্য তাকে মাদক দেওয়ার বিষয়টা অস্বীকার করেছেন। তার যুক্তি ছিল এটা 'হ্যান্ডলিং ত্রুটি' এবং তদন্তকারীদের বলেছিলেন ওই গ্লাস 'দূষিত' হয়েছিল ঘটনার একদিন আগে।
এক বিবৃতিতে মি. গুয়েরিয়াউয়ের আইনজীবী বলেছেন, "সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রাথমিক প্রতিবেদন পড়ে ঘটনা সম্পর্কে যে ধারণা তৈরি হতে পারে, সেই অশ্লীল ব্যাখ্যা থেকে আমরা কয়েক মাইল দূরে আছি।"
আগামী বছরে এই মামলার বিচার হওয়ার কথা রয়েছে।
মিজ জোসো এখন এমন ঘটনার বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছেন এবং ফরাসি আইনি ব্যবস্থার নিরিখে "ক্ষতিগ্রস্তদের সফর সহজ করা" তার উদ্দেশ্য।
"এটা একটা বিপর্যয়কর মুহূর্ত। কারণ প্রমাণের অভাবে অভিযোগ দায়ের করা খুব কম ভুক্তভোগীই বিচার পেতে সক্ষম হন। পর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং মানসিক বা আইনি সহায়তা নেই। যৌন সহিংসতার মামলায় আমরা সর্বত্রই ত্রুটি দেখতে পাই।"
জিসেল পেলিকটের মেয়ে ক্যারোলিনের সঙ্গে মিজ জোসো উদ্যোগ নিয়েছেন যাতে 'ড্রাগ-টেস্টিং কিট' (মাদক পরীক্ষা করা যায় এমন কিট) ফ্রান্সের ওষুধের দোকানে উপলব্ধ করানো যেতে পারে। পেলিকট মামলার আবহে এই কিট পরীক্ষামূলকভাবে দেখার জন্য সরকারি সমর্থনও পেয়েছে।
"আমি আশাবাদী। চিকিৎসা জগৎ এবং ফরাসি জনগণ চাইছে যে লজ্জা পক্ষ বদলাক (লজ্জা ভুক্তভোগীর বদলে অভিযুক্তের হোক)," জিসেল পেলিকটের বিখ্যাত উদ্ধৃতি আরও একবার তুলে ধরেছেন মিজ জোসো।
তবে 'প্যারিস অ্যাডিকশন মনিটরিং সেন্টার'-এর রসায়নবিদ এবং বিশেষজ্ঞ ড. লেইলা চাওয়াচি বলছেন, মাদক ও ধর্ষণ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার দীর্ঘ সংগ্রামের একটা ধাপ হলো এই মামলা।
"এটাকে (মাদক ব্যবহার করে অচৈতন্য করে ধর্ষণ) বড় জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সমস্যা হয়ে উঠতে হবে যাতে প্রত্যেকে (বিষয়টাকে) গুরুত্ব সহকারে নেয় এবং ভুক্তভোগীদের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারে উন্নতির জন্য কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে।"
তিনি বলেন, "আমাদের সবার বিষয়টা নিয়ে ভাবা দরকার যাতে এটা শুধুমাত্র ন্যায় বিচারের ইস্যু না হয়ে, স্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে বিবেচিত হয়। এটা আমাদের সবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।"
বর্তমানে ফরাসি আইনে "সম্মতি" শব্দটাকে ধর্ষণের সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাই কেউ কেউ যুক্তি দেখিয়েছেন যে এটা আরও স্পষ্ট করার জন্য পরিবর্তন করা উচিত।
তবে মিজ নোবলিনস্কি মনে করেন, ফোকাসটা অন্য কোথাও থাকা উচিত।
তিনি বলেছেন, "আইনের বদলের উপর নয়, (ফোকাস) থাকা উচিত, পুলিশের উপর, তদন্তের উপর এবং তার সঠিকভাবে অর্থায়নের উপর।"
"তাদের পর্যাপ্ত সম্পদ নেই। তাদের কাছে অনেক মামলা আছে, আর এটাই আসল বিষয়। যখন আপনাকে অনেক কিছু সামলাতে হয়, তখন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন।"
বিচারের প্রথম সপ্তাহগুলোতে আদালত প্রাঙ্গণে যখন তিনি প্রতিদিন যাতায়াত করতেন তখন কাঁধ কুঁজো করে হাঁটতেন জিসেল পেলিকট। তার ভঙ্গি প্রতিরক্ষামূলক ছিল।
যেভাবে এই মামলা নজর কেড়েছিল তাতে তাকে তখন বিচলিত বলে মনে হয়েছিল। তবে সমাপনী যুক্তির সময় আসতে আসতে তার আচরণ সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল। একেবারে স্থির হয়ে বসেছিলেন তিনি।
একটা বৃহত্তর পরিবর্তনের সঙ্গে এটা মিলে গিয়েছে। বিচারের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মামলার সঙ্গে যুক্ত আইনজীবী, যারা এই মামলা দেখছিলেন এবং মিসেস পেলিকট নিজে তারই নেওয়া একটা সিদ্ধান্তের অসাধারণ প্রভাব বুঝতে পেরেছিলেন।
আর সেই সিদ্ধান্তটা শুধুমাত্র এই মামলার উন্মুক্ত বিচার প্রক্রিয়া হওয়ার বিষয়ে নয়, প্রতিটা প্রমাণ ও ঘটনার বিবরণ আদালতে সর্বসমক্ষে দেখানোর সিদ্ধান্ত।
এলসা লাবোহে বলেছেন, "তিনি আমাদের দেখাচ্ছেন যে... আপনি যদি ভিকটিম (ভুক্তভোগী) হন... তাহলে লজ্জা না বয়ে বেড়ানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। মাথা উঁচু রাখুন।"
"একজন নারী হিসেবে আপনাকে শুরু করতে হবে একজন সন্দেহভাজন হিসাবে। আপনাকে শুরু করতে হবে একজন মিথ্যাবাদী হিসাবে এবং আপনাকেই প্রমাণ করতে হবে যে এটা সত্যি।"
"প্রত্যেক নারীকেই যে কিছু না কিছুর মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে সেই বিষয় নিয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। এটা সবাই জানে। আর এইদিক থেকেই তিনি বিশ্বের সব নারীর প্রতিনিধিত্ব করছেন।"
"জিসেল পেলিকট এটাকে (মামলাকে) নিজের চেয়ে বড় করে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পুরো বিষয়টাকে সমাজের অংশ হিসাবে আমরা যেভাবে যৌন সহিংসতাকে দেখি, তার সঙ্গে জুড়েছেন তিনি।"
ফরাসি সাংবাদিক জুলিয়েট ক্যাম্পিয়ন আদালত কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসলে তাকে মামলার প্রভাব সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলাম। একটু থেমে চিন্তা করে বললেন, "ওই সমস্ত ভিডিও দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল ... একজন নারী হিসাবে, এটা জটিল এবং আমি ক্লান্ত বোধ করছি।"
তার কথায়, "কিন্তু আমরা আমাদের কাজটা অন্তত করেছি আর এটা নিয়ে কথা বলেছি। খুবই ছোট পদক্ষেপ। এতে বড় কিছু হবে না।"
"আমি আপাতত একমাত্র জিনিসই আশা করতে পারি যে এটা কিছু পুরুষের জন্য গেম চেঞ্জার হবে এবং হয়তো কিছু নারীর জন্যও।"
প্রতি ১০ মিনিটে এক জন নারী প্রাণ হারাচ্ছেন প্রেমিক কিংবা স্বজনের হাতে
বিশ্বে প্রতি ১০ মিনিটে একজন নারী তার প্রেমিক কিংবা পরিবারের সদস্যের হাতে প্রাণ হারাচ্ছেন। জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে এ উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে।
এই হিসাব অনুযায়ী, প্রতি ঘণ্টায় ছয় জন এবং প্রতিদিন গড়ে ১৪০ জন নারী তাদেরই কোনো ঘনিষ্ঠ মানুষের হাতে প্রাণ হারাচ্ছেন। জাতিসংঘের নারী বিষয়ক সংস্থা ইউএনওমেন এবং মাদক ও অপরাধ বিষয়ক দপ্তর ইউএনওডিসির যৌথ প্রতিবেদন অনুযায়ী, শুধু গত বছরই ৫১ হাজার নারীকে পরিকল্পনা করে হত্যা করা হয়েছে। এদের ঘাতক ছিল তাদের প্রেমিক কিংবা পরিবারের কোনো সদস্য।
‘ফেমিসাইড ২০২৩: ঘনিষ্ঠ সঙ্গী/পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নারীর হত্যার বৈশ্বিক পরিসংখ্যান’ শীর্ষক প্রতিবেদনে এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ২০২৩ সালে বিশ্ব জুড়ে ৮৫ হাজার ফেমিসাইডের ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশই ঘটেছে প্রেমিক বা পরিবারের সদস্যদের হাতে। এ
দের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঘটনা ঘটেছে আফ্রিকায়, যেখানে ২১ হাজার ৭০০ নারী নিহত হয়েছেন। এশিয়ায় এ সংখ্যা ১৮ হাজার ৫০০, আমেরিকায় ৮ হাজার ৩০০ এবং ইউরোপে ২ হাজার ৩০০।
ভারতের পতাকায় ‘প্রণাম’ করলে চিকিৎসা পাবে বাংলাদেশিরা
পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ির এক চিকিৎসক বলেছেন, তিনি বাংলাদেশিদের চিকিৎসা দেবেন। কিন্তু এরজন্য ভারতীয় পতাকায় প্রণাম করে তার চেম্বারে প্রবেশ করতে হবে। শিখর বন্দোপাধ্যায় নামে এই চিকিৎসক ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে এ কথা বলেন।
শিখর বন্দোপাধ্যায় বলেন, ‘বাংলাদেশে আমাদের পতাকা অবমাননা করা হয়েছে, যা আমাকে কষ্ট দিয়েছে। আমি রোগীদের ফিরিয়ে দিতে চাই না। কিন্তু যারা আমাদের দেশে আসবে তাদের আমাদের পতাকাকে সম্মান জানাতে হবে।’
পশ্চিমবঙ্গের নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এই চিকিৎসক বলেন, আমি যে সরকারি হাসপাতালে কাজ করি সেখানে কোনো রোগীকেই আমি ফেরাতে পারব না। কিন্তু শিলিগুড়িতে আমার ব্যক্তিগত চেম্বারে আমি জাতীয় পতাকা ঝুলিয়েছি। সেখানে একটি বার্তাও যুক্ত করেছি। যারা আমার মাতৃভূমির পতাকাকে সম্মান জানাবে না তারা আমার কাছ থেকে চিকিৎসাও প্রত্যাশা করতে পারে না।
পতাকার ওপর থাকা বার্তায় লেখা রয়েছে, ‘ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকা আমাদের মাতৃসম। এই পতাকাকে প্রণাম করে চেম্বারে প্রবেশ করবেন। বিশেষত বাংলাদেশ থেকে আগত রোগীরা প্রণাম না করলে এখানে রোগী দেখা হবে না।’
চন্দ্রনাথ অধিকারী নামে অপর এক চিকিৎসক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসকে বলেছেন, তিনিও যে সরকারি হাসপাতালে কাজ করেন সেখানে সবাইকে চিকিৎসা দেবেন। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত চেম্বারে কোনো বাংলাদেশি রোগীকে তিনি দেখবেন না।
উল্লেখ্য, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিতর্কিত হিন্দু পণ্ডিত চিন্ময় দাসকে নিয়ে ভারতীয় মিডিয়ায় অতিরঞ্জিত খবর এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কথা বলায় ঢাকাসহ দেশের বেশ কয়েকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রবেশপথে ভারতের পতাকা এঁকে দিয়েছিলেন শিক্ষার্থীরা।
এরপর পতাকাকে অবমাননা এবং হিন্দুদের ওপর কথিত হামলা বৃদ্ধি নিয়ে বাংলাদেশি রোগীদের চিকিৎসা না দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে কলকাতার একটি হাসপাতাল। এরপর আরও কয়েকটি ভারতীয় হাসপাতাল বলেছে তারা বাংলাদেশিদের চিকিৎসা দেবে না।
ভারতীয় বংশোদ্ভূত কাশ প্যাটেল এফবিআই প্রধান হচ্ছেন
যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-এর পরবর্তী পরিচালক হিসেবে কাশ প্যাটেলকে বেছে নিয়েছেন মার্কিন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। কাশ প্যাটেল ট্রাম্পের একজন ঘনিষ্ট মিত্র এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত।
ট্রাম্প তার সোশ্যাল ট্রুথে লিখেছেন, কাশ একজন চমৎকার আইনজীবী, তদন্তকারী এবং 'আমেরিকা ফার্স্ট' যোদ্ধা। দুর্নীতি উন্মোচন, ন্যায়বিচার এবং আমেরিকান জনগণকে রক্ষা করার জন্য কাজ করেছেন প্যাটেল।
এছাড়া প্রথম মেয়াদে কাশ প্যাটেলের ভূমিকা নিয়েও প্রশংসা করেছেন ট্রাম্প। ২০১৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ট্রাম্প যখন প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তখন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের কর্মকর্তা ছিলেন কাশ। তখন প্রতিরক্ষামন্ত্রীর চিফ অব স্টাফও ছিলেন তিনি।
গত বছরই এক অনুষ্ঠানে কাশ প্যাটেলকে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, তৈরি হও কাশ, তুমি তৈরি হও।
১৯৮০ সালে নিউ ইয়র্কে কাশ প্যাটেলের জন্ম। বেড়ে উঠেছেন গার্ডেন সিটিতে। তার প্রকৃত নাম কাশ্যপ প্রমোদ প্যাটেল। তার বাবা-মা দুজনই গুজরাটি। তারা থাকতেন কানাডায়, পরে পাড়ি জমান যুক্তরাষ্ট্রে।
কাশ ২০০২ সালে ইউনিভার্সিটি অব রিচমন্ড থেকে ইতিহাস ও আইনে ডিগ্রি নেন, দুই বছর পর ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে সনদ নেন তিনি।
আটলান্টিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, কাশ প্যাটেল এমন একজন যিনি ট্রাম্পের জন্য সবকিছু করতে পারেন। এ ছাড়া কাশ জানিয়েছেন, ভারতের সঙ্গে তার গভীর সম্পর্ক আছে।
ক্রীড়া বার্তা
২০২৫ সালে বাংলাদেশের ক্রিকেটের যত ব্যস্ততা
২০২৪ সাল ছিলো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও অনেকগুলো টেস্টের বছর। নারী-পুরুষ মিলিয়েই দেশের ক্রিকেটে ছিলো অনেক ব্যস্ততা। ঠাসা সূচি আছে ২০২৫ সালেও। তবে নতুন বছরে ওয়ানডে সংস্করণে আছে বেশি খেলা, আছে বড় আসর। এই বছর আবার টেস্টের সংখ্যা কম বাংলাদেশের।
দেখে নেওয়া যাক ভবিষ্যৎ সফরসূচির মধ্যে থাকা ২০২৫ সালে বাংলাদেশের ক্রিকেট।
পুরুষ ক্রিকেট
ফেব্রুয়ারি- মার্চে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি
মার্চে জিম্বাবুয়ে সফরে আছে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি।
মে মাসে পাকিস্তান সফরে আছে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি।
জুনে শ্রীলঙ্কা সফরে দুই টেস্ট, তিন ওয়ানডে ও তিনটা টি-টোয়েন্টি আছে।
অগাস্টে বাংলাদেশ সফরে এসে ভারত খেলবে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি।
সেপ্টেম্বরে হতে পারে এশিয়া কাপ (ভেন্যু চূড়ান্ত নয়)
ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলতে আসবে বাংলাদেশে, আছে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি।
নভেম্বরে আয়ারল্যান্ড তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলতে আসবে বাংলাদেশে।
নারী ক্রিকেট
জানুয়ারিতে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ যাবে বাংলাদেশ
অগাস্ট-সেপ্টেম্বরে ভারতে হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ (কোয়ালিফাই করলে সেখানে খেলবে বাংলাদেশ)
ডিসেম্বরে ভারত সফরে তিনটি করে ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি খেলবেন নিগার সুলতানা জ্যোতিরা।
নির্ধারিত এই সূচির দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে আরও এক বা একাধিক সিরিজ আয়োজিত হতে পারে।
আইসিসি নীরব দর্শক, ভারত - পাকিস্তান দুই দলই নিজেদের অবস্থানে অনড়
ধারাবাহিক নাটক চলছে ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজন নিয়ে। ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বেশ পুরোনো। যার কারণে পাকিস্তানের মাটিতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি অনুষ্ঠিত হলে সেখানে খেলতে যাবে না ভারত। সেটা আগেই আইসিসিকে জানিয়ে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই।
যার কারণে এশিয়া কাপের মতো হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি আয়োজনের পক্ষে মত দিয়েছে বিসিসিআই। তাতে মত আছে আইসিসির। তবে এককভাবে টুর্নামেন্ট আয়োজনে অনড় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সেটা না হলে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে অংশগ্রহণ করবে না পাকিস্তান। সে সঙ্গে ভবিষ্যতে ভারতে অনুষ্ঠিত হওয়া সব টুর্নামেন্ট বয়কট করা হবে বলে পিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
যার কারণে টুর্নামেন্টটি আয়োজন নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা সেই ধোঁয়াশা কাটাতে শুক্রবার দুবাইয়ে আইসিসির হেড অফিসে বিসিসিআই এবং পিসিবির কর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছে আইসিসির শীর্ষ কর্তারা। তবে তাতেও হয়নি কোনো সুরাহা। দুই পক্ষই নিজের সিদ্ধান্তের ওপর অনড় অবস্থানে রয়েছে। যার কারণে মাত্র ১৫ মিনিটে শেষ হয় সভা।
অন্যদিকে ২০২৫-এর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে ‘মিনি ওয়ার্ল্ডকাপ’ এই টুর্নামেন্টটি। পাকিস্তান ও ভারতের সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা যায়, দুই বোর্ডই নিজেদের সরকারের সিদ্ধান্তের দিকে তাকিয়ে আছে। এই নিয়ে বিসিসিআইয়ের সহসভাপতি রাজীব শুক্লা বলেছেন যে, তারা বোর্ড পিসিবির সঙ্গে আলোচনা করছে এবং আইসিসিও বিষয়টির সমাধানের চেস্টা করছে।
তবে তিনি জানান, ভারতের সরকার যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটাই তারা মেনে নেবে। তবে পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে এই বিষয়ে শুক্রবার একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'দলের নিরাপত্তার উদ্বেগ রয়েছে। যার কারণে ভারতের পাকিস্তানে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।' তবে পাকিস্তানি গণ্যমাধ্যমগুলোর সূত্রমতে, আজ আবারও বসতে যাচ্ছে আইসিসির সভা। সেখানে নির্ধারণ করা হতে পারে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ভবিষ্যৎ।
Can England bring it home this time?
In the latest episode of The Daily Star’s podcast Pitch Perfect, we bring you an in-depth discussion about the key battles that may shift the balance in the grand finale of the tournament.
শিক্ষা বার্তা
উচ্চশিক্ষায় শিক্ষকদের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের বিকল্প নেই
আমাদের মধ্যে অনেকেই আছে, যারা স্কুল-কলেজে বেশ ভালো রেজাল্ট রাখলেও বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসে কিছুটা হোঁচট খাই। আর ভিনদেশ হলে তো কথাই নেই। ভিন্ন ভাষা থেকে শুরু করে নতুন সংস্কৃতি ও পরিবেশ, না বলা অনেক পার্থক্যই ধরা পড়ে তখন।
যারা বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী, তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই ফান্ডিং হয় কোনো না কোনো অধ্যাপকের মাধ্যমে। এদিক থেকে সামাজিক বিজ্ঞান এবং কলা অনুষদের ফান্ডিং বা স্কলারশিপ ভিন্ন। এই অংশে বেশিরভাগ ফান্ডিংই হয় বিশ্ববিদ্যালয় বা বিভাগের সেন্ট্রাল পর্যায় থেকে। তাই শুরুর দিকে ভিনদেশের শিক্ষার্থী সম্পর্কে অধ্যাপক জানেন কেবল তার অ্যাপ্লিকেশন পর্যায়ে জমা দেওয়া ডকুমেন্টস বা কাগজপত্র থেকেই।
তাই এখানে প্রায় সব অধ্যাপককেই বলতে শুনি, শ্রেণীকক্ষের বাইরে শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো বিকল্প নেই।
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা হয়, একজন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর গবেষণা ও থিসিসের বিষয়ের আগ্রহ পরিবর্তন হয়। কেননা আমাদের দেশে কোর্স বা কারিকুলামে এত বৈচিত্র্য নেই। আবার এখানে নিজ বিভাগের বাইরেও অন্য বিভাগের নির্দিষ্ট কিছু কোর্স নেওয়া যায়। আমার সহপাঠীদের দেখেছি, যোগাযোগ বিভাগে পড়েও অনেকেই মনোবিজ্ঞান বা সাইকোলজি, পাবলিক হেলথ বিভাগ থেকে কোর্স বাছাই করছে। যার ফলে উচ্চশিক্ষার এই সময়টাতে থিসিসের বিষয়েও অনেক পরিবর্তন আসে। আর এই প্রতিটি পর্যায়ে পরামর্শের জন্য প্রয়োজন অধ্যাপকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।
যুক্তরাষ্ট্রে যেহেতু উচ্চশিক্ষা মানেই গবেষণা, তাই সেমিস্টারের শুরু থেকেই গবেষণা, এর মেথড আয়ত্ত করা প্রয়োজন। এখানে প্রায় প্রত্যেক শিক্ষকই বিভিন্ন গবেষণা, প্রকল্পের কাজে যুক্ত থাকেন। তাই নিজের গবেষণা পরিকল্পনা বা কাজের ইচ্ছা প্রকাশ করলে শিক্ষকের সঙ্গে গবেষণা সহকারী হিসেবে কাজ করা যায়। আমার বেশ কিছু সহপাঠী গ্রীষ্মের ছুটির সময়টা গবেষণা সহকারী হিসেবে কাজ করেই তিন মাস পাড় করে দিয়েছেন। যেহেতু এসময় সেমিস্টারের কোনো কোর্স এবং ফান্ড কোনোটাই থাকে না, তাই এই গবেষণার কাজটি অভিজ্ঞতা অর্জন ছাড়াও আয়ের উৎস হিসেবে নেয় অনেকে।
আর একজন আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীর ভিন্ন এক পরিবেশে নানা প্রতিকূলতার সম্মুখীন হওয়াটাও স্বাভাবিক। দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে থাকা বন্ধুদের কিছু বিষয় দেখে যেমন সহজ মনে হয়েছে, নিজে যখন বাড়ি ছেড়ে প্রথমবারের মতো বিদেশে পড়তে এসেছি, সামান্য বিষয়গুলোও অনেক ঝামেলার মনে হয়েছে।
আমরা নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি দেওয়ার অনেক পরিকল্পনাই করি খুব উৎসাহ নিয়ে, কিন্তু নতুন এক দেশে শুরুর সময়টা প্রতিকূলই বটে। অন্তত যে এই অবস্থার মধ্য দিয়ে যায়, যাকে কখনো বাড়ি ছেড়ে এই আত্মীয়-পরিচয়হীন অঞ্চলে থাকতে হয়নি, তার জন্য তো অবশ্যই। অনেক ক্ষেত্রে এই ছোটখাটো বিষয়গুলো বা অসুস্থতা, হেলথ ইনস্যুরেন্সের নানা পলিসির কারণে পড়ালেখায় প্রভাব পড়ে। আর এখানে গ্রেডিং গেল মানে তো পুরো ফান্ডিংই গেল। তাই নিজের এই বিষয়গুলো সুপারভাইজার বা অ্যাডভাইজারকে জানিয়ে রাখা নিরাপদ। এখানকার শিক্ষকরাও সাধ্যমত চেষ্টা করেন একজন শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য, তার সার্বিক বিষয়ে সহযোগিতা করতে। তাই বলা চলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগাযোগের কোনো বিকল্প নেই।
নতুন বই বিতরণ, সবাইকে দিতে না পেরে উপদেষ্টার দুঃখ প্রকাশ
ইংরেজি নববর্ষের প্রথম দিনে নতুন বই হাতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত শিক্ষার্থীরা। তবে দেশের সব প্রান্তের সব শিক্ষার্থীর হাতে একযোগে নতুন বই তুলে দিতে পারেনি সরকার।
এ নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ দুঃখ প্রকাশ করেছেন।
আজ বুধবার সকালে রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'নতুন বছরের প্রথম দিনে সারা দেশের সব শিক্ষার্থীর হাতে নতুন বই তুলে দিতে না পেরে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে আমরা আন্তরিক দুঃখিত।'
এর আগে, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনটিসিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান বলেন, 'মাত্র আড়াই মাসে ৪৪১টি বই পরিমার্জন করেছি। ছয় কোটি বই গেছে। চার কোটি ট্রাকে ওঠার অপেক্ষায়।'
তিনি বলেন, 'আগামী ৫ জানুয়ারি প্রাথমিক ও দশম শ্রেণির সব বই, ১০ জানুয়ারি মাধ্যমিকের আটটি বই এবং ২০ জানুয়ারির মধ্যে সব বই পাঠানোর চেষ্টা করব।'
এ বছর প্রায় ৪১ কোটি নতুন বই বিতরণ করা হবে বলেও জানান তিনি।
পাঠ্যবইয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদের নাম ভুল ছাপা হয়েছে
পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে জুলাইর ছাত্র-জনতা গণঅভ্যুত্থানের এক শহীদের ভুল নাম ছেপেছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)।
বাংলা পাঠ্যবইয়ের এক অংশে লেখা হয়েছে, বিক্ষোভ চলাকালীন সময় নাহিয়ান নামে একজন নিহত হয়েছেন। তবে এনসিটিবির কর্মকর্তারা বলেছেন, তারা প্রকৃতপক্ষে নাফিসা হোসেনের কথা উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন।
একই বইয়ে বলা হয়েছে, 'পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রংপুরে ছাত্রনেতা আবু সাঈদ দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়ান। পুলিশ তাকে খুব কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করে। এতে আন্দোলন সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সারা দেশের মানুষ রাস্তায় নেমে আসে। বিশাল এক গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয়।'
'ঢাকার উত্তরায় শিক্ষার্থী মীর মুগ্ধ আন্দোলনরত সবাইকে পানি বিতরণ করতে করতে নিহত হন। নিহত হন (গোলাম) নাফিজ, নাহিয়ান, আনাসসহ অগণিত প্রাণ। মায়ের কোলের শিশু, বাবার সাথে খেলতে থাকা শিশু, রিকশাওয়ালা, শ্রমিক, কৃষক, ফেরিওয়ালা, চাকুরিজীবী, মা, পথচারী কেউ বাদ যায় না। সারা দেশে হত্যা করা হয় হাজারো মানুষকে'।
দ্য ডেইলি স্টার উল্লেখিত তিন শহীদ—নাফিজ, নাহিয়ান ও আনাসের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানতে চাইলে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সূত্র জানায়, তারা শহীদদের মধ্যে একজন নারীর নাম যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে তারা টঙ্গীর সাহাজউদ্দিন সরকার উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের এইচএসসি পরীক্ষার্থী নাফিসার নাম অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সাভারে বিক্ষোভ চলাকালীন সময় আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের গুলিতে নিহত হন নাফিসা।
'আমি নাহিয়ান নামে কাউকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেইনি', জানান ওই সূত্র।
আদৌ জুলাইর গণঅভ্যুত্থানে নাহিয়ান নামে কেউ শহীদ হয়েছেন কী না, তা নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
উৎস আরও জানান, ইতোমধ্যে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবইগুলো ছাপাখানায় পাঠানো হয়েছে।
এ বিষয়ে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক এ কে এম রিয়াজুল হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি স্বীকার করেন, তারাও এই ভুলটি চিহ্নিত করেছেন।
তিনি বলেন, 'আমরা এ বিষয়টির সুরাহা করব। আজ স্কুলগুলোতে যে পিডিএফ সংস্করণ পাঠানো হবে, সেটায় আমরা এই ভুলটি সংশোধন করে দেব। স্কুলগুলোতেও আমরা শিগগির একটি সংশোধনী পাঠাব।'
এনসিটিবি কর্মকর্তারা জানান, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় বেশ কয়েকটি পত্রিকায় নৌবাহিনী কলেজের ১৬ বছর বয়সী শিক্ষার্থী গোলাম নাফিজের ছবি ছাপা হয়েছিল। ওই ছবিতে দেখা যায় পুলিশের গুলিতে রক্তাক্ত নাফিজ একটি রিকশার পাদানিতে নিশ্চল অবস্থায় পড়ে আছেন। এ সময় তার মাথায় বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা বাধা ছিল। এই ছবিটি আবু সাঈদ ও মুগ্ধের ছবির মতো গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম প্রতীকে পরিণত হয়।
ইসলামী শিবিরকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মেরামতের যুদ্ধে প্রস্তুত থাকতে হবে: জামায়াত আমির
ইসলামী ছাত্রশিবিরকে আরেকটি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, সেই যুদ্ধটা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মেরামত করার যুদ্ধ।
'শিক্ষা যেহেতু জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষায় বেশি আঘাত করা হয়েছে বেশি। উদ্দেশ্যহীন মানহীন একটা শিক্ষা ব্যবস্থা দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেটা জাতির খুব কম প্রয়োজনে আসছে। এখানে গবেষণা নাই, চর্চা নাই, উৎকর্ষ নাই। নৈতিকতা নাই, দুনিয়ার সঙ্গে তাল মিল নাই। সবকিছুকে একদম তছনছ করে দেওয়া হয়েছে।'
তিনি আজ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্রশিবির আয়োজিত সদস্য সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।
শফিকুর রহমান বলেন, 'যেহেতু জাতির মেরুদণ্ড, সেখানে তোমাদের শপথ নিতে হবে। আর কোনো চাপাতি কোম্পানিকে, কোনো গাঁজাখোরকে ওখানে ঢুকতে দেওয়া হবে না। হাতে অস্ত্র নিয়ে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। গণরুম যারা কায়েম করে তাদের ওখানে ঢুকতে দেওয়া হবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যারা টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি করে, তাদের ঠিকানা ওখানে হবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুধু শিক্ষা গবেষণা থাকবে। এই দায়িত্ব তোমাদের নিতে হবে।'
তিনি জাতীয় ঐক্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় বা জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয় এরকম সকল হঠকারী আচরণ থেকে সকলকে বিরত থাকার আহ্বান জানান।
আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সকল হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করে তিনি বলেন, 'এই বিচার জাতি দেখতে চায়। একজন অপরাধীও যেন বাঁচতে না পারে সেটা দেখতে চায়। যত সময়ই লাগুক, বিচার করতে হবে।'
তিনি বলেন, 'এরা (আওয়ামী লীগ) রাজনৈতিক দল হতে পারে না। যারা ক্ষমতায় বসে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে পারে না, নিজের দেশের মানুষকে হত্যা করে গদি রক্ষার জন্য, তারা কখনো রাজনৈতিক দল হতে পারে না। তারা একটি সন্ত্রাসী দল। সরকার তাদের ছাত্র সংগঠনকে নিষিদ্ধ করেছে। আবরার ফাহাদসহ অসংখ্য মানুষকে হত্যা করে মায়ের বুক খালি করেছে তারা।'
'এরা প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অস্ত্রাগারে পরিণত করেছিল। মদের বোতল আর অস্ত্র দিয়ে ভরে রেখেছিল। গণরুম তৈরি করে নির্যাতন চালাত। নামাজী ছেলেদের শিবির ট্যাগ দিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত।'
তিনি আরও বলেন, 'এটা শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর বুয়েট নয়, সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে তারা চরের মতো দখল করে নিয়েছিল। এমনকি আমাদের মেয়েদের বিদ্যাপিঠগুলোও তারা কলুষিত করেছিল।'
তিনি বলেন, '৭১ এ একটা স্বাধীনতা এসেছিল। এ জাতি এনেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার মর্মবাণী ডুকরে কেঁদেছিল। কারণ স্বাধীনতার ফসল বাংলাদেশের জনগণের ঘরে উঠেনি। একটা গোষ্ঠী এটা হাইজ্যাক করেছিল। অন্য দেশের হাতে এটা তুলে দিয়েছিল। তার প্রমাণ পাশের দেশের প্রধানমন্ত্রী ২৪ এর বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা দিতে গিয়ে ভারতীয় বাহিনীকে বলেছেন এটা ভারতের দিবস।'
স্বাস্থ্য বার্তা
ভারতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: দেশের স্বাস্থ্যসেবা সংস্কারের এখনই সময়
বাংলাদেশিদের জন্য ভারতের ভিসা নিষেধাজ্ঞাকে প্রাথমিকভাবে বাধা হিসেবে দেখা হলেও এটি দেশের স্বাস্থ্য খাতকে শক্তিশালী করা ও রোগীদের আস্থা ফিরিয়ে আনার সুবর্ণ সুযোগ হয়ে উঠেতে পারে।
প্রতি বছর প্রায় সাড়ে তিন লাখ বাংলাদেশি ভারতে চিকিৎসা নিতে যান। ভিসা বিধিনিষেধ দেশের স্বাস্থ্য খাতে সমস্যাগুলোর সমাধান ও বিদেশে যাওয়া রোগীদের দেশে চিকিৎসা দেওয়ার সুযোগ এনে দিয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে এই সুযোগে উঠে দাঁড়াতে ও দেশবাসীর মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন।
২০২০ সালে গুরুতর অসুস্থ মিরপুরের সানজিদার (আসল নাম নয়) কথা ধরা যেতে পারে। ডিম্বাশয়ের সিস্ট অপসারণের জন্য ঢাকার গ্রিন লাইফ হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পর তার বায়োপসি রিপোর্টে দুঃসংবাদ পাওয়া যায়: তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত।
তাকে কেমোথেরাপির পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। তিনি চিকিৎসকের সুপারিশ অনুসারে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গেলে দেখেন যে তার আগের পরীক্ষাগুলোকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। সেসময় এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে তার চিকিৎসক বিষয়টিকে মোটেও গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আতঙ্কিত ও হতাশ হয়ে তার পরিবার বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
সানজিদা মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে গিয়েছিলেন। যেখানে চিকিৎসকরা তার আগের চিকিত্সা পর্যালোচনা করে রোগ নির্ণয় করেছিলেন। তারা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ঢাকায় অস্ত্রোপচার ভুল ছিল। উপযুক্ত অপারেশন হলে তার ক্যানসার আগেই দূর করা যেত।
মুম্বাইয়ে আরও একটি অস্ত্রোপচার ও তিন দফা কেমোথেরাপি শেষে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। বর্তমানে তিনি নিয়মিত ওষুধ খান এবং ফলোআপের জন্য প্রতি ছয় মাস পর পর ভারতে যান। তার এই চরম দুর্গতি এ কথাই প্রমাণ করে যে, সানজিদা নিজ দেশে যথাযথ চিকিৎসা পাননি। তিনি এ দেশের চিকিৎসকদের অমনোযোগিতা ও অপেশাদারিত্বের কথা তুলে ধরে জানান যে ভারতের চিকিৎসকরা রোগীদের অনেক যত্ন নিয়ে দেখেন।
সানজিদা দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, 'যাতায়াতের খরচ বেশি হলেও দেশের তুলনায় ভারতে কম টাকায় চিকিৎসা নেওয়া যায়। সেখানকার চিকিৎসা তুলনামূলক বিশ্বাসযোগ্য।'
এমন ঘটনা শুধু সানজিদারই নয়। ২০১৯ সালে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা শহিদুর রহমান (৬৯) বুকে ব্যথা অনুভব করলে চিকিৎসকের কাছে যান। ঢাকার দুই বড় হাসপাতাল তার হার্টে তিনটি ব্লক আছে জানিয়ে স্টেন্ট বসানোর পরামর্শ দেয়। তাদের কথায় সন্দেহ হয় শহিদুরের। তিনি প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. দেবী শেঠির পরামর্শ নিতে বেঙ্গালুরু যান। পরীক্ষার পর দেখা যায় হার্টে ব্লক নেই। তাকে ওষুধ দেওয়া হয়। এরপর তার আর বুকের ব্যথা হয়নি। তিনি দেশের স্বাস্থ্যসেবায় আস্থা হারান।
আস্থার সংকট
বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো আধিপত্য বিস্তার করে আছে। তৃতীয় শ্রেণির হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সংখ্যা অনেক বেশি।
সানজিদা ও শহিদুরের ঘটনাগুলো দেশের স্বাস্থ্যখাতে গভীর সংকটের দুইটি উদাহরণ মাত্র। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রোগীদের আস্থাহীনতায় জর্জরিত। আপাতদৃষ্টিতে দেশের স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো শক্তিশালী বলে মনে হয়। দেশে ৫৬৬টি সরকারি হাসপাতাল আছে। এর মধ্যে ৩৭টি রাষ্ট্র পরিচালিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার।
বেসরকারি বিনিয়োগের ফলে তৃতীয় শ্রেণির হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সংখ্যা বেড়েছে। তাই স্বাস্থ্যসেবায় অগ্রগতি ধোঁয়াশা তৈরি করেছে। অনেক বাংলাদেশি এখনো বিদেশে চিকিত্সা নিতে বাধ্য হচ্ছেন। রোগীদের বিশ্বাস দেশের বর্তমান পরিষেবা তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে না।
রোগীদের বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার কারণ অনেক। দেশে চিকিৎসকরা তাড়াহুড়ো করে পরামর্শ দেন, রোগ নির্ণয়ে ত্রুটি থাকে। চিকিত্সা খরচ অনেক। এ ছাড়াও, রোগীদের প্রতি চিকিত্সকদের উদাসীনতার অভিযোগ আছে। অনেকের অভিযোগ, চিকিৎসকরা রোগীদের সঙ্গে 'অমানবিক' আচরণ করেন।
বিপরীতে, অনেক রোগীর মতে ভারত চিকিত্সা সেবায় শুধু যে দক্ষ তা নয়। সেখানকার চিকিৎসকরা রোগীদের এমন যত্ন নেন যে তারা সেই আচরণকে মানবিক বোধ করেন।
ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিন প্রকাশিত ২০২৩ সালের সমীক্ষা অনুসারে—বাংলাদেশি রোগীরা প্রাথমিকভাবে কার্ডিওলজি (১৪ শতাংশ), অনকোলজি (১৩ শতাংশ), গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি (১১ শতাংশ) ও অন্যান্য জটিল সমস্যার চিকিৎসা করাতে ভারতে যান।
প্রতিবেদনে দেখা গেছে—দক্ষ বিশেষজ্ঞ, ফলো-আপ ও যত্নসহ ভারতের স্বাস্থ্যসেবা বছরে আনুমানিক তিন লাখ থেকে সাড়ে তিন লাখ বাংলাদেশি রোগী টানে। কলকাতা, চেন্নাই, ভেলোর ও মুম্বাইয়ে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি রোগী যান।
স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রুমানা হক ডেইলি স্টারকে বলেন, 'দেশের স্বাস্থ্যসেবায় পর্যাপ্ত দক্ষ চিকিৎসক ও প্রযুক্তিবিদের অভাব। বিশেষ করে ক্যানসার ও অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মতো জটিল রোগের জন্য। আমাদের দক্ষ চিকিৎসক থাকলেও তারা অনেক চাপে থাকেন। তাই রোগীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী সেবা দিতে পারছেন না।'
ভারত ও থাইল্যান্ড প্রথম পছন্দ হওয়ায় বাংলাদেশি রোগীরা বিদেশে চিকিৎসার জন্য বছরে পাঁচ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি খরচ করেন। রুমানা হক মনে করেন, 'দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো যদি রোগীদের সেবা ভালোভাবে দেন তাহলে বিদেশে যাওয়া অনেক কমানো যেতে পারে।'
এভারকেয়ার হসপিটালস ঢাকার ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি বিশেষজ্ঞ তামজেদ আহমেদ ডেইলি স্টারকে বলেন, 'গত দুই থেকে তিন মাসে ভারতে পরামর্শ নিতে যাওয়া রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। ভারতের ভিসা বিধিনিষেধ সত্ত্বেও তা বাড়ছে।'
স্কয়ার হাসপাতালের চিফ অপারেটিং অফিসার মো. এসাম ইবনে ইউসুফ সিদ্দিকী এই বিধিনিষেধের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবকে ঘিরে অনিশ্চয়তার কথা তুলে ধরে ডেইলি স্টারকে বলেন, 'গত তিন বছরে স্কয়ার হাসপাতালে রোগীর সংখ্যায় তেমন পরিবর্তন হয়নি।'
পদ্ধতিগত সংকট ও রোগীর অসন্তুষ্টি
রোগীরা প্রায়ই বাংলাদেশের অপ্রতুল ডায়াগনস্টিক সুবিধার কথা বলেন। এমনকি উন্নত যন্ত্রপাতিতে সাজানো বেসরকারি হাসপাতালগুলো কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাব আছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল হামিদ ডেইলি স্টারকে বলেন, 'যথাযথভাবে রোগ নির্ণয়ে অসুবিধা, পরামর্শের জন্য চিকিৎসকের অপর্যাপ্ত সময় ও উদাসীন আচরণ রোগীদের আস্থা নষ্ট করেছে। ভারতের চিকিৎসকরা রোগীর সঙ্গে আলোচনায় দক্ষতা অর্জন করেছেন। তাদেরকে মানসিক সহায়তা দেন। বাংলাদেশে চিকিৎসকরা তাড়াহুড়ো করেন।'
করোনা মহামারির সময় যখন বিদেশে যাওয়া সীমিত ছিল তখন বাংলাদেশি রোগীদের দেশে চিকিৎসা নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তখন অনেকে মানসম্পন্ন চিকিৎসা পেয়েছিলেন। তবে অবহেলা ও অদক্ষতার দীর্ঘ ইতিহাস রোগীদের বিদেশে যেতে বাধ্য করছে।
সংস্কারের আহ্বান
চিকিৎসা খাতের সংশ্লিষ্টরা এসব অসঙ্গতির কথা স্বীকার করেছেন। ল্যাবএইড হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা এএম শামীম ডেইলি স্টারকে বলেন, 'বাংলাদেশি চিকিৎসকরা কারিগরিভাবে দক্ষ হলেও তাদের আচরণ ভালো করতে হবে। রোগীদের আরও বেশি সময় দিতে হবে। জটিল রোগের চিকিৎসা করার সক্ষমতা আমাদের আছে, কিন্তু আচরণ ও পরামর্শ যথাযথ না হলে রোগীদের আস্থা নষ্ট হয়।'
একইভাবে আইচি মেডিকেল গ্রুপের অধ্যাপক মো. মোয়াজ্জেম হোসেন পদ্ধতিগত সংস্কারের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমাদের দক্ষ প্রযুক্তিবিদ, অভিন্ন খরচ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। রোগীদের এমন যত্ন দেওয়া দরকার যাতে তারা আত্মবিশ্বাসী হন এবং হাসপাতালগুলোকে তাত্ক্ষণিক মুনাফার তুলনায় রোগী-কেন্দ্রিক পরিষেবাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।'
ভারতের ভিসা বিধিনিষেধ অসুবিধাজনক হলেও বাংলাদেশকে চিন্তা-ভাবনা ও সংস্কারের বিরল সুযোগ এনে দিয়েছে। এটি রোগীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা, তাদের যত্নে সময় দেওয়া ও বিদেশে যেতে বাধ্য করে যেসব কারণ সেগুলো দূর করার সুযোগ এনে দিয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, এসব সমস্যার সমাধান না হলে দেশের মানুষ বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার ওপর স্থায়ীভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।
ক্যান্সারের বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি কী, এগুলো কাজ করে?
অনেক ক্ষেত্রে সুপরিচিত ব্যক্তিরাও দাবি করেছেন, ক্যান্সার উপশমে প্রথাগত চিকিৎসার পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন বা বিকল্প চিকিৎসায় তারা উপকৃত হয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিরাময়ও হয়েছেন।
তবে ক্যান্সারের চিকিৎসা দেয় এমন অনেক দাতব্য সংস্থা (চ্যারিটি) বলছে, কোনো থেরাপি বা বিকল্প উপায়ে ক্যান্সার চিকিৎসার মেডিক্যাল প্রমাণ তাদের কাছে নেই। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, এই বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি বা থেরাপিগুলো আসলে কী এবং এগুলোর ব্যবহার কীভাবে বাড়ছে?
ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও রাজনীতিবিদ নভজিৎ সিং সিধু গত নভেম্বরে জানান, তার স্ত্রী এখন পুরোপুরি ক্যান্সারমুক্ত। নিত্যদিনের খাবারে লেবুপানি, কাঁচা হলুদ, অ্যাপল সিডার ভিনেগার (সিরকা), নিমপাতা, তুলশি, মিস্টি কুমড়া, ডালিম, আমলকি, বিটরুট ও আখরোটের মতো উপাদান রেখেছিলেন তিনি।
সিধুর এই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর ভারতের দুই শতাধিক ক্যান্সার রোগ বিশেষজ্ঞ এক যৌথ বিবৃতি দেন।
এতে তারা দাবি করেন, চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রাকৃতিক উপদানগুলোর প্রভাব নিয়ে গবেষণা চলছে, তবে এগুলোর ব্যবহারে সমর্থন করার মতো প্রমাণ তাদের হাতে নেই।
বরং 'অপ্রমাণিত' এসব উপাদান বা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে গিয়ে ক্যান্সারের মূল চিকিৎসা বিলম্বিত না করতেও বিশেষজ্ঞরা সবার প্রতি আহ্বান জানান ওই বিবৃতিতে।
অস্ট্রেলিয়ান ডেল এলি ম্যাকফারসন গত সেপ্টেম্বরে জানান, সাত বছর আগে তার স্তন ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। কেমোথেরাপির পরিবর্তে তিনি বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন।
চিকিৎসকরা বলছেন, স্তন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কেমোথেরাপির পাশাপাশি বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে আকুপাংচার (শরীরের বিভিন্ন পয়েন্টে চাপ দিয়ে বা সুঁচ ফুটিয়ে চিকিৎসার পদ্ধতি), যোগ ব্যায়াম, মেডিটেশন (শরীর ও মনে শিথিল করার বিশেষ পদ্ধতি) ব্যবহার করেন অনেকে।
এগুলো ব্যথা দূর করতে এবং রোগীকে ভালো বোধ করতে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট বাদ দিয়ে কেবল ডায়েটে বিশেষ কোনো প্রাকৃতিক উপাদান বা মিনারেল, ভিটামিন যোগ করে নিরাময় লাভের চেষ্টার ব্যাপারে চিকিৎসকরা সতর্কও করে দিয়েছেন।
দাতব্য সংস্থাগুলো দাবি করছে, এসব বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির কোনো কোনোটা ক্ষতিকর হতে পারে বা মারাত্মক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এমনকি মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টে বিঘ্নও ঘটাতে পারে।
ক্যান্সার বিষয়ক মেডিক্যাল জার্নাল জামা অঙ্কোলজিতে ২০১৮ সালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দাবি করা হয়, বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করার কারণে রোগীদের ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে যাওয়ার হার কমে আসার সম্পর্ক রয়েছে।
কিন্তু এরপরও ক্যান্সার আক্রান্ত অনেকে এসব পদ্ধতির ওপর নির্ভর করছেন। এসব পদ্ধতির জনপ্রিয়তাও বাড়ছে।
ক্যান্সার চিকিৎসা সেবাদানকারী ব্যক্তিদের সংস্থা আমেরিকান সোসাইটি অব ক্লিনিক্যাল অঙ্কোলজি (এএসসিও)-এর এক জরিপে জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৪০ শতাংশের ধারণা বিকল্প পদ্ধতির চিকিৎসায় ক্যান্সার নিরাময় সম্ভব।
অনলাইনে 'ক্যান্সার-নিরাময়কারী' ডায়েট নির্দেশ করে তৈরি ভিডিওগুলো লাখ লাখ মানুষ দেখছেন এবং অ্যামাজনে এ ধরনের বইগুলো বিক্রি তালিকার শীর্ষে উঠে আসছে।
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে (আগের টুইটার) একটি থ্রেড ব্যাপক হারে শেয়ার করা হয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে প্রধানত খাদ্য তালিকায় পরিবর্তন এনেই ক্যান্সার 'প্রাকৃতিকভাবে' নিরাময় করা সম্ভব। ৪৮ ঘণ্টায় এই থ্রেডে দুই লাখ লাইক পড়ে।
ক্যান্সারকে 'অনাহারে' রাখতে রোগীদের উপবাস বা না খেয়ে থাকার কথা বলা হয় এতে। আরও বলা হয়, নির্দিষ্ট কিছু খাবার খাওয়ার মাধ্যমে 'ডিএনএ-কে প্রভাবিত' করে 'স্টেম সেলকে শক্তিশালী' করা যায়।
ম্যাকমিলান নামে একটি ক্যান্সার চ্যারিটি বলছে, কোনো বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বনের আগে ক্যান্সার চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
বিকল্প পদ্ধতির জনপ্রিয়তা কেন বাড়ছে?
কোনো ধরনের প্রমাণ ছাড়াই বিকল্প পদ্ধতি বা থেরাপিগুলোকে 'অলৌকিক আরোগ্য' বলে প্রচার করা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।
ব্রিটিশ ক্যান্সার সার্জন ডক্টর লিজ ও'রিয়োর্ডান বলছেন, "ক্যান্সার একটি আতঙ্ক। এর ঝুঁকিসহ অন্যান্য বিষয়ে বলতে হবে আমাদের। রোগীরা আশা চান, আরোগ্যের অঙ্গীকার চান। কিন্তু মূলধারার এক চিকিৎসক সেটা দিতে পারেন না।"
তথাকথিত এসব নিরাময় পদ্ধতিকে ব্যথাহীন বা প্রাকৃতিক- এরকম তকমা দেওয়া হয়, তবে আসলে এগুলো ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের অবস্থা আরও খারাপ করতে পারে এবং মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টকে বিঘ্নিত বা মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে।
আরেকটি কারণ হলো, ভালো মানের ক্যান্সার চিকিৎসা বিশ্বের অনেকের কাছেই সহজলভ্য নয় এবং এটি বেশ ব্যয়বহুল।
ডক্টর লিজ ও'রিয়োর্ডান বলছেন, "টাকা যেখানে একটি ইস্যু সেখানে তুলনামূলক সস্তা পদ্ধতিগুলো খুবই আকর্ষণীয় মনে হতে পারে। আমার দুশ্চিন্তা হলো, ঝুঁকিপূর্ণ লোকগুলোকে মানুষ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছে এবং প্রয়োজন নেই এরকম অনেক পণ্যও তাদের কাছে বিক্রি করছে।"
ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়, আফ্রিকা অঞ্চলে ক্যান্সার ও এর চিকিৎসা নিয়ে সচেতনতার অভাব অনেক বেশি। এছাড়া প্রশিক্ষিত চিকিৎসা সেবাদানকারীর সংকটও রয়েছে। মানুষের চিকিৎসা বিমার হারও কম। ফলে বিকল্প বিভিন্ন পদ্ধতির ওপর মানুষের নির্ভরতা অনেক বেশি।
এরকম চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর নির্ভরতা অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতির সঙ্গেও জড়িত।
আফ্রিকা, এশিয়া ও ভারতে চিকিৎসার অনেক প্রাচীন পদ্ধতির চল রয়েছে এবং দার্শনিক ব্যাখ্যার কারণে এগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতাও বেড়েছে। চীনের প্রচলিত কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি ও আয়ুর্বেদ কোনো কোনো রোগের উপশমে কাজ করে বলে প্রমাণ যদিও রয়েছে, তবে ক্যান্সারের চিকিৎসায় এগুলোর সহায়ক ভূমিকার প্রমাণ অপ্রতুল।
বিশ্বে বহুল প্রচলিত বিকল্প থেরাপি ও ডায়েট কোনগুলো?
আয়ুর্বেদিক 'চিকিৎসা'
আয়ুর্বেদ হলো প্রাচীন ভারতীয় এক চিকিৎসা পদ্ধতি। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক উপদানের ব্যবহার করে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থান টিপে মূলত এই চিকিৎসা দেওয়া হয়। বিশ্বব্যাপী দিনে দিনে এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ২০২৮ সাল নাগাদ এর বাজার এখনকার তিনগুণ হয়ে যেতে পারে বলে মার্কেট রিসার্চ ফিউচারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
আয়ূর্বেদে ভারতীয় উপমহাদেশে বহুল উৎপাদিত মশলা হলুদকে এমন এক পণ্য বিশ্বাস করা হয়, যার ক্যান্সার নিরাময়ের গুণ আছে।
স্বাস্থ্য বিষয়ক জার্নাল ল্যানসেটের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হোমিওপ্যাথি, বায়োপ্যাথি, নিউরোপ্যাথি বা হার্বাল পদ্ধতি, ঘরোয়া প্রতিকার, গমের চারা দিয়ে বা পানি দিয়ে চিকিৎসা, আকুপাংচারের মতো নানা পদ্ধতির ওপর নির্ভরতা রয়েছে ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকাগুলোয়।
এর কোনো কোনোটায় ব্যথা-বেদনা হয়তো লাঘব হয়, কিন্তু ক্যান্সার চিকিৎসায় এসবের ভূমিকা নেই বলে মনে করেন ডক্টর ও'রিয়োর্ডান।
ক্যান্সার সংক্রান্ত চ্যারিটি ক্যান্সার রিসার্চ ইউকে বলছে, হলুদের একটি উপাদান যার নাম কারকিউমিন, এটি ক্যান্সার সেল মেরে ফেলতে পারে, তবে এটি ঘটতে পারে নির্দিষ্ট কয়েক ধরনের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে।
তবে এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন। হলুদ বা কারকিউমিন ক্যান্সার প্রতিরোধ বা নিরাময় করতে পারে এর কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই।
চীনে প্রচলিত চিকিৎসাবিদ্যা
ক্লিনিক্যাল অঙ্কোলজি জার্নালে একটি গবেষণার রিভিউ আর্টিক্যালে বলা হয়েছে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক জায়গায় ক্যান্সার চিকিৎসায় চীনের প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতি (ট্যাডিশনাল চায়নিজ মেডিসিন বা টিসিএম) বেছে নেওয়ার একটা চল বাড়তে দেখা যাচ্ছে।
কিন্তু এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা নিয়ে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের কমই প্রশ্ন করতে দেখা গেছে।
টিসিএম হলো এমন এক বিষয় যেখানে আকুপাংচার, মেসেজ থেরাপি, হার্বাল থেরাপি এবং তাই চি (এক ধরনের মার্শাল আর্ট) এর সবগুলোই ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের লতাপাতা থেকেও শত শত রকেমর নির্জাস নেওয়া হয়।
ডক্টর লিজ ও'রিয়োর্ডান বলছেন, চিকিৎসকের পরামর্শে মেডিক্যার ট্রিটমেন্টের সহায়ক হিসেব টিসিএম ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে কোনো কোনো হার্বাল উপাদান মূল চিকিৎসাকে বিঘ্নিত করতে পারে এমন ঝুঁকি রয়েছে।
ডায়েট পরিবর্তন
কিটো (খাদ্য তালিকায় শর্করা কমিয়ে আমিষ বাড়িয়ে দেওয়ার পদ্ধতি), ভেগান (ভেজিটেরিয়ান বা শাকসবজিনির্ভর খাদ্যতালিকা) বা উপবাস কেন্দ্রিক বিভিন্ন খাদ্যাভ্যাস বিশ্বে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। ক্যান্সারকে 'অনাহারে' রাখতে ডায়েট নিয়ন্ত্রণের কথাও বলা হচ্ছে।
ক্যান্সার গবেষক ডক্টর ডেভিড রবার্ট গ্রিমস বিবিসিকে বলছেন, "আপনি ক্যান্সারকে অনাহারে রাখতে পারবে না, বরং কেবল নিজের শরীরকে না খাইয়ে রাখতে পারবেন। এই প্রক্রিয়ায় আপনি যদি ওজন হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েন তখন ক্যান্সারের প্রভাব আরও মারাত্মক হতে পারে।"
ঝুঁকি বা ক্ষতির কথা চিন্তা না করেই অনেক রোগী এরকম বিভিন্ন খাদ্যাভ্যাসে ঝুঁকে পড়ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
ভারতের পাঞ্জাবের মোহনদাই অসওয়াল হসপিটালের ক্যান্সার চিকিৎসক ডক্টর কানুপ্রিয়া ভাটিয়া ক্যান্সার রোগীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এধরনের প্রচারণায় প্রভাবিত না হতে।
তিনি বলেন, "নিজ উদ্যোগে (ক্যান্সার থেকে মুক্তি পেতে) কোনো কিছু খেতে বা পান করতে শুরু করবেন না যেটা পরে ক্ষতির কারণ হতে পারে।"
ফেনবেনডাজোল
বিভিন্ন প্রাণীর শরীরে পরজীবীর সংক্রমণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এই ফেনবেনডাজোল ওষুধটি। অন্যান্যা বিকল্প থেরাপির সঙ্গে এই ওষুধটি সেবন করে ক্যান্সারমুক্ত হয়েছে, এক মার্কিন ব্যবসায়ী এই দাবি করার পর ক্যান্সার চিকিৎসায় এর জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে যায়।
তবে প্রথমে তিনি বলেননি যে তিনি ক্যান্সার চিকিৎসার অন্যান্য ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালেও অংশ নিচ্ছিলেন।
দক্ষিণ কোরিয়া এই ওষুধটি এত পরিমাণেই বিক্রি হয় যে মজুত ফুরিয়ে যায়। সেবনকারীদের অনেকে সোশাল মিডিয়ায় নিজেদের অভিজ্ঞতার জানাতে শুরু করেন, যদিও পরে এক কৌতুকাভিনেতা ও গায়ক দাবি করেন ওষুধটি তার ওপর কার্যকরী ছিলো না, যে কারণে তিনি এটি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।
ক্যান্সার রিসার্চ ইউকে জানিয়েছে, এই ওষুধের কোনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি এবং এর নিরাপত্তার দিকটও প্রমাণিত নয়।
গ্রাভিওলা
গ্রাভিওলা গাছের ফল, পাতা ও ছাল অনেককাল ধরে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে নানা রোগের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কোনো কোনো সংক্রমণের ক্ষেত্রে এর কার্যকারিত প্রমাণিতও হয়েছে।
স্থানীয়ভাবে এবং ইন্টারনেটে এমন তথ্যও ছড়িয়ে পড়ে যে ক্যান্সার আরোগ্যে গ্রাভিওলার ফলের ভূমিকা আছে। এমনকি সোশাল মিডিয়ার কিছু পোস্টে দাবি করা হয়, কেমোথেরাপির চেয়েও এই ফল দশ হাজার গুণ বেশি কার্যকর।
বিভিন্ন ক্যান্সার চ্যারিটি ও ফ্রেঞ্চ ক্যান্সার ইনস্টিটিউট বলছে, ক্যান্সার দূর করার কোনো 'মিরাকল ফুড' বা 'অলৌকিক খাবার' নেই।
চিকিৎসক ও ক্যান্সার দাতব্য সংস্থাগুলো কী বলছে?
এ ধরনের বিভিন্ন বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতিতে মারাত্মক বিপদ লুকিয়ে আছে বলে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন। এসব পদ্ধতি ব্যবহারে মূল চিকিৎসা বিঘ্নিত হওয়ার বা রোগীর বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে আসার বিষয়টি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।
ডক্টর রিয়োর্ডান বলেন, "মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি এ ধরনের পদ্ধতি কোনোটির প্রয়োগ ঠিক হতে পারে। সমস্যাটা হয় তখনই যখন শুধু এসব পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়। এক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যুর ঝুঁকি দুই বা আড়াই গুণ বেড়ে যায়।"
ডক্টর গ্রিমস বলেন, শক্তিশালী গবেষণা ওপর ভিত্তি করে ক্যান্সার চিকিৎসা চলে।
"বিকল্প পদ্ধতিগুলোর কারণে নয়, বরং বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের কঠোর পরিশ্রমের কারণেই বিশ্বজুড়ে ক্যান্সার থেকে মানুষ সুস্থ হয়ে উঠছেন এবং তাদের বেঁচে যাওয়ার হার বাড়ছে", যোগ করেন তিনি।
ভারতের ম্যাক্স ইনস্টিটিউট অব ক্যান্সার কেয়ারের চেয়ারম্যান ডক্টর হারিত চতুর্বেদি বলেন, "ক্যান্সার এমন কোনো রোগ নয় যেটা কোনো জাদুকরি ফর্মুলায় দূর হয়ে যাবে।"
বরং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রতিটি রোগীর জন্য তাদের ক্যান্সারের ধরন, জিনগত বিশেষ পরিবর্তন, যে অঙ্গ থেকে ক্যান্সার ছড়িয়েছে সেটাসহ নানা বিষয় অনুসন্ধান করে বিশেষ চিকিৎসা পরিকল্পনা দেওয়া হয়।
অসুস্থতায় একটু আরাম পাওয়া যাবে এরকম কোনো সহায়ক পদ্ধতি রোগীরা নিতে চাইলে চিকিৎৎসকরা সাধারণত তাদের সমর্থন দেন। কিন্তু তারা কখনই শুধু এসব পদ্ধতির ওপর নির্ভর করার কথা বলেন না।
শীতে ব্রণ বেড়ে গেলে কী করবেন
শীতকালে ত্বকে দেখা দেয় নানা ধরনের সমস্যা। বিশেষ করে শীতে ত্বক থেকে প্রাকৃতিক তেল কম নিঃসৃত হওয়ায় ব্রণ বেড়ে যায়। তাই ব্রণ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে শীতে বিশেষ যত্ন নেওয়া জরুরি।
শীতকালে ব্রণ কমানোর জন্য কিছু কার্যকরী টিপস জানিয়েছেন বিউটিএক্সাপার্ট পন্নি খান। চলুন জেনে নেওয়া যাক সে সম্পর্কে।
১. ত্বক পরিষ্কার রাখতে হবে-
শীতকালে ত্বক পরিষ্কার রাখতে হালকা, পিএইচ-ব্যালেন্সড ক্লিনজার ব্যবহার করা ভালো। এতে ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয় না এবং ব্রণ বাড়ার সম্ভাবনাও কমে।
২. ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার-
শীতে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার না করলে ত্বক অতিরিক্ত তেল উৎপন্ন করে, যা ব্রণের সৃষ্টি করতে পারে। একটি হালকা, অয়েল-ফ্রি ময়েশ্চারাইজার বেছে নিন যাতে ত্বক আর্দ্র থাকে এবং ব্রণ নিয়ন্ত্রণে থাকে।
৩. তেলযুক্ত প্রসাধনী থেকে দূরে থাকতে হবে-
শীতে ত্বকে অতিরিক্ত তেলযুক্ত পণ্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ অতিরিক্ত তেল ত্বকের পোর বন্ধ করে দেয় এবং ব্রণ সৃষ্টি করে। তেলের বদলে জলভিত্তিক বা অয়েল-ফ্রি প্রোডাক্ট ব্যবহার করুন।
৪. আর্দ্রতা বজায় রাখুন-
শীতকালে ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়ার কারণে ব্রণ বেড়ে যায়। এজন্য ঘরের আর্দ্রতা বজায় রাখা জরুরি। একটি হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করলে শুষ্কতা কমবে এবং ত্বক আর্দ্র থাকবে।
৫. সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং পানি পান
শীতে অনেকেই পানি কম পান করেন, কিন্তু শরীর ও ত্বকের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে পর্যাপ্ত পানি পান করা জরুরি। এছাড়া, পুষ্টিকর খাবার যেমন তাজা ফল, শাকসবজি এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য ত্বক সুস্থ রাখে এবং ব্রণ কমায়।
৬. ডাক্তারি পরামর্শ নিন-
ব্রণ যদি বেশি হয়ে থাকে এবং বাড়তে থাকে, তাহলে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। চিকিৎসক প্রয়োজনে সঠিক ক্রিম বা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট সাজেস্ট করতে পারেন যা শীতকালে ব্রণ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে।
মোজা পরে ঘুমানো স্বাস্থের জন্য ভালো
এবার বেশ খানিকটা আগেভাগেই চলে এসেছে শীত, ভালোই জেঁকে বসেছে। ভারি কাপড় পরে বাইরে বের হতে হচ্ছে। সেইসঙ্গে অনেকেই উষ্ণ থাকতে বাসার ভেতরে মোজা পরছেন, রাতে ঘুমাচ্ছেনও মোজা পরে। তবে অনেকেই জানেন না, মোজা পরে শোয়ার অভ্যাস স্বাস্থ্যকর নাকি ক্ষতিকর।
চিকিৎসকরা বলছেন, মানুষের হাত ও পা অতিমাত্রায় ঠান্ডা হয়ে যাওয়াকে রায়নাউড সিনড্রোম বলা হয়, যার ফলে পায়ে ভালোভাবে রক্ত পৌঁছাতে পারে না। এতে করে হাত ও পায়ে অসাড়তা তৈরি হয়। শীতের রাতে পায়ে মোজা পরলে এই সিনড্রোমের উপসর্গ কমে।
মোজা পরে ঘুমালে পা উষ্ণ থাকে, ফলে রক্ত সঞ্চালন ভালোভাবে হয়। এর ফলে শরীরে রক্ত প্রবাহ এবং অক্সিজেন প্রয়োজন মতো নির্দিষ্ট থাকে এবং হার্ট, ফুসফুস এবং পেশী তাদের সর্বোত্তম ক্ষমতাকে কাজ লাগাতে পারে।
নারীদের মেনোপজের সময় রাতে হট ফ্ল্যাশ দেখা দিলে অর্থাৎ আকস্মিকভাবে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি, শরীর গরম এবং ঘাম অনুভব হয়। মোজা পরলে পায়ের অংশ উষ্ণ থাকে যা শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আমাদের শরীরের সবচেয়ে সংবেদনশীল অঙ্গগুলোর মধ্যে পা একটি। যখন পা ঠান্ডা থাকে তখন স্বাভাবিকভাবেই ঘুমাতে অসুবিধা হতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ায় ছয়জন পুরুষ নিয়ে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, মোজা পরিহিত পুরুষরা ৩২ মিনিট বেশি এবং মোজা ছাড়া ব্যক্তিদের তুলনায় সাড়ে ৭ মিনিট পূর্বেই দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মোজা পরে ঘুমালে পা উষ্ণতা পায়, যা দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তে এবং দীর্ঘক্ষণ ঘুমাতে সাহায্য করে।
তবে মোজা পরে ঘুমানোর কিছু ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। মোজা পরে ঘুমালে শরীরের রক্ত সঞ্চালন ভালভাবে যেমন হয়, তেমনি মোজা বেশি টাইট হলে রক্ত চলাচল কমে যেতে পারে। মোজা যদি বাতাস চলাচলের উপযোগী না হয় তবে তাপকে শরীর থেকে বের হতে বাধা দেবে এবং শরীর অতিরিক্ত গরম হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও মোজা যদি পরিষ্কার না হয় তবে পায়ে বিভিন্ন সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়।
শিশুরাও মোজা পরে ঘুমাতে পারে। তবে নরম, প্রাকৃতিক, বাতাস চলাচল করতে পারার মতো উপাদান যেমন তুলার ঢিলেঢালা মোজা দিতে হবে। টাইট ইলাস্টিক টপসসহ মোজা এড়িয়ে চলাই শ্রেয়, যেহেতু এটি শিশুর শরীরের রক্ত প্রবাহকে সীমাবদ্ধ করতে পারে।
যদি শরীরে রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা, পা ফুলে যাওয়া অথবা পায়ে রক্ত প্রবাহ সীমিত করে দেওয়ার মতো শারীরিক সমস্যা থাকে তবে মোজা পরে ঘুমানোর বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নিন।