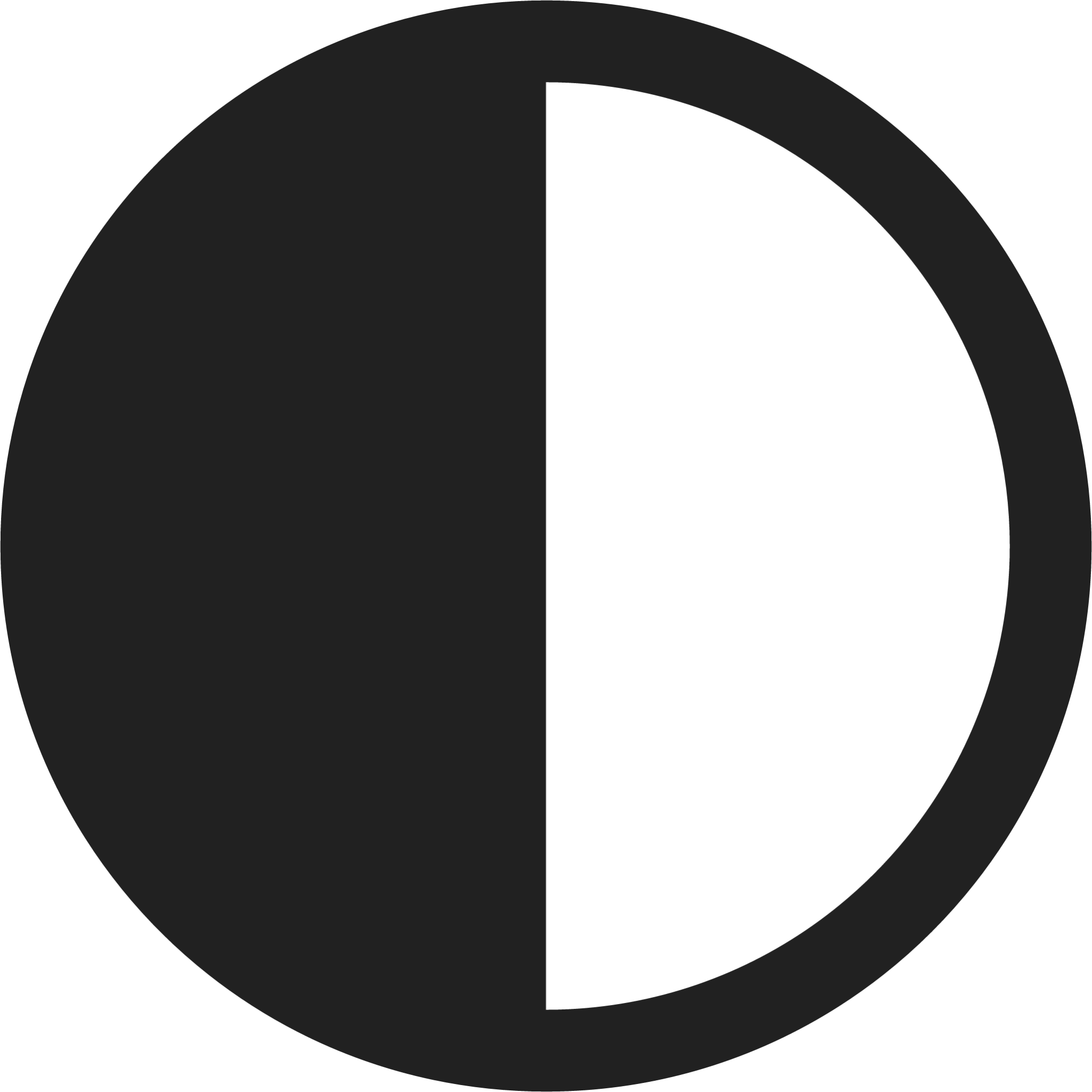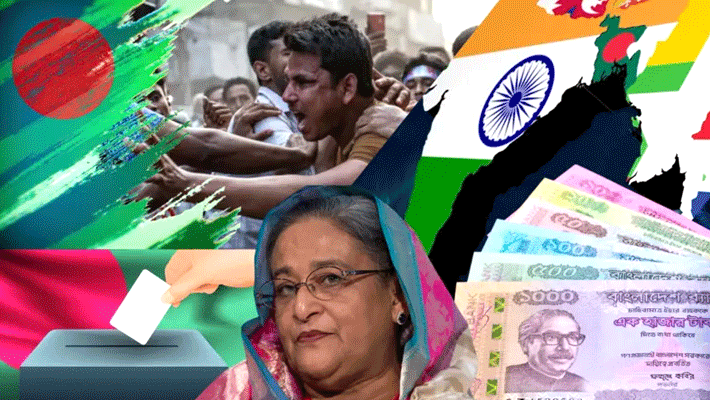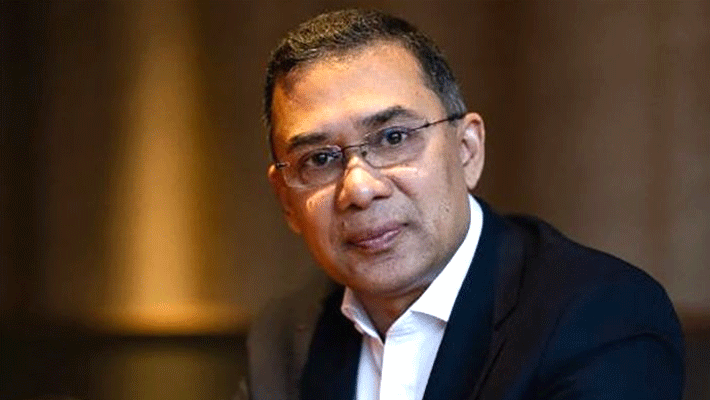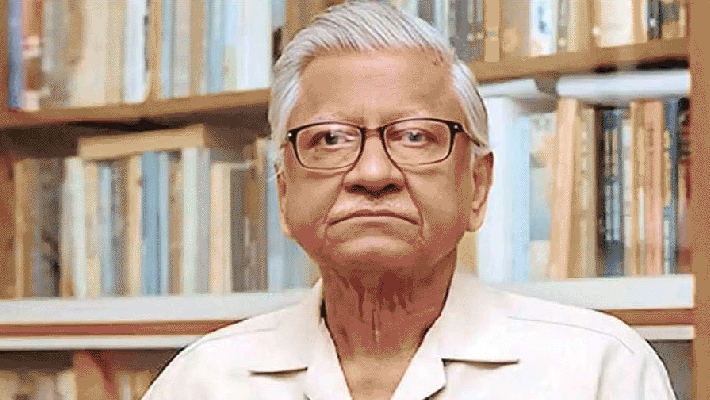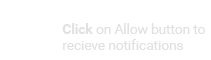শীতের তীব্রতা বেড়েছে, কুয়াশা থাকতে পারে আরও ২-৩ দিন
তীব্র শীতে কাঁপছে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ছিল কুয়াশার দাপট, দেখা মেলেনি সূর্যের। শীতের তীব্রতা বাড়ায় ভোগান্তি বেড়েছে সাধারণ মানুষের। আবহাওয়া অফিস বলছে, ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে আরও দুই থেকে তিন দিন কুয়াশা থাকতে পারে।
আবহাওয়াবিদ বজলুর রশিদ দ্য ডেইলি স্টারকে জানান, গতকাল ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস কম ছিল।
আবহাওয়ার সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়া অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে দুপুর পর্যন্ত সারাদেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে এবং দিনের তাপমাত্রা এক থেকে দুই থেকে ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে।
দ্য ডেইলি স্টারের ঠাকুরগাঁও সংবাদদাতা জানান, সূর্যের দেখা না মেলায় ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়সহ উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে হাড় কাঁপানো শীতে দৈনন্দিন কাজ চালাকে হিমশিম খাচ্ছেন নিম্ন আয়ের মানুষ।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় দেশের তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা ছিল ১১ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বুধবার বিকেল ৩টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৫ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আবহাওয়াবিদ বজলুর রশিদ দ্য ডেইলি স্টারকে জানান, গতকাল ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দিনের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস কম ছিল।
আবহাওয়ার সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার আবহাওয়া অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। মধ্যরাত থেকে দুপুর পর্যন্ত সারাদেশে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকবে এবং দিনের তাপমাত্রা এক থেকে দুই থেকে ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে।
দ্য ডেইলি স্টারের ঠাকুরগাঁও সংবাদদাতা জানান, সূর্যের দেখা না মেলায় ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়সহ উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে হাড় কাঁপানো শীতে দৈনন্দিন কাজ চালাকে হিমশিম খাচ্ছেন নিম্ন আয়ের মানুষ।
তেঁতুলিয়া আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় দেশের তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা ছিল ১১ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বুধবার বিকেল ৩টায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৫ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস।
নতুন বছরে বাংলাদেশের সামনে যত চ্যালেঞ্জ
সদ্য শেষ হয়ে যাওয়া ২০২৪ এ বছর জুড়ে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর রেশ নিয়েই নতুন বছরে পা দিয়েছে বাংলাদেশ। বিগত বছরে যেমন নানামুখী চ্যালেঞ্জ আর অভূতপূর্ব ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে গেছে বাংলাদেশ - নতুন বছরেও রাজনীতি, নির্বাচন আর অর্থনীতিতে চ্যালেঞ্জ থাকবে।
চলতি বছরেই ঘোষণা হতে পারে পরবর্তী নির্বাচনের সম্ভাব্য সময়, যা সরাসরি প্রভাব রাখবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনীতি আর কূটনৈতিক সম্পর্কে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে মতভেদ দেখা যাচ্ছে সামনে বছর তা আরও ঘনীভূত হতে পারে। বিশেষ করে নির্বাচন এগিয়ে আসার সাথে সাথে এই মতভেদ রূপ নিতে পারে সংঘাতেও।
এছাড়াও ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশ নেয়া-না নেয়াও একটি বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে। একইসঙ্গে শেখ হাসিনার ভারতে অবস্থানের প্রভাব পড়তে পারে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কেও।
অন্যদিকে, বাংলাদেশের সীমান্তঘেঁষা মিয়ানমারের দুটি রাজ্য আরাকান আর্মির দখলে যাওয়ায় দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের রূপ কী হবে, তা নিয়েও বেশ জটিলতায় পড়তে হতে পারে বাংলাদেশকে।
এছাড়াও পাঁচই অগাস্টের পর দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা এবং মব সংস্কৃতির মতো বিষয়গুলো যে প্রকট আকার ধারণ করেছে, সেটাকে শৃঙ্খলায় ফেরানোও দেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে।
তবে সবচেয়ে বড় যে চ্যালেঞ্জেটির মুখোমুখি বাংলাদেশকে হতে হবে, তা হলো অর্থনীতি।
মূল্যস্ফীতি, টাকার বিপরীতে বাড়তে থাকা ডলারের দাম এবং আর্থিক খাতে যে সংকট ২০২৪ সালে দেখা গেছে, তা পরবর্তী বছরেও বাংলাদেশকে বেশ ভোগাবে বলেই মত বিশ্লেষকদের।
নির্বাচন ও রাজনীতি
নতুন বছর অর্থাৎ ২০২৫ হতে পারে বাংলাদেশের জন্য নির্বাচনের বছর। ফলে নতুন বছরে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।
গণঅভ্যুত্থানের পর নির্বাচন ও সংস্কার ইস্যুতে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর নানা ধরনের মতবিভেদ দেখা গেছে।
বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে এই মতভেদ যদি আরও প্রকট হয় তবে সেটা সংকটের জন্ম দিতে পারে বলে শঙ্কা প্রকাশ করছেন বিশ্লেষকরা।
' জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র' দেয়া নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে শুরু হওয়া আলোচনা প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, বিপ্লব বা গণঅভ্যুত্থানের পার্টিসিপেন্ট শুধু ছাত্ররা না, সেখানে বিএনপি-জামায়াত আছে।
"তারা (বিএনপি ও জামায়াত) সংবিধানের অনুসারী, বিপ্লবের না। সুতরাং এখানে ডিফারেন্সেস অব অপিনিয়ন (মতভেদ) থাকছে। আর নির্বাচনের সময় যত ঘনিয়ে আসবে, এই দুইয়ের মধ্যে একটা সাংঘর্ষিক অবস্থান তৈরি হতে পারে", বলেন এই রাজনৈতিক বিশ্লেষক।
তাছাড়া রাজনৈতিক দলগুলো আগের মতোই পরিবারতন্ত্রের মধ্যে আটকে থাকবে, নাকি নিজেদের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা করবে, সে বিষয়টিও রাজনীতিতে চ্যালেঞ্জ হয়ে আসতে পারে।
আর গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে নির্বাচনকে যেহেতু একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যমে হিসেবে দেখা হয়, সেখানে নির্বাচন আয়োজনে আন্তর্জাতিক একটি চাপ থাকতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে।
এছাড়াও বাংলাদেশের জন্য ২০২৫'এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হতে পারে আওয়ামী লীগ। নির্বাচনে দলটির অংশগ্রহণ থাকা বা না থাকা নিয়ে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।
অধ্যাপক আহমেদের মতে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং বিষয় হবে অংশগ্রহণমূলক স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করা।
"যদি আপনি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা বলেন তাহলে আপানকে ভাবতে হবে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে আসতে পারবে কিনা। এই প্রশ্নের একটা অসমাধান বের করতে হবে এবং এই সমাধানটা খানিকটা চ্যালেঞ্জিং", বলেন অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ।
কূটনৈতিক সম্পর্ক - মাথাব্যাথা ভারত আর মিয়ানমার
কেবল দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটেই না, দেশের বাইরের কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও চ্যালেঞ্জিং ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে আওয়ামী লীগ।
বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশ ভারতে ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অবস্থানের কারণে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কেও পড়তে পারে বড় প্রভাব।
এ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক আমেনা মহসিন বিবিসি বাংলাকে বলেন, "শেখ হাসিনাতো ওখানে বসে নেই। ওখানে তিনি নানা ধরনের রাজনীতির সঙ্গে ইনভলভড আছেন, তাই না? যারা চলে গেছে, তারা তো চুপ থাকবে না। আর দেশের বাইরেও তাদের মিত্ররা আছে।"
বিশেষ করে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ইস্যু এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভারত "নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষন করবে এবং সেখানে টানাপোড়েন থাকবে" বলেও মনে করেন তিনি।
অন্যদিকে, অন্তর্বর্তী সরকার থাকাকালীন ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক স্বাভাবিক করা সম্ভব হবে কী-না সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে অধ্যাপক সাব্বির আহমেদের।
"শেখ হাসিনার ভারতে আশ্রয়ের কারণে বর্তমান সরকারের জন্য সম্পর্ক স্বাভাবিক করাটা অস্বস্তিকর হতে পারে। শেখ হাসিনার অন্যায়ের বিচার করতে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেখান থেকে তারা সরতে পারবে না, আবার ভারতের সঙ্গে সম্পর্কটা তারা এমন জায়গায়ও নিতে পারবে না, যাতে আমাদের দেশ সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়", বলেন তিনি।
সেক্ষেত্রে, নির্বাচিত সরকার না আসা পর্যন্ত পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে বাংলাদেশকে বেগ পেতে হবে।
আবার অনেকটা একই দৃশ্যপট আরেক প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের ক্ষেত্রেও।
শুরু থেকেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতিতে মিয়ানমারকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়নি। অথচ বাংলাদেশের সংকটের তালিকায় বেশ উপরেই জায়গা করে নেবে রোহিঙ্গা ইস্যুটি।
তার ওপর বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো আরাকান আর্মি দখলে নেয়ায় নির্বাচিত সরকার ছাড়া দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের গতিপথ নির্ধারণ বেশ কঠিন হবে বলেই মত বিশ্লেষকদের।
"দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে আমাদের ভীষণভাবে মনোযোগ দিতে হবে এবং মিয়ানমারের ক্ষেত্রে দেশটির মধ্যে থাকা বিভিন্ন ফ্র্যাকশনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এগয়ে যেতে হবে", বলেন অধ্যাপক মহসিন।
একইসঙ্গে বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে চলমান ভূরাজনীতিতে নিজেদের দৃঢ় অবস্থান ধরে রাখাও বাংলাদেশের জন্য চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি
পাঁচই অগাস্টের পর থেকে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটেছে। ছিনতাই, রাহাজানি, লুটপাট, চাঁদাবাজি বাড়ার খবর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তরফেই এখন স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে।
ভঙ্গুর অবস্থা থেকে খুব একটা ঘুরে দাঁড়াতে দেখা যায়নি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও। উত্থান ঘটেছে মব সংস্কৃতির। বেড়েছে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা।
এসব বিশৃঙ্খলাকে ২০২৫ সালে শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনাও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।
অধ্যাপক মহসিন বলেন, "২০২৪ সালে এক ধরনের একটা কেওস (চরম বিশৃঙ্খলা) কিন্তু আমরা দেখেছি। ওই শৃঙ্খলাটা ফেরত আনা কিন্তু বড় ব্যাপার থাকবে।"
"কিন্তু শৃঙ্খলার নামে আবার কারো শ্বাসরুদ্ধ করে দিচ্ছি, সেটা হবে না", বলেন এই বিশ্লেষক।
এগুলোর মধ্যে ভারসাম্য আনার পাশাপাশি মানবাধিকার পরিস্থিতির দিকেও নজর দেয়ার কথা বলেন এই বিশ্লেষক।
"একেকজনের বিরুদ্ধে অনেকগুলো মামলা হচ্ছে, এটা কিন্তু ঠিক না। ১০০টা মামলা দিয়ে দিলেন বা কোনোভাবেই জড়িত না তার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দিয়ে দিলেন - এই জায়গা থেকে উত্তরণ করতে হবে, কারণ মানবাধিকার ইস্যুটা এখানে একটা বড় জায়গা হয়ে যাচ্ছে", বলেন তিনি।
অন্যদিকে, দেশের বিভিন্ন জায়গায় যে ব্যাপকহারে চাঁদাবাজি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে, তা নিয়ে এখনও কার্যকর কিছু করা হচ্ছে না বলে মনে করেন বিশ্লেষকদের কেউ কেউ।
অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ বলছেন, জুলাই বিপ্লবে অনেকগুলো পক্ষ অংশীদার হলেও তাদের স্বার্থের সমীকরণ আলাদা। এটা সমাধান হয়নি।
উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, "রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দখল করে বসে আছে। সেই পদগুলোকে তারা তাদের করায়ত্ত করে নিয়েছে। এর মাধ্যমে তারা তাদের দলীয় স্বার্থকে সুসংহত করার চেষ্টা করছে।"
তিনি বলছেন, বহু জায়গায় আগের দলের আওয়ামী লীগের) স্থানে নতুন দল চাঁদাবাজিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু সে বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে না।
এছাড়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে রাজনীতিকরণের হাত থেকে মুক্ত করাটা চ্যালেঞ্জিং হবে বলে মনে করেন অধ্যাপক মহসিন।
"প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ আমরা বলি না? সেই জায়গাটা ইন্সটিটিউশনালাইজেশন অব ইন্সটিটিউশন- সেটা আমাদের ভীষণভাবে প্রয়োজন", বলেন তিনি।
আর উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ছাত্রদের রাজনীতির আগে শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
অর্থনীতির যত চ্যালেঞ্জ
তবে বাংলাদেশের জন্য ২০২৫ সালে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জিং ফ্যাক্টর হতে পারে অর্থনীতি, যা আগের বছরও প্রকট ছিল।
অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর আগের সরকারের আমলে আর্থিক খাতে যে পরিমাণ দুর্নীতির উন্মোচিত হয়েছে, তা থেকে বেরিয়ে নতুন করে দেশের অর্থনীতিকে গঠন প্রক্রিয়া বেশ কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হবে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদেরা।
ইতোমধ্যেই ২০২৪-২৫ অর্হবছরে বাংলাদেশের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার সাড়ে চার শতাংশ হবে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল - আইএমএফ।
আর সার্বিক মূল্যস্ফীতি হবে নয় দশমিক সাত শতাংশ।
অর্থনীতিবিদরা বলছেন, অনবরত বাড়তে থাকা মূল্যস্ফীতি এবং ডলারের সঙ্গে টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখতে না পারায় ২০২৫ সালের জন্য ভালো ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে না।
অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বলেন, "মূল্যস্ফীতি অব্যাহত আছে, আর একে কিছুতেই বাগ মানানো যাচ্ছে না। এটা একটা বড় সমস্যা। আর ডলারের সঙ্গে আমাদের টাকার যে বিনিময় হার - সেটা ক্রমাগত উপরের দিকে যাচ্ছে এবং সেটাকে একটা জায়গায় স্থিতিশীল করা যাচ্ছে না"।
তার ওপর আছে রিজার্ভ সংকট।
"কোনোভাবেই এর অবস্থা ২০-২২ বিলিয়নের ওপরে যাচ্ছে না" উল্লেখ করে এই অর্থনীতিবিদ বলেন, "আমাদের একটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ভঙ্গুর রিজার্ভের অবস্থা এটাকে কীভাবে পরিবর্তন করা যায়। সেটা যদি না করা যায় তাহলে এক্সচেঞ্জ রেটের ইনস্ট্যাবিলিটি সেটা অব্যাহত থাকবে, সেটা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না।"
সেক্ষেত্রে রিজার্ভ বাড়াতে হলে রেমিট্যান্সের দিকে নজর দেয়ার পরামর্শ দেন অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ।
এছাড়াও ব্যাংক খাতে অস্থিরতার প্রভাব থাকবে সামনে বছরও। বিশেষ করে টাকা ছাপিয়ে ব্যাংকগুলোকে উদ্ধার করার পদক্ষেপের নেতিবাচক ফলাফলও দেখা যাবে আর্থিক খাতে।
তার ওপর রাজনৈতিক দোলাচলের প্রভাবও থাকবে বিনিয়োগে।
"আমাদের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে আমাদের বিনিয়োগ বাড়ছে না। এটা জিডিপির ২২-২৩-২৪ শতাংশের মধ্যে স্থির হয়ে আছে। এটাকে যদি ৪০ শতাংশে না নেয়া যায়, তাহলে কিন্তু আমরা সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির হার আশা করতে পারি না", বলেন এই অর্থনীতিবিদ।
২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় তারেক রহমান-বাবরসহ সব আসামি খালাস
বহুল আলোচিত একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলার মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত তারেক রহমান ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরসহ সব আসামিকে খালাস দিয়েছেন হাইকোর্ট।
বিচারিক আদালতের রায় বাতিল করে রোববার (১ ডিসেম্বর ) বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। এর আগে গত বৃহস্পতিবার বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চে এর শুনানি শেষ হয়।
গত ২১ নভেম্বর এ মামলায় খালাস চেয়ে করা আসামির আপিল ও ডেথ রেফারেন্স শুনানি শেষ হয়। রোববার বেলা বেলা ১১টার কিছু আগে শুরু হয় রায় পড়া। এরপর পৌনে ১২টার দিকে রায় ঘোষণা করেন হাইকোর্ট। খালাস দেয়া হয় সব আসামিকে। সেইসঙ্গে এই মামলাটি অবৈধ ছিল বলেও জানান আদালত।
প্রায় ছয় বছর আগে বিচারিক আদালতের রায়ের পর ডেথ রেফারেন্সের ও আসামিদের আপিল-জেল আপিলের শুনানি শুরু হয় ২০২২ সালের ৪ ডিসেম্বর। গত দেড় বছর বিচারপতি সহিদুল করিম ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চে এ মামলার শুনানি হয়েছে।
ছাত্র-জনতার প্রবল আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ ছেড়ে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। তার ক্ষমতাচ্যুতির পর বিচার বিভাগেও পরিবর্তন আসে। প্রধান বিচারপতির পদ থেকে ওবায়দুল হাসানের পদত্যাগের পর আপিল বিভাগের আরো পাঁচ বিচারপতি পদত্যাগ করেন।
নতুন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ গত ১১, ১২ ও ১৫ আগস্ট এখতিয়ার পরিবর্তন করে হাইকোর্টের ৫৪টি হাইকোর্ট বেঞ্চ পুনর্গঠন করেন। বেঞ্চ পুনর্গঠনের পর মামলাটি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চে আসে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার সমাবেশে গ্রেনেড হামলা চালিয়ে ২৪ জনকে হত্যা করা হয়। আওয়ামী লীগের দাবি, এ হামলা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। হামলার পরদিন মতিঝিল থানার তত্কালীন এসআই শরীফ ফারুক আহমেদ বাদী হয়ে একটি মামলা করেন। থানা পুলিশ, ডিবির হাত ঘুরে সিআইডি এই মামলার তদন্তভার পায়। ঘটনার চার বছর পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে ২০০৮ সালের ১১ জুন হত্যার অভিযোগ এবং বিস্ফোরকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আলাদা দুটি অভিযোগপত্র দেন সিআইডির জ্যেষ্ঠ এএসপি ফজলুল কবির। জঙ্গি দল হরকাতুল জিহাদ বাংলাদেশের নেতা মুফতি আব্দুল হান্নানসহ ২২ জনকে সেখানে আসামি করা হয়। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে ২০০৮ সালের ২৯ অক্টোবর অভিযোগ গঠন করে তাদের বিচারও শুরু হয়। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর রাষ্ট্রপক্ষ মামলাটির অধিকতর তদন্তের আবেদন করলে ট্রাইব্যুনাল তা মঞ্জুর করে। সিআইডির বিশেষ সুপার আব্দুল কাহার আকন্দ অধিকতর তদন্ত শেষে ২০১১ সালের ৩ জুলাই আসামির তালিকায় আরো ৩০ জনকে যোগ করে সম্পূরক অভিযোগপত্র দেন।
সেখানে বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ চারদলীয় জোট সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী ও বিএনপি-জামায়াতের নেতাদের নাম আসে। দুই মামলায় মোট ৫২ আসামির বিচার শুরু হলেও অন্য মামলায় তিনজনের ফাঁসি কার্যকর হওয়ায় মোট ৪৯ আসামির বিচার করেন বিচারিক আদালত।
২০১৮ সালের ১০ অক্টোবর ওই মামলার রায় হয়। রায়ে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুত্ফুজ্জামান বাবর, উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুসহ ১৯ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়।
তারেক রহমান, খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরীসহ ১৯ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেন বিচারিক আদালত। সেই সঙ্গে ১১ পুলিশ ও সেনা কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
রায়ের পর ওই বছরের ২৭ নভেম্বর বিচারিক আদালতের রায় প্রয়োজনীয় নথিসহ হাইকোর্টের ডেথ রেফারেন্স শাখায় এসে পৌঁছে। দণ্ডিতরাও রায়ের বিরুদ্ধে আপিল-জেল আপিল করেন। পরে পেপারবুক প্রস্তুত করা হয়।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অস্থিরতা ঠেকাতে ‘জাতীয় ছাত্র সংহতি সপ্তাহ’
আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পুনর্বাসন ঠেকাতে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে চলমান অস্থিরতা নিরসনে আগামী এক সপ্তাহ 'জাতীয় ছাত্র সংহতি সপ্তাহ' পালন করবে ফ্যাসিবাদবিরোধী সব ছাত্রসংগঠন।
রাজধানীর বাংলামোটরে সোমবার রাতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন আয়োজিত অন্যান্য সব ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে জরুরি বৈঠক শেষে এই ঘোষণা দেন আহ্বায়ক হাসনাত আব্দুল্লাহ।
তিনি বলেন, 'ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে সবাই একসঙ্গে এসেছিল বলেই সামগ্রিকভাবে আমরা ফ্যাসিস্ট ও খুনি শেখ হাসিনাকে আমরা স্থায়ীভাবে বাংলাদেশ থেকে উৎখাত করতে পেরেছি। এর পরে আমাদের প্রত্যাশিত বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছে। শুরু হওয়ার পর থেকেই আমরা দেখছি যে, ফ্যাসিবাদীদের নানা ধরনের ষড়যন্ত্র। তারা বিদেশে বসেও বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র করছে এবং বিভিন্ন ফরমেটে তারা আবার ফিরে আসতে চাচ্ছে।
আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, জিরো টলারেন্স টু আওয়ামী লীগ।'
হাসনাত বলেন, 'ফ্যাসিবাদবিরোধী যে রাজনৈতিক শক্তিগুলো ছিল ৫ আগস্টের আগে, সেই প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের পুনর্বাসনের প্রশ্নে জিরো টলারেন্স নীতি অবলম্বন করবে। কোনো ফরমেটেই আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না। তারা যত চেষ্টাই করুক না কেন।'
তিনি বলেন, 'আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেশে বিভিন্ন সময় যে আন্দোলনগুলো দানা বাঁধছে, প্রত্যেক দাবি নিয়ে রাস্তায় আসছে। আমরা দেখছি, সেখানে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের ব্যাপক অর্থায়ন রয়েছে। গত ১৬ বছরের দুঃশাসনে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের অর্থনীতিকে নাজুক অবস্থায় নিয়ে গিয়ে নিজেদের পকেট ভারী করেছে। ব্যাংকগুলোকে খালি করে ফেলা হয়েছে। দুই লাখ কোটি টাকার বেশি পাচার করেছে।'
'আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি, গত তিনটি নির্বাচনে যারা নির্বাচিত হয়েছে আওয়ামী লীগ থেকে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে। আইনগতভাবে এটি যদি করা না যায়, তাহলে বিদেশে বসে বাংলাদেশকে পিছিয়ে নেওয়ার জন্য যে ষড়যন্ত্র করছে, সেই ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকবে,' যোগ করেন তিনি।
অন্তর্বর্তী সরকারকে দৃশ্যমান পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান হাসনাত। তিনি আরও বলেন, 'যে প্রশাসন ফ্যাসিবাদকে হৃষ্টপুষ্ট করেছে, বাংলাদেশের মানুষের অধিকার হরণ করেছে, সরকার যদি ভেবে থাকে এই একই প্রশাসন দিয়ে তারা একটি প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ গঠন করবে, তাহলে তারা ভুল করছে। আওয়ামী রাজনৈতিক রেকোমেনডেশনে যাদের নিয়োগ হয়েছে, তাদের বাদ দিয়ে প্রশাসন পুনর্গঠন করতে হবে। তা না হলে সরকারের সংস্কার কার্যক্রমের জটিলতা অব্যাহত থাকবে।'
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অস্থিরতার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, 'আজকেও আপনারা দেখেছেন মাহবুবুর রহমান মোল্লা কলেজে একজন শিক্ষার্থীকে এমন কেউ পেটাচ্ছে, যাকে কোনোভাবেই ছাত্র মনে হয় না। অর্থাৎ ছাত্র পরিচয়ে প্রতিটি আন্দোলনে...অটোরিকশাচালকদের আন্দোলনে আমরা ছাত্রলীগ-যুবলীগের অংশগ্রহণ দেখেছি। তারা উপলক্ষ খোঁজে। সেই জায়গা থেকে সব ছাত্রসমাজ একমত হয়েছি, আগামী এক সপ্তাহ আমরা জাতীয় ছাত্র সংহতি সপ্তাহ পালন করব। এই এক সপ্তাহে ফ্যাসিবাদবিরোধী সংগঠনগুলো বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যাবে, একতা ও সংহতির বার্তা পৌঁছে দেবে এবং আওয়ামী ফ্যাসিবাদের পুনর্বাসন ঠেকাতে আমাদের সংহতির কোনো বিকল্প নেই—সেই বার্তা পৌঁছে দেবে। পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক মেলবন্ধন দৃঢ় করার জন্য আমাদের এই কর্মসূচি।'
কপ-২৯ সম্মেলনে যোগ দিতে বাকুতে পৌঁছেছেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস
আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিতব্য কপ-২৯ জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দিতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস আজ (১১ নভেম্বর) বিকেলে পৌঁছেছেন। তিনি বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে বাকু পৌঁছান।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানান, ড. ইউনূস ও তার সফরসঙ্গীরা আজ সকাল ১১টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আজারবাইজানের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। এই রাষ্ট্রীয় সফরে তিনি ১১ থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত আজারবাইজানে থাকবেন।
কপ-২৯ সম্মেলনের বিভিন্ন ফোরামে বক্তব্য প্রদান এবং আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করবেন অধ্যাপক ড. ইউনূস। তার বক্তব্যে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশ যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে, তা তুলে ধরার পাশাপাশি জলবায়ু বিষয়ক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশের করণীয় বিষয়গুলোও আলোচনায় আসবে।
এই সফর বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার সুযোগ এনে দেবে বলে আশা করা হচ্ছে।
‘জনগণ জাগলে কোনো অপশক্তিই তাকে পরাজিত করতে পারে না’
শিক্ষাবিদ, সমাজ-বিশ্লেষক ও চিন্তাবিদ আবুল কাসেম ফজলুল হক। জন্ম ১৯৪০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করেছেন দীর্ঘ চার দশক। পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত কলাম লিখে চলছেন এখনো।
তিনি ২০০০ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত স্বদেশ চিন্তা সংঘের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তার রাষ্ট্রচিন্তা পরিব্যাপ্ত হয়েছে জাতীয়তাবাদ থেকে আন্তর্জাতিকতাবাদ পর্যন্ত।
সময়ের গুরুত্বপূর্ণ এই চিন্তকের মৌলিক ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৫০টির বেশি। তিনি ১৯৮১ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। গত ১০ জুন ঢাকার পরীবাগের বাসায় সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি ও গণতন্ত্রসহ বিবিধ বিষয়ে দ্য ডেইলি স্টারের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি।
উপাচার্য-শিক্ষকদের দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। এরকম ঘটনা দেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যায়তনিক পরিবেশ যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তেমনি এর প্রভাব পড়ছে শিক্ষার্থীদের ওপরেও। এর পেছনের কারণ কী?
আবুল কাসেম ফজলুল হক: উপাচার্য-শিক্ষক দুই গোষ্ঠীই অন্যায় করে করছে। দুই পক্ষই নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য এমন সংকট তৈরি করছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরা সবাই স্বার্থ, পদ ও ক্ষমতার জন্য দলাদলি করে। কখনো ভিসির পক্ষে লোক বেশি হয়, কখনো শিক্ষক সমিতিতে। যখন যার পক্ষে লোক কম থাকছে তারা চাপে পড়ছে। আর তখনই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার্থী, প্রতিষ্ঠান।
এ থেকে উত্তরণ ঘটাতে পারে সরকারি দল তথা সরকার। তারা তাদের কর্তৃত্ব সীমিত রাখতে পারে। যেকোনো প্রতিষ্ঠানে সরকার কর্তৃত্ব করবে। কিন্তু এটা করতে হবে বিধির মধ্যে থেকে। আইনের বাইরে গিয়ে না।
আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে অনেক কথা বলতে শোনা যায়। বলা হচ্ছে—ছাত্র সংসদ নির্বাচন নেই বলে গতিহীন হচ্ছে মৌলিক ছাত্র রাজনীতি। আপনিও কি তাই মনে করেন?
আবুল কাসেম ফজলুল হক: ১৯৭২ সাল থেকে এই সংকট শুরু হয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোনো সরকারই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করেনি। তারা সবাই নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো হয় এমন উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি।
স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর— এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করতে দেয় না সরকার। নানা কায়দায় হস্তক্ষেপ করে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সেভাবে ঠিক থাকে না।
আর ছাত্রদের দিয়ে লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি করানোর জন্যই ছাত্র সংসদ নির্বাচন দেওয়া হয় না। এক কথায় আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের কথা কেউ চিন্তা করে না।
আবরারের ঘটনায় বুয়েটে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হলো। ক্ষমতাসীনরা সেখানে আবার ছাত্র রাজনীতি চালু করতে চায়। এই ছাত্র রাজনীতি দিয়ে দেশের কি হবে?
আবুল কাসেম ফজলুল হক: বর্তমানে যে ছাত্র রাজনীতি চালু আছে তা দিয়ে আগামীতে সুস্থ-স্বাভাবিক রাজনৈতিক নেতা তৈরি হবে না। প্রকৃত ছাত্রনেতা তৈরি হবে নির্বাচনের মাধ্যমে, তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকবে সচেতন শিক্ষকরা। চর্চা করবে সাহিত্য-সংস্কৃতি, রাষ্ট্র নিয়ে করবে পড়াশোনা, নানা বিষয়ে আয়োজন করবে বিতর্ক।
কিন্তু বর্তমান ছাত্র রাজনীতিতে সে চর্চা হয় না। শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই শিক্ষার্থীদের, বরং কিছু শিক্ষক ছাত্রদের গুণ্ডামিতে প্রশ্রয় দেয় নিজেদের সুবিধার জন্য। আর ছাত্ররা সেভাবেই চলে এবং তারা কেবল বড় দলের হয়ে কাজ করে। এভাবে লেজুড়বৃত্তির রাজনৈতিক চর্চা অস্বাভাবিক পরিবেশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের এবং তাদের।
দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হচ্ছে রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে। এই রাজনীতি দেশকে কোন পথে নিয়ে যাচ্ছে?
আবুল কাসেম ফজলুল হক: এটাকে বলা যায় মহাজনের রাজনীতি। বাংলাদেশের রাজনীতি অনেক দিন ধরেই অস্বাভাবিক অবস্থায় আছে। একদল বড় থেকে আরও বড় হচ্ছে। অর্থের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় নেতারা লিপ্ত। কারও মধ্যে দেশ নিয়ে ভাবনা-ভালোবাসা নেই। কৃষক সারাদিন পরিশ্রম করে অল্প ভোগ করতে পারে, বাকিটা ছেড়ে দিতে হয়। নেতারা গরীব মানুষের জীবনকে রীতিমতো ভোগ করে।
বাস্তবতা হচ্ছে ভালো-মন্দ মিলিয়ে আওয়ামী লীগই বেশি শক্তিশালী এবং মনে হচ্ছে তারা আরও অনেক দিন ক্ষমতায় থাকবে। তাদের হাতে সুযোগ আছে পরিবর্তনের এবং সেটা কেবল পারবে শেখ হাসিনা। তার মতো ক্ষমতা দেশে আর কারও নেই।
অনেক বাবারা সন্তান হারিয়ে বিচারের দাবিতে ঘুরছেন। আপনি নিজ সন্তান হারিয়ে কেন বিচার চাইলেন না?
আবুল কাসেম ফজলুল হক: আমি কেন বিচার চাইব? আমার সন্তান দীপন কি ব্যক্তিগত কারণে হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে? পারিবারিক কারণে খুন হয়েছে? এমন হলে আমি বিচার চাইতাম।
আমার সন্তানকে মুক্তবুদ্ধি-চর্চার জন্য হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করে বিচারের দায়িত্ব তো রাষ্ট্রের। আমি না চাইলেও তো রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব পালন করবে। আইনকে গতিশীল রাখবে।
সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা কোটা বহাল রেখেছেন হাইকোর্ট। তরুণদের একটা বড় অংশ এর প্রতিবাদ করছেন। এ বিষয়টি নিয়ে আপনার মতামত জানতে চাই।
আবুল কাসেম ফজলুল হক: হাইকোর্ট রায় দিলেই সে বিষয়টা ন্যায়সঙ্গত হবে এমনটা মনে করার কারণ নেই। মনে রাখতে হবে একাত্তরে যারা প্রাণ দিয়েছেন তারা কখনো কোনো কিছুর বিনিময়ে চাননি। মানে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল হবে এমন চিন্তায় মুক্তিযুদ্ধ করেননি। তথাপি স্বাধীনতা পরবর্তী সরকার শহীদ পরিবার এবং আহতের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কোটা চালু করে। পারিবারিক সংকট তথা এক ধরনের নিরাপত্তার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কিন্তু বর্তমানে সেই অবস্থা নেই। কোটার রেওয়াজ দীর্ঘস্থায়ী হবে— এমনটি অপ্রত্যাশিত।
তারপরও মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সন্তানের জন্য কোটার সুবিধা মানা যায়। কিন্তু ছেলে-মেয়ের ঘরে নাতির সুবিধা বেমানান। এতে সামাজিক বৈষম্য বাড়ছে। অনাদিকাল ধরে এই কোটা পদ্ধতি চলতে পারে না। এতে যারা দেশের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, স্বাধিকার, স্বনির্ভরতা চেয়েছেন— তাদের আত্মাও কষ্ট পাবে।
জাতীয় নির্বাচনের পরে উপজেলা নির্বাচন নিয়েও ভোটারদের তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। গণতান্ত্রিক একটা দেশে এমন ভোট বিমুখতা কী বার্তা দেয়?
আবুল কাসেম ফজলুল হক: দেশের কোনো রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতন্ত্র নেই, গণতন্ত্র নেই আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও। তাহলে জাতীয় নির্বাচনে সবার অংশগ্রহণ কীভাবে হবে? এমন নির্বাচনে জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনা কেন থাকবে? গণতন্ত্র আশা করলে তার একটি ধারাবাহিক চর্চা থাকতে হবে। এরপর এর ফল আসবে ধীরে ধীরে।
অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে সাধারণ মানুষেরও কোনো আওয়াজ নেই। তারা ঘুমন্ত। মনে রাখতে হবে ভোগবাদী ও সুবিধাবাদী নেতৃত্বের দ্বারা সুষ্ঠু নির্বাচন কিংবা জাতীয় সমস্যার সমাধান হবে না। বরং নেতৃত্বের সংকটে পড়বে আগামী।
ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিয়ে মোদি সরকার ব্যাপক সমালোচিত হয়েছে। তার প্রভাব পড়েছে ভারতের জাতীয় নির্বাচনেও। এ বিষয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ কী?
আবুল কাসেম ফজলুল হক: ধর্মকে ব্যবহার করে কেউ বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে প্রকৃত অর্থে তরুণ কিংবা প্রগতিশীল প্রজন্ম কখনোই গ্রহণ করে না।
তার উদাহরণ ভারতের এবারের নির্বাচন। ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে সেখানকার তরুণ প্রজন্ম প্রত্যাখ্যান করেছে। এটি তাদের দেশের রাজনৈতিক নেতাদের জন্য শিক্ষা। আমাদের জন্যও বটে।
বাংলাদেশ বস্তুত কোন দিকে যাচ্ছে?
আবুল কাসেম ফজলুল হক: আমরা খুব খারাপ সময় পার করছি। সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষা সবখানেই সংকট। কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সবাই চুপ। মিডিয়া কেবল প্রশংসা করে, উন্নয়ন দেখে। ব্যবসায়ী মালিক যেভাবে বলে সাংবাদিকরা সেভাবে চলে। নিজেদের কোনো বিবেচনা নেই।
দুয়েকটি পত্রিকা কিছু লেখে, বলে। সেগুলোর কোনো প্রভাব নেই, উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া নেই। কার্যকারিতা নেই সমাজে।
আমি মনে করি জনগণের জেগে ওঠা উচিত। আমরা দেখেছি জনগণ যখন বিবেকবুদ্ধি দিয়ে সংঘবদ্ধ হয়েছে তখন সেই শক্তির সামনে কোথাও কোনো অত্যাচারী শাসক, কোনো যুদ্ধবাজ শক্তি টিকতে পারেনি। কেননা জনগণ পারমাণবিক বোমার চেয়েও শক্তিশালী। জনগণ জাগলে কোনো অপশক্তিই তাকে পরাজিত করতে পারে না।
ঈদ কী সবার মাঝেই সমান হয়ে আসে?
আবুল কাসেম ফজলুল হক: না, বাজারের কারণে মানুষের মনে আনন্দ নেই আর। জিনিসপত্রের যে দাম তাতে তারা কী খাবে, কীভাবে চলবে? লোক দেখানো কোরবানি করে অনেকে। কিন্তু প্রতিবেশীর প্রতি খেয়াল রাখে না, যেভাবে রাখে না রাষ্ট্র। অথচ ঈদের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। এটা কেউ মন দিয়ে অনুভব করে না।
গুগলের বিচার শুরু হচ্ছে, ভেঙেও যেতে পারে এই কোম্পানি
গুগলের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে বিজ্ঞাপন ব্যবসা। এবার সেই বিজ্ঞাপন ব্যবসাকে লক্ষ্যবস্তু করেছে মার্কিন সরকার। অভিযোগ, গুগল এই লাভজনক বিজ্ঞাপন প্রযুক্তির ব্যবসায় একচেটিয়াত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। আজ সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের এক আদালতে এ–সংক্রান্ত বিচার শুরু হবে।
বিবিসি জানায়, ২০২৩ সালে গুগল অনলাইন বিজ্ঞাপন ব্যবসা থেকে ২০০ বিলিয়ন বা ২০ হাজার কোটি ডলার রাজস্ব আয় করেছে। এই খাতের অন্যান্য কোম্পানির সঙ্গে গুগলের আয়ের ব্যবধান যোজন যোজন। সে কারণে অনেক দিন থেকেই গুগলের মূল কোম্পানি অ্যালফাবেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এই অনলাইন বিজ্ঞাপনের জগতে গুগল একচেটিয়া ব্যবসা করছে।
অ্যালফাবেট অবশ্য একচেটিয়া ব্যবসার অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। তারা বলেছে, এই ব্যবসায় তাদের কৌশল অত্যন্ত কার্যকর; সে কারণে তাদের এই বাড়বাড়ন্ত। এখানে একচেটিয়াত্বের কিছু নেই। কিন্তু সরকার বলছে, গুগল বাজারে তার প্রভাব খাটিয়ে প্রতিযোগীদের দমিয়ে রাখছে।
জর্জিয়া স্কুল অব লর অধ্যাপক লরা ফিলিপস সোয়্যের বলেন, এই শিল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ; প্রতিদিন শত শত কোটি মানুষ এই জগতে বিচরণ করে। সে কারণে এই মামলা জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বলে মনে করেন তিনি।
যুক্তরাষ্ট্রের বড় কোম্পানিগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় কোম্পানি হিসেবে গুগলের বিরুদ্ধে অ্যান্টি–ট্রাস্ট বা প্রতিযোগিতা ভঙ্গের মামলা হলো। আগস্ট মাসেই যুক্তরাষ্ট্রের এক বিচারক বলেছেন, অনলাইন সার্চ বা অনুসন্ধানের বাজারে গুগলের প্রভাব অবৈধ।
বিচার বিভাগ ও কোয়ালিশন অব স্টেটসের মামলার বিবরণে বলা হয়েছে, ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের রাজ্যে গুগলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাজারে তার যে প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, তা দিয়ে গুগল এই বাজারে অন্যদের উঠতে দেয় না বা তাদের টুঁটি চেপে ধরে ও প্রতিযোগিতা রুদ্ধ করে।
কিন্তু গুগল বলছে, এই ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের জগতে শত শত কোম্পানি আছে। প্রতিদিন তারা কোটি কোটি গ্রাহকের সামনে এসব বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে, গুগল সেই কোম্পানিগুলোর মধ্যে একটি।
গুগল আরও বলেছে, ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের জগতে প্রতিযোগিতা বাড়ছে। অর্থাৎ বিজ্ঞাপনদাতারা আরও বেশি ডিজিটালমুখী হচ্ছেন। শুধু গুগল নয়, অন্যান্য কোম্পানি যেমন অ্যাপল, আমাজন ও টিকটকের মতো কোম্পানির বিজ্ঞাপনী রাজস্ব বাড়ছে।
উভয় পক্ষই আজ যুক্তরাষ্ট্রের এক ডিস্ট্রিক্ট আদালতে নিজেদের যুক্তি ও সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করবে। এর আগে গত মাসেই যুক্তরাষ্ট্রের সেই আদালত রুলিংয়ে বলেছেন যে অনলাইন বিজ্ঞাপনের জগতে গুগল একচেটিয়া হয়ে উঠেছে। তারা এখন অন্যান্য কোম্পানির টুঁটি চেপে ধরার চেষ্টা করছে। বিচারক আরও বলেন, গুগল এখন একচেটিয়া কোম্পানি হিসেবে কাজ করছে।
গুগল বরাবর যা বলে, গত মাসের রায়ের পরও তাই বলেছে, গুগলের পণ্য অন্যদের চেয়ে ভালো; সে জন্য তাদের বিজ্ঞাপনী রাজস্ব আয় অন্যদের চেয়ে বেশি।
গুগল কি ভেঙে যাবে
গত মাসের সেই রুলিংয়ে আরও বলা হয়, ইন্টারনেটের জগতে নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে যা যা করা দরকার, গুগল তার সবই করেছে এবং সম্ভাব্য প্রতিযোগীদের কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। এরপর কী ঘটে, এখন সেটাই দেখার বিষয়। সেই রুলিং টিকে গেলে মার্কিন সরকার গুগলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে; এমনকি তারা গুগলের মতো কোম্পানিকে ভেঙেও দিতে পারে। সেটা হলে বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের অ্যান্টি–ট্রাস্ট আইনের অধীনে সবচেয়ে বড় ঘটনা হবে। ১৯৮০-এর দশকে সে দেশের কিছু টেলিকম কোম্পানি এবং ২০ শতকের শুরুর দিকে একাধিক তেল কোম্পানি এ আইনের অধীনে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল।
গুগল ভেঙে দেওয়া হলে বিনিয়োগকারীদের কাছে তা বড় ঘটনাই হবে। অ্যালফাবেট বড় এক কোম্পানি। এই কোম্পানির বাজার মূলধন দুই ট্রিলিয়ন বা ২ লাখ কোটি মার্কিন ডলারের বেশি, আর তার ব্যবসার মূল হাতিয়ার হচ্ছে গুগল। বিশ্বের খুব কম মানুষ ও কোম্পানি আছে, যারা কোনো না কোনোভাবে গুগলের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।
এই কোম্পানি কীভাবে ভেঙে দেওয়া হবে এবং এরপর তারা মুনাফা ধরে রাখতে পারবে কি না এবং বাজারে তার বড় প্রভাব পড়বে কি না, এসব প্রশ্ন উঠেছে। তার চেয়ে বড় কথা, সারা পৃথিবীতে এখন যেভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হচ্ছে, তাতে পরিবর্তন আসবে।
যুক্তরাষ্ট্রের বাজার বিশ্লেষক ড্যান ইভেস বলেন, গুগলের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের বড় বিজয় হতে যাচ্ছে। এই সফলতা ব্যবহার করে সরকার সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নেবে বলে মত দেন তিনি। তাঁর মতে, গুগল ভেঙে দেওয়া সমাধান নয়।
অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের আরেক আদালত মনে করে, ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের এই খুঁটিনাটি বিষয় খুবই জটিল; সে কারণে বিচার বিভাগের পক্ষে রায় দেওয়া কঠিন হতে পারে। অ্যান্টি–ট্রাস্ট বিষয়ের আইনের শিক্ষক রেবেকা অ্যালেন্সওর্থ বলেন, মানুষ সার্চ ইঞ্জিন বোঝে। কিন্তু বিজ্ঞাপন প্রযুক্তি অনেক জটিল, এটা সবার বোধগম্য নয়।
প্রযুক্তির জগতে একচেটিয়া
একচেটিয়াতন্ত্রের অভিযোগ কেবল গুগলের বিরুদ্ধে নয়, অন্যান্য বড় কোম্পানির বিরুদ্ধেও আছে। চলতি বছর প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠান অ্যাপলের বিরুদ্ধেও স্মার্টফোনের বাজারে একচ্ছত্র আধিপত্য ধরে রাখা ও বাজার থেকে প্রতিযোগীদের হটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি এই অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মামলাও হয়েছে।
গত কয়েক বছরে ইন্টারনেটের জগতে গুগলের প্রাধান্য অবশ্য কিছুটা খর্ব হয়েছে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআইভিত্তিক চ্যাটজিপিটি আসার পর গুগলের প্রাধান্য কিছুটা কমেছে। এই প্রতিযোগিতায় গুগল কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে। তবে বিজ্ঞাপনের ব্যবসা দিয়ে সেই ক্ষতি তারা কাটাতে পারছে।
কিন্তু গত মাসে আদালতের রুলিংয়ের পর গুগল সম্ভবত তার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে। এরপর আজ থেকে শুরু হওয়া বিচারে কী রায় হয়, মানুষ সেদিকে তাকিয়ে থাকবে।
১১ ট্রিলিয়ন ডলারের বিশ্ব পর্যটন শিল্প, নতুন রেকর্ড
চলতি বছর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে একজন মানুষের প্রতি ১০ ডলারের এক ডলার খরচ হচ্ছে পর্যটনে। এই খরচ যাচ্ছে হোটেল বুকিং প্রমোদতরী ও উড়োজাহাজ বুকিংয়ে। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ট্রাভেল অ্যান্ড টুরিজমের (ডব্লিউটিটিসি) বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, জনসম্পৃক্ততা বেড়ে যাওয়ায় বৈশ্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে পর্যটন শিল্প খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।
ডব্লিউটিটিসির তথ্য মতে, চলতি বছর বৈশ্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে পর্যটনের অবদান এর আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২ দশমিক এক শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১১ দশমিক এক ট্রিলিয়ন ডলার। ২০১৯ সালের হিসাবে এই প্রবৃদ্ধি সাড়ে সাত শতাংশ।
ডব্লিউটিটিসির প্রধান নিবার্হী জুলিয়া সিম্পসন বার্তা সংস্থাটিকে বলেন, 'গত বছর বেশকিছু কারণে বৈশ্বিক মন্দা ও উচ্চ মূল্যস্ফীতি সত্ত্বেও পর্যটন খাত এখন বিশ্বব্যাপী প্রকৃত অর্থনৈতিক কেন্দ্র।'
বৈশ্বিক পর্যটনে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জার্মানির অবদান বাড়ছে বলেও প্রতিবেদেন উল্লেখ করা হয়েছে।
এতে আরও বলা হয়, চলতি বছর পর্যটন খাতে কর্মসংস্থান ৩৪৮ মিলিয়ন। ২০১৯ সালের তুলনায় এই সংখ্যা ১৩ দশমিক ছয় মিলিয়ন বেশি।
পর্যটকদের বাড়তি চাপ সামলাতে এই খাতে কর্মসংস্থান ক্রমাগত বাড়ছে।
ইউএস ট্রাভেল অ্যাসোসিয়েশনের হিসাবে, যুক্তরাষ্ট্রে পর্যটন খাতে বর্তমানে আরও এক মিলিয়ন মানুষের কাজের সুযোগ আছে। গত বছর এই খাতে কর্মরত ছিলেন ২৭ মিলিয়ন মানুষ।
যেভাবে কুৎসিত হয়ে উঠল একটি সুন্দরী প্রতিযোগিতা
ঘটনাটি দ্বীপরাষ্ট্র ফিজির। সেখানকার পার্ল রিসোর্ট অ্যান্ড স্পাতে আয়োজন করা হয়েছিল সুন্দরী প্রতিযোগিতা। উদ্দেশ্যে দেশের সেরা সুন্দরী নির্বাচন করা, যিনি প্রতিনিধিত্ব করবেন নভেম্বরে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠেয় মিস ইউনিভার্স সুন্দরী প্রতিযোগিতায়।
গত ৩০ আগস্ট চূড়ান্ত বিজয়ী ঘোষণা করার দিন ধার্য ছিল। ঘোষণা অনুযায়ী ওই দিন রাতে চূড়ান্ত পর্বের আয়োজন করা হয়। সবকিছু ঠিকঠাকই এগোচ্ছিল। ফুলেরতোড়া হাতে মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা মানশিকা প্রসাদকে সেরা সুন্দরীর মুকুট পরিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু এর কিছু সময় পরই সুন্দরী প্রতিযোগিতার বিষয়গুলো যেন কুৎসিত পর্বে রূপ নিল।
পরবর্তী কয়েক দিনে ঘটল নানা নাটকীয় ঘটনা। ছিনিয়ে নেওয়া হল সুন্দরীকে পরানো সেই মুকুট। উঠল ভিত্তিহীন অনেক অভিযোগ। আবির্ভাব ঘটল একজন প্রতিযোগীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা রহস্যময় একজন ব্যক্তির।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিজয়ী ঘোষণার দু’দিন পর আয়োজক সংস্থা মিস ইউনিভার্স ফিজি একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দেয়। এতে যেন সবকিছু ওলট-পালট লাগে ২৪ বছর বয়সী এমবিএ শিক্ষার্থী মানশিকার কাছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিযোগিতার ‘নীতিমালায় গুরুতর লঙ্ঘন’ হয়েছে। শিগগিরই ‘সংশোধিত ফল’ ঘোষণা করা হবে।
এর কয়েক ঘণ্টা পর মানশিকাকে বলে দেওয়া হয়, মিস ইউনিভার্স সুন্দরী প্রতিযোগিতায় তার যাওয়া হচ্ছে না। তার স্থলাভিষিক্ত হবেন প্রতিযোগিতায় রানারআপ হওয়া সিডনির বাসিন্দা নাদিন রবার্টস। ৩০ বছর বয়সী এই মডেল ও আবাসন ব্যবসায়ীর মা ফিজির নাগরিক।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অভিযোগ করা হয়, প্রতিযোগিতায় ‘সঠিক প্রক্রিয়া’ মানা হয়নি। ভোট কারচুপির মাধ্যমে মানশিকাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। অনুষ্ঠান আয়োজকেরা আর্থিক সুবিধা পেতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত একজন প্রতিযোগীকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে।
ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল মানশিকা এক বিবৃতিতে জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে তিনি কিছু সময়ের জন্য বিরতি নেবেন। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, ঘটে যাওয়া অনেক কিছু সম্পর্কেই সাধারণ মানুষ জানে না।
এদিকে ‘দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য’ মিস ইউনিভার্স ফিজিকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিজের ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দেওয়ার আগে সংহতি জানিয়ে দেওয়া বার্তায় নতুন বিজয়ী নাদিন বলেন, “এ ঘটনার নেতিবাচক প্রভাব আমাদের সবার ওপরই পড়েছে।”
যেভাবে কুৎসিত রূপ নেয় সুন্দরী প্রতিযোগিতা
সাত বিচারকের একজন ছিলেন মেলিসা হোয়াইট। তিনি বলেন, সবকিছু ঠিকমতোই চলছিল। আরেকজন বিচারক জেনিফার চান বলেন, এই পর্যায়ে মানশিকা সুস্পষ্ট বিজয়ী ছিলেন। তাকে ৪-৩ ভোটে প্রথমে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছিল।
তবে চানের মতে, সদ্য জয়ী মিস ইউনিভার্স ফিজি যখন মুকুট মাথায় মঞ্চে দাঁড়ান, তখন বিচারকেরা বুঝতে পেরেছিলেন কোথাও যেন ঘাপলা আছে। তার ডান দিকে রানারআপ উত্তরীয় পরা নাদিনকে ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছিল।
পরদিন বিচারকদের সঙ্গে নৌভ্রমণে যান মানশিকা। যদিও তখনও দাফতরিকভাবে মানশিকার বিজয় নিশ্চিত করা হয়নি। শুধু তা–ই নয়, ওই ভ্রমণে বিচারকদের একজন রিরি ফেবরিয়ানি অনুপস্থিতি ছিলেন, যা ছিল চোখে পড়ার মতো একটি ঘটনা। তিনি লাক্স প্রজেক্টসের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। এই কোম্পানি মিস ইউনিভার্স ফিজি আয়োজনের লাইসেন্স কিনেছিল।
বিচারক মেলিসা বলেন, “আমার কাছে বিষয়টি অদ্ভুত ঠেকছিল।” ফেবরিয়ানির সঙ্গে একই কক্ষে ছিলেন তিনি। মেলিসা বলেন, “কিন্তু তিনি (ফেবরিয়ানি) শুধু বলতেন তাকে অনেক কাজ করতে হবে এবং তার বসের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন।” বিশ্রামের কথা বলে তিনি নৌভ্রমণেও যোগ দেননি।
ফেবরিয়ানি ফোনে কার সঙ্গে বার্তা আদান-প্রদান করছেন, অন্য কারও সেটা জানার উপায় নেই। তবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তার কক্ষসঙ্গী ‘জ্যামি’ নামের একজনের সঙ্গে অনবরত বার্তা আদান-প্রদান ও ফোনে কথা বলে যাচ্ছেন।
আবাসন কোম্পানি লাক্স প্রজেক্টসের প্রতিনিধি হিসেবে বিচারক প্যানেলে ছিলেন ফেবরিয়ানি। কিন্তু তিনি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টিও দেখতেন। ফেবরিয়ানি বিচারক প্যানেলে থাকার পরও ভোটের ফলাফলে খুশি হতে পারেনি কোম্পানিটি।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে লাক্স প্রজেক্টস বলে, লাইসেন্স পাওয়া প্রতিষ্ঠানের একটি ভোট থাকা উচিত। আর চুক্তিবদ্ধ আয়োজক গ্র্যান্ট ডোয়ার সেই ‘ভোট গুনতে ব্যর্থ হয়েছিলেন’। লাক্স প্রজেক্টস নাদিনকে ভোট দিত, এতে ফলাফল ৪-৪–এ সমতায় থাকত। এছাড়া কোম্পানিটি বলেছে, এ অবস্থায় লাইসেন্স পাওয়া প্রতিষ্ঠানেরই ‘নির্ধারক ভোট’ আছে, যা নাদিনকে জয়ী করে।
কিন্তু বিচারক চান বলেন, “প্রতিযোগিতার কোনও পর্যায়েই আমাদেরকে অষ্টম বিচারক সম্পর্কে কিংবা কোনও অনুপস্থিত বিচারক সম্পর্কে বলা হয়নি।”
তিনি বলেন, “এটা ওয়েবসাইটেও ছিল না, কোথাও বলা হয়নি। এছাড়া আপনি একটি প্রতিযোগিতার সময় না থেকে কীভাবে ভোট দিতে পারেন?”
বিচারক মেলিসার কিছুটা খটকা লাগল। তিনি বলেন, কিছুটা খোঁজ নিয়ে দেখতে পান, লাক্স প্রজেক্টসের সঙ্গে জ্যামি ম্যাকইন্টায়ার নামের অস্ট্রেলিয়ার এক ব্যবসায়ী ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আর নাদিনের সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্পর্ক রয়েছে।
অনলাইনে পাওয়া তথ্যানুযায়ী নিজেকে উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারী হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন জ্যামি। ২০২২ সাল থেকে নাদিনের সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্পর্ক। প্রতারণামূলক আবাসন প্রকল্পে বিনিয়োগের কারণে ২০১৬ সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ব্যবসা করার বিষয়ে তার ওপর এক দশকের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়। সূত্র: বিবিসি