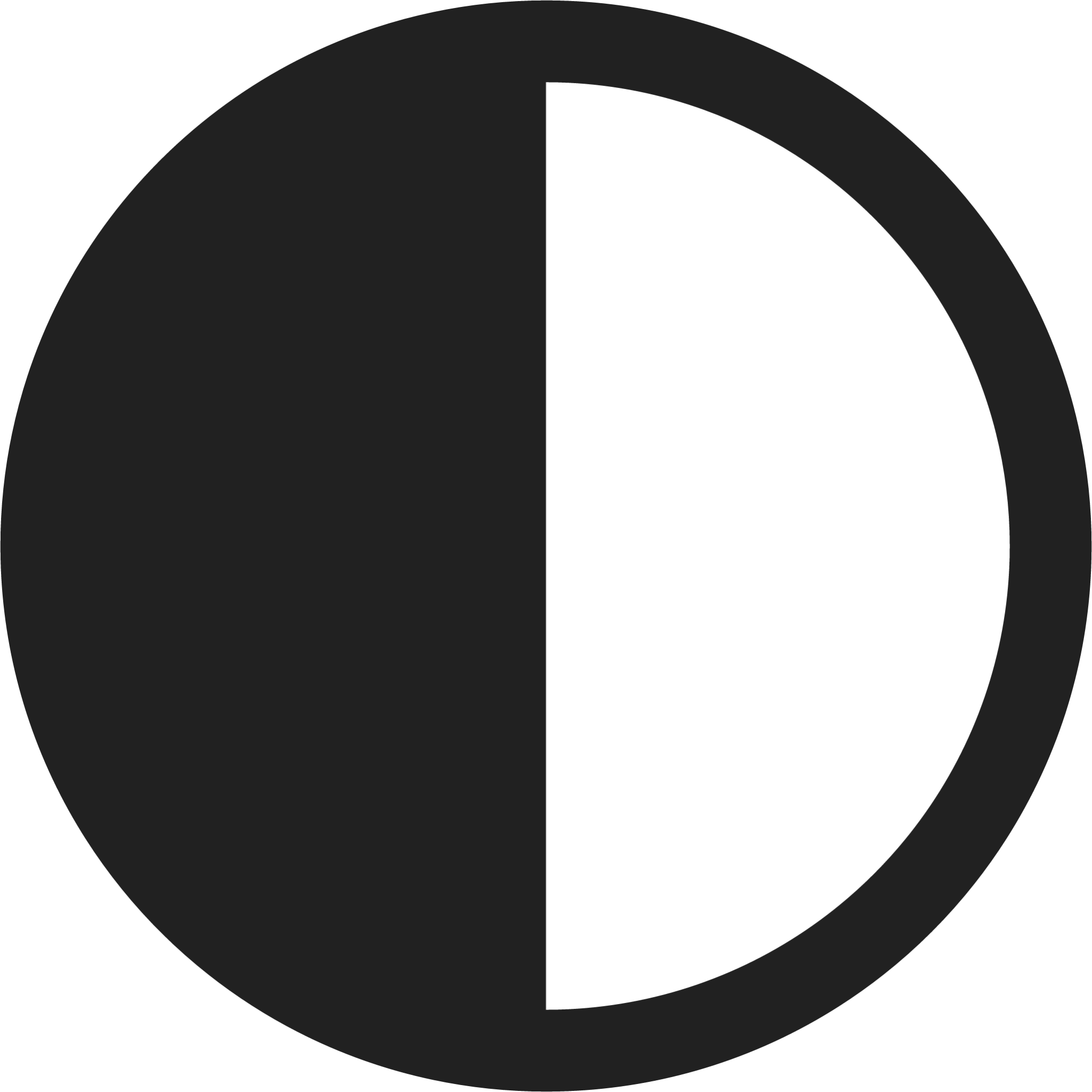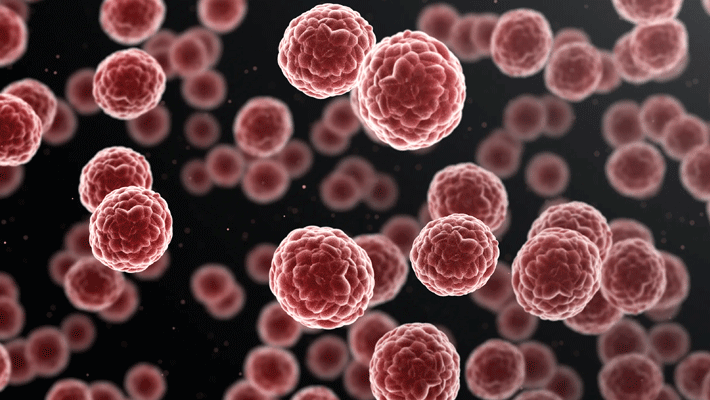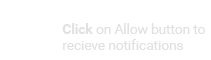ভারতের ভিসা নিষেধাজ্ঞা: দেশের স্বাস্থ্যসেবা সংস্কারের এখনই সময়
বাংলাদেশিদের জন্য ভারতের ভিসা নিষেধাজ্ঞাকে প্রাথমিকভাবে বাধা হিসেবে দেখা হলেও এটি দেশের স্বাস্থ্য খাতকে শক্তিশালী করা ও রোগীদের আস্থা ফিরিয়ে আনার সুবর্ণ সুযোগ হয়ে উঠেতে পারে।
প্রতি বছর প্রায় সাড়ে তিন লাখ বাংলাদেশি ভারতে চিকিৎসা নিতে যান। ভিসা বিধিনিষেধ দেশের স্বাস্থ্য খাতে সমস্যাগুলোর সমাধান ও বিদেশে যাওয়া রোগীদের দেশে চিকিৎসা দেওয়ার সুযোগ এনে দিয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে এই সুযোগে উঠে দাঁড়াতে ও দেশবাসীর মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন।
২০২০ সালে গুরুতর অসুস্থ মিরপুরের সানজিদার (আসল নাম নয়) কথা ধরা যেতে পারে। ডিম্বাশয়ের সিস্ট অপসারণের জন্য ঢাকার গ্রিন লাইফ হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের পর তার বায়োপসি রিপোর্টে দুঃসংবাদ পাওয়া যায়: তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত।
তাকে কেমোথেরাপির পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। তিনি চিকিৎসকের সুপারিশ অনুসারে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য গেলে দেখেন যে তার আগের পরীক্ষাগুলোকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। সেসময় এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে তার চিকিৎসক বিষয়টিকে মোটেও গুরুত্ব দিচ্ছেন না। আতঙ্কিত ও হতাশ হয়ে তার পরিবার বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
সানজিদা মুম্বাইয়ের টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে গিয়েছিলেন। যেখানে চিকিৎসকরা তার আগের চিকিত্সা পর্যালোচনা করে রোগ নির্ণয় করেছিলেন। তারা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ঢাকায় অস্ত্রোপচার ভুল ছিল। উপযুক্ত অপারেশন হলে তার ক্যানসার আগেই দূর করা যেত।
মুম্বাইয়ে আরও একটি অস্ত্রোপচার ও তিন দফা কেমোথেরাপি শেষে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন। বর্তমানে তিনি নিয়মিত ওষুধ খান এবং ফলোআপের জন্য প্রতি ছয় মাস পর পর ভারতে যান। তার এই চরম দুর্গতি এ কথাই প্রমাণ করে যে, সানজিদা নিজ দেশে যথাযথ চিকিৎসা পাননি। তিনি এ দেশের চিকিৎসকদের অমনোযোগিতা ও অপেশাদারিত্বের কথা তুলে ধরে জানান যে ভারতের চিকিৎসকরা রোগীদের অনেক যত্ন নিয়ে দেখেন।
সানজিদা দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, 'যাতায়াতের খরচ বেশি হলেও দেশের তুলনায় ভারতে কম টাকায় চিকিৎসা নেওয়া যায়। সেখানকার চিকিৎসা তুলনামূলক বিশ্বাসযোগ্য।'
এমন ঘটনা শুধু সানজিদারই নয়। ২০১৯ সালে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা শহিদুর রহমান (৬৯) বুকে ব্যথা অনুভব করলে চিকিৎসকের কাছে যান। ঢাকার দুই বড় হাসপাতাল তার হার্টে তিনটি ব্লক আছে জানিয়ে স্টেন্ট বসানোর পরামর্শ দেয়। তাদের কথায় সন্দেহ হয় শহিদুরের। তিনি প্রখ্যাত হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. দেবী শেঠির পরামর্শ নিতে বেঙ্গালুরু যান। পরীক্ষার পর দেখা যায় হার্টে ব্লক নেই। তাকে ওষুধ দেওয়া হয়। এরপর তার আর বুকের ব্যথা হয়নি। তিনি দেশের স্বাস্থ্যসেবায় আস্থা হারান।
আস্থার সংকট
বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো আধিপত্য বিস্তার করে আছে। তৃতীয় শ্রেণির হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সংখ্যা অনেক বেশি।
সানজিদা ও শহিদুরের ঘটনাগুলো দেশের স্বাস্থ্যখাতে গভীর সংকটের দুইটি উদাহরণ মাত্র। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রোগীদের আস্থাহীনতায় জর্জরিত। আপাতদৃষ্টিতে দেশের স্বাস্থ্যসেবা অবকাঠামো শক্তিশালী বলে মনে হয়। দেশে ৫৬৬টি সরকারি হাসপাতাল আছে। এর মধ্যে ৩৭টি রাষ্ট্র পরিচালিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার।
বেসরকারি বিনিয়োগের ফলে তৃতীয় শ্রেণির হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সংখ্যা বেড়েছে। তাই স্বাস্থ্যসেবায় অগ্রগতি ধোঁয়াশা তৈরি করেছে। অনেক বাংলাদেশি এখনো বিদেশে চিকিত্সা নিতে বাধ্য হচ্ছেন। রোগীদের বিশ্বাস দেশের বর্তমান পরিষেবা তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারে না।
রোগীদের বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার কারণ অনেক। দেশে চিকিৎসকরা তাড়াহুড়ো করে পরামর্শ দেন, রোগ নির্ণয়ে ত্রুটি থাকে। চিকিত্সা খরচ অনেক। এ ছাড়াও, রোগীদের প্রতি চিকিত্সকদের উদাসীনতার অভিযোগ আছে। অনেকের অভিযোগ, চিকিৎসকরা রোগীদের সঙ্গে 'অমানবিক' আচরণ করেন।
বিপরীতে, অনেক রোগীর মতে ভারত চিকিত্সা সেবায় শুধু যে দক্ষ তা নয়। সেখানকার চিকিৎসকরা রোগীদের এমন যত্ন নেন যে তারা সেই আচরণকে মানবিক বোধ করেন।
ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিন প্রকাশিত ২০২৩ সালের সমীক্ষা অনুসারে—বাংলাদেশি রোগীরা প্রাথমিকভাবে কার্ডিওলজি (১৪ শতাংশ), অনকোলজি (১৩ শতাংশ), গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি (১১ শতাংশ) ও অন্যান্য জটিল সমস্যার চিকিৎসা করাতে ভারতে যান।
প্রতিবেদনে দেখা গেছে—দক্ষ বিশেষজ্ঞ, ফলো-আপ ও যত্নসহ ভারতের স্বাস্থ্যসেবা বছরে আনুমানিক তিন লাখ থেকে সাড়ে তিন লাখ বাংলাদেশি রোগী টানে। কলকাতা, চেন্নাই, ভেলোর ও মুম্বাইয়ে সবচেয়ে বেশি বাংলাদেশি রোগী যান।
স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রুমানা হক ডেইলি স্টারকে বলেন, 'দেশের স্বাস্থ্যসেবায় পর্যাপ্ত দক্ষ চিকিৎসক ও প্রযুক্তিবিদের অভাব। বিশেষ করে ক্যানসার ও অঙ্গ প্রতিস্থাপনের মতো জটিল রোগের জন্য। আমাদের দক্ষ চিকিৎসক থাকলেও তারা অনেক চাপে থাকেন। তাই রোগীদের প্রত্যাশা অনুযায়ী সেবা দিতে পারছেন না।'
ভারত ও থাইল্যান্ড প্রথম পছন্দ হওয়ায় বাংলাদেশি রোগীরা বিদেশে চিকিৎসার জন্য বছরে পাঁচ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি খরচ করেন। রুমানা হক মনে করেন, 'দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো যদি রোগীদের সেবা ভালোভাবে দেন তাহলে বিদেশে যাওয়া অনেক কমানো যেতে পারে।'
এভারকেয়ার হসপিটালস ঢাকার ক্লিনিক্যাল অ্যান্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি বিশেষজ্ঞ তামজেদ আহমেদ ডেইলি স্টারকে বলেন, 'গত দুই থেকে তিন মাসে ভারতে পরামর্শ নিতে যাওয়া রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। ভারতের ভিসা বিধিনিষেধ সত্ত্বেও তা বাড়ছে।'
স্কয়ার হাসপাতালের চিফ অপারেটিং অফিসার মো. এসাম ইবনে ইউসুফ সিদ্দিকী এই বিধিনিষেধের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবকে ঘিরে অনিশ্চয়তার কথা তুলে ধরে ডেইলি স্টারকে বলেন, 'গত তিন বছরে স্কয়ার হাসপাতালে রোগীর সংখ্যায় তেমন পরিবর্তন হয়নি।'
পদ্ধতিগত সংকট ও রোগীর অসন্তুষ্টি
রোগীরা প্রায়ই বাংলাদেশের অপ্রতুল ডায়াগনস্টিক সুবিধার কথা বলেন। এমনকি উন্নত যন্ত্রপাতিতে সাজানো বেসরকারি হাসপাতালগুলো কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাব আছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সৈয়দ আবদুল হামিদ ডেইলি স্টারকে বলেন, 'যথাযথভাবে রোগ নির্ণয়ে অসুবিধা, পরামর্শের জন্য চিকিৎসকের অপর্যাপ্ত সময় ও উদাসীন আচরণ রোগীদের আস্থা নষ্ট করেছে। ভারতের চিকিৎসকরা রোগীর সঙ্গে আলোচনায় দক্ষতা অর্জন করেছেন। তাদেরকে মানসিক সহায়তা দেন। বাংলাদেশে চিকিৎসকরা তাড়াহুড়ো করেন।'
করোনা মহামারির সময় যখন বিদেশে যাওয়া সীমিত ছিল তখন বাংলাদেশি রোগীদের দেশে চিকিৎসা নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। তখন অনেকে মানসম্পন্ন চিকিৎসা পেয়েছিলেন। তবে অবহেলা ও অদক্ষতার দীর্ঘ ইতিহাস রোগীদের বিদেশে যেতে বাধ্য করছে।
সংস্কারের আহ্বান
চিকিৎসা খাতের সংশ্লিষ্টরা এসব অসঙ্গতির কথা স্বীকার করেছেন। ল্যাবএইড হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা এএম শামীম ডেইলি স্টারকে বলেন, 'বাংলাদেশি চিকিৎসকরা কারিগরিভাবে দক্ষ হলেও তাদের আচরণ ভালো করতে হবে। রোগীদের আরও বেশি সময় দিতে হবে। জটিল রোগের চিকিৎসা করার সক্ষমতা আমাদের আছে, কিন্তু আচরণ ও পরামর্শ যথাযথ না হলে রোগীদের আস্থা নষ্ট হয়।'
একইভাবে আইচি মেডিকেল গ্রুপের অধ্যাপক মো. মোয়াজ্জেম হোসেন পদ্ধতিগত সংস্কারের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমাদের দক্ষ প্রযুক্তিবিদ, অভিন্ন খরচ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে পর্যাপ্ত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। রোগীদের এমন যত্ন দেওয়া দরকার যাতে তারা আত্মবিশ্বাসী হন এবং হাসপাতালগুলোকে তাত্ক্ষণিক মুনাফার তুলনায় রোগী-কেন্দ্রিক পরিষেবাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।'
ভারতের ভিসা বিধিনিষেধ অসুবিধাজনক হলেও বাংলাদেশকে চিন্তা-ভাবনা ও সংস্কারের বিরল সুযোগ এনে দিয়েছে। এটি রোগীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা, তাদের যত্নে সময় দেওয়া ও বিদেশে যেতে বাধ্য করে যেসব কারণ সেগুলো দূর করার সুযোগ এনে দিয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, এসব সমস্যার সমাধান না হলে দেশের মানুষ বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ার ওপর স্থায়ীভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।
ক্যান্সারের বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি কী, এগুলো কাজ করে?
অনেক ক্ষেত্রে সুপরিচিত ব্যক্তিরাও দাবি করেছেন, ক্যান্সার উপশমে প্রথাগত চিকিৎসার পাশাপাশি খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন বা বিকল্প চিকিৎসায় তারা উপকৃত হয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরোপুরি নিরাময়ও হয়েছেন।
তবে ক্যান্সারের চিকিৎসা দেয় এমন অনেক দাতব্য সংস্থা (চ্যারিটি) বলছে, কোনো থেরাপি বা বিকল্প উপায়ে ক্যান্সার চিকিৎসার মেডিক্যাল প্রমাণ তাদের কাছে নেই। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, এই বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি বা থেরাপিগুলো আসলে কী এবং এগুলোর ব্যবহার কীভাবে বাড়ছে?
ভারতের সাবেক ক্রিকেটার ও রাজনীতিবিদ নভজিৎ সিং সিধু গত নভেম্বরে জানান, তার স্ত্রী এখন পুরোপুরি ক্যান্সারমুক্ত। নিত্যদিনের খাবারে লেবুপানি, কাঁচা হলুদ, অ্যাপল সিডার ভিনেগার (সিরকা), নিমপাতা, তুলশি, মিস্টি কুমড়া, ডালিম, আমলকি, বিটরুট ও আখরোটের মতো উপাদান রেখেছিলেন তিনি।
সিধুর এই ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর ভারতের দুই শতাধিক ক্যান্সার রোগ বিশেষজ্ঞ এক যৌথ বিবৃতি দেন।
এতে তারা দাবি করেন, চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রাকৃতিক উপদানগুলোর প্রভাব নিয়ে গবেষণা চলছে, তবে এগুলোর ব্যবহারে সমর্থন করার মতো প্রমাণ তাদের হাতে নেই।
বরং 'অপ্রমাণিত' এসব উপাদান বা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতে গিয়ে ক্যান্সারের মূল চিকিৎসা বিলম্বিত না করতেও বিশেষজ্ঞরা সবার প্রতি আহ্বান জানান ওই বিবৃতিতে।
অস্ট্রেলিয়ান ডেল এলি ম্যাকফারসন গত সেপ্টেম্বরে জানান, সাত বছর আগে তার স্তন ক্যান্সার ধরা পড়েছিল। কেমোথেরাপির পরিবর্তে তিনি বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন।
চিকিৎসকরা বলছেন, স্তন ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কেমোথেরাপির পাশাপাশি বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে আকুপাংচার (শরীরের বিভিন্ন পয়েন্টে চাপ দিয়ে বা সুঁচ ফুটিয়ে চিকিৎসার পদ্ধতি), যোগ ব্যায়াম, মেডিটেশন (শরীর ও মনে শিথিল করার বিশেষ পদ্ধতি) ব্যবহার করেন অনেকে।
এগুলো ব্যথা দূর করতে এবং রোগীকে ভালো বোধ করতে সহায়ক হতে পারে। কিন্তু মেডিক্যাল ট্রিটমেন্ট বাদ দিয়ে কেবল ডায়েটে বিশেষ কোনো প্রাকৃতিক উপাদান বা মিনারেল, ভিটামিন যোগ করে নিরাময় লাভের চেষ্টার ব্যাপারে চিকিৎসকরা সতর্কও করে দিয়েছেন।
দাতব্য সংস্থাগুলো দাবি করছে, এসব বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির কোনো কোনোটা ক্ষতিকর হতে পারে বা মারাত্মক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হতে পারে, এমনকি মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টে বিঘ্নও ঘটাতে পারে।
ক্যান্সার বিষয়ক মেডিক্যাল জার্নাল জামা অঙ্কোলজিতে ২০১৮ সালে প্রকাশিত এক গবেষণায় দাবি করা হয়, বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করার কারণে রোগীদের ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে যাওয়ার হার কমে আসার সম্পর্ক রয়েছে।
কিন্তু এরপরও ক্যান্সার আক্রান্ত অনেকে এসব পদ্ধতির ওপর নির্ভর করছেন। এসব পদ্ধতির জনপ্রিয়তাও বাড়ছে।
ক্যান্সার চিকিৎসা সেবাদানকারী ব্যক্তিদের সংস্থা আমেরিকান সোসাইটি অব ক্লিনিক্যাল অঙ্কোলজি (এএসসিও)-এর এক জরিপে জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে ৪০ শতাংশের ধারণা বিকল্প পদ্ধতির চিকিৎসায় ক্যান্সার নিরাময় সম্ভব।
অনলাইনে 'ক্যান্সার-নিরাময়কারী' ডায়েট নির্দেশ করে তৈরি ভিডিওগুলো লাখ লাখ মানুষ দেখছেন এবং অ্যামাজনে এ ধরনের বইগুলো বিক্রি তালিকার শীর্ষে উঠে আসছে।
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্সে (আগের টুইটার) একটি থ্রেড ব্যাপক হারে শেয়ার করা হয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে প্রধানত খাদ্য তালিকায় পরিবর্তন এনেই ক্যান্সার 'প্রাকৃতিকভাবে' নিরাময় করা সম্ভব। ৪৮ ঘণ্টায় এই থ্রেডে দুই লাখ লাইক পড়ে।
ক্যান্সারকে 'অনাহারে' রাখতে রোগীদের উপবাস বা না খেয়ে থাকার কথা বলা হয় এতে। আরও বলা হয়, নির্দিষ্ট কিছু খাবার খাওয়ার মাধ্যমে 'ডিএনএ-কে প্রভাবিত' করে 'স্টেম সেলকে শক্তিশালী' করা যায়।
ম্যাকমিলান নামে একটি ক্যান্সার চ্যারিটি বলছে, কোনো বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বনের আগে ক্যান্সার চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
বিকল্প পদ্ধতির জনপ্রিয়তা কেন বাড়ছে?
কোনো ধরনের প্রমাণ ছাড়াই বিকল্প পদ্ধতি বা থেরাপিগুলোকে 'অলৌকিক আরোগ্য' বলে প্রচার করা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়।
ব্রিটিশ ক্যান্সার সার্জন ডক্টর লিজ ও'রিয়োর্ডান বলছেন, "ক্যান্সার একটি আতঙ্ক। এর ঝুঁকিসহ অন্যান্য বিষয়ে বলতে হবে আমাদের। রোগীরা আশা চান, আরোগ্যের অঙ্গীকার চান। কিন্তু মূলধারার এক চিকিৎসক সেটা দিতে পারেন না।"
তথাকথিত এসব নিরাময় পদ্ধতিকে ব্যথাহীন বা প্রাকৃতিক- এরকম তকমা দেওয়া হয়, তবে আসলে এগুলো ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের অবস্থা আরও খারাপ করতে পারে এবং মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টকে বিঘ্নিত বা মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে।
আরেকটি কারণ হলো, ভালো মানের ক্যান্সার চিকিৎসা বিশ্বের অনেকের কাছেই সহজলভ্য নয় এবং এটি বেশ ব্যয়বহুল।
ডক্টর লিজ ও'রিয়োর্ডান বলছেন, "টাকা যেখানে একটি ইস্যু সেখানে তুলনামূলক সস্তা পদ্ধতিগুলো খুবই আকর্ষণীয় মনে হতে পারে। আমার দুশ্চিন্তা হলো, ঝুঁকিপূর্ণ লোকগুলোকে মানুষ লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছে এবং প্রয়োজন নেই এরকম অনেক পণ্যও তাদের কাছে বিক্রি করছে।"
ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়, আফ্রিকা অঞ্চলে ক্যান্সার ও এর চিকিৎসা নিয়ে সচেতনতার অভাব অনেক বেশি। এছাড়া প্রশিক্ষিত চিকিৎসা সেবাদানকারীর সংকটও রয়েছে। মানুষের চিকিৎসা বিমার হারও কম। ফলে বিকল্প বিভিন্ন পদ্ধতির ওপর মানুষের নির্ভরতা অনেক বেশি।
এরকম চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর নির্ভরতা অনেক ক্ষেত্রে সংস্কৃতির সঙ্গেও জড়িত।
আফ্রিকা, এশিয়া ও ভারতে চিকিৎসার অনেক প্রাচীন পদ্ধতির চল রয়েছে এবং দার্শনিক ব্যাখ্যার কারণে এগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতাও বেড়েছে। চীনের প্রচলিত কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি ও আয়ুর্বেদ কোনো কোনো রোগের উপশমে কাজ করে বলে প্রমাণ যদিও রয়েছে, তবে ক্যান্সারের চিকিৎসায় এগুলোর সহায়ক ভূমিকার প্রমাণ অপ্রতুল।
বিশ্বে বহুল প্রচলিত বিকল্প থেরাপি ও ডায়েট কোনগুলো?
আয়ুর্বেদিক 'চিকিৎসা'
আয়ুর্বেদ হলো প্রাচীন ভারতীয় এক চিকিৎসা পদ্ধতি। বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক উপদানের ব্যবহার করে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থান টিপে মূলত এই চিকিৎসা দেওয়া হয়। বিশ্বব্যাপী দিনে দিনে এর জনপ্রিয়তা বাড়ছে। ২০২৮ সাল নাগাদ এর বাজার এখনকার তিনগুণ হয়ে যেতে পারে বলে মার্কেট রিসার্চ ফিউচারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
আয়ূর্বেদে ভারতীয় উপমহাদেশে বহুল উৎপাদিত মশলা হলুদকে এমন এক পণ্য বিশ্বাস করা হয়, যার ক্যান্সার নিরাময়ের গুণ আছে।
স্বাস্থ্য বিষয়ক জার্নাল ল্যানসেটের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হোমিওপ্যাথি, বায়োপ্যাথি, নিউরোপ্যাথি বা হার্বাল পদ্ধতি, ঘরোয়া প্রতিকার, গমের চারা দিয়ে বা পানি দিয়ে চিকিৎসা, আকুপাংচারের মতো নানা পদ্ধতির ওপর নির্ভরতা রয়েছে ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকাগুলোয়।
এর কোনো কোনোটায় ব্যথা-বেদনা হয়তো লাঘব হয়, কিন্তু ক্যান্সার চিকিৎসায় এসবের ভূমিকা নেই বলে মনে করেন ডক্টর ও'রিয়োর্ডান।
ক্যান্সার সংক্রান্ত চ্যারিটি ক্যান্সার রিসার্চ ইউকে বলছে, হলুদের একটি উপাদান যার নাম কারকিউমিন, এটি ক্যান্সার সেল মেরে ফেলতে পারে, তবে এটি ঘটতে পারে নির্দিষ্ট কয়েক ধরনের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে।
তবে এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন। হলুদ বা কারকিউমিন ক্যান্সার প্রতিরোধ বা নিরাময় করতে পারে এর কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই।
চীনে প্রচলিত চিকিৎসাবিদ্যা
ক্লিনিক্যাল অঙ্কোলজি জার্নালে একটি গবেষণার রিভিউ আর্টিক্যালে বলা হয়েছে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক জায়গায় ক্যান্সার চিকিৎসায় চীনের প্রথাগত চিকিৎসা পদ্ধতি (ট্যাডিশনাল চায়নিজ মেডিসিন বা টিসিএম) বেছে নেওয়ার একটা চল বাড়তে দেখা যাচ্ছে।
কিন্তু এর নিরাপত্তা ও কার্যকারিতা নিয়ে ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের কমই প্রশ্ন করতে দেখা গেছে।
টিসিএম হলো এমন এক বিষয় যেখানে আকুপাংচার, মেসেজ থেরাপি, হার্বাল থেরাপি এবং তাই চি (এক ধরনের মার্শাল আর্ট) এর সবগুলোই ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের লতাপাতা থেকেও শত শত রকেমর নির্জাস নেওয়া হয়।
ডক্টর লিজ ও'রিয়োর্ডান বলছেন, চিকিৎসকের পরামর্শে মেডিক্যার ট্রিটমেন্টের সহায়ক হিসেব টিসিএম ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে কোনো কোনো হার্বাল উপাদান মূল চিকিৎসাকে বিঘ্নিত করতে পারে এমন ঝুঁকি রয়েছে।
ডায়েট পরিবর্তন
কিটো (খাদ্য তালিকায় শর্করা কমিয়ে আমিষ বাড়িয়ে দেওয়ার পদ্ধতি), ভেগান (ভেজিটেরিয়ান বা শাকসবজিনির্ভর খাদ্যতালিকা) বা উপবাস কেন্দ্রিক বিভিন্ন খাদ্যাভ্যাস বিশ্বে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। ক্যান্সারকে 'অনাহারে' রাখতে ডায়েট নিয়ন্ত্রণের কথাও বলা হচ্ছে।
ক্যান্সার গবেষক ডক্টর ডেভিড রবার্ট গ্রিমস বিবিসিকে বলছেন, "আপনি ক্যান্সারকে অনাহারে রাখতে পারবে না, বরং কেবল নিজের শরীরকে না খাইয়ে রাখতে পারবেন। এই প্রক্রিয়ায় আপনি যদি ওজন হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েন তখন ক্যান্সারের প্রভাব আরও মারাত্মক হতে পারে।"
ঝুঁকি বা ক্ষতির কথা চিন্তা না করেই অনেক রোগী এরকম বিভিন্ন খাদ্যাভ্যাসে ঝুঁকে পড়ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
ভারতের পাঞ্জাবের মোহনদাই অসওয়াল হসপিটালের ক্যান্সার চিকিৎসক ডক্টর কানুপ্রিয়া ভাটিয়া ক্যান্সার রোগীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এধরনের প্রচারণায় প্রভাবিত না হতে।
তিনি বলেন, "নিজ উদ্যোগে (ক্যান্সার থেকে মুক্তি পেতে) কোনো কিছু খেতে বা পান করতে শুরু করবেন না যেটা পরে ক্ষতির কারণ হতে পারে।"
ফেনবেনডাজোল
বিভিন্ন প্রাণীর শরীরে পরজীবীর সংক্রমণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় এই ফেনবেনডাজোল ওষুধটি। অন্যান্যা বিকল্প থেরাপির সঙ্গে এই ওষুধটি সেবন করে ক্যান্সারমুক্ত হয়েছে, এক মার্কিন ব্যবসায়ী এই দাবি করার পর ক্যান্সার চিকিৎসায় এর জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে যায়।
তবে প্রথমে তিনি বলেননি যে তিনি ক্যান্সার চিকিৎসার অন্যান্য ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালেও অংশ নিচ্ছিলেন।
দক্ষিণ কোরিয়া এই ওষুধটি এত পরিমাণেই বিক্রি হয় যে মজুত ফুরিয়ে যায়। সেবনকারীদের অনেকে সোশাল মিডিয়ায় নিজেদের অভিজ্ঞতার জানাতে শুরু করেন, যদিও পরে এক কৌতুকাভিনেতা ও গায়ক দাবি করেন ওষুধটি তার ওপর কার্যকরী ছিলো না, যে কারণে তিনি এটি খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।
ক্যান্সার রিসার্চ ইউকে জানিয়েছে, এই ওষুধের কোনো ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল হয়নি এবং এর নিরাপত্তার দিকটও প্রমাণিত নয়।
গ্রাভিওলা
গ্রাভিওলা গাছের ফল, পাতা ও ছাল অনেককাল ধরে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে নানা রোগের প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কোনো কোনো সংক্রমণের ক্ষেত্রে এর কার্যকারিত প্রমাণিতও হয়েছে।
স্থানীয়ভাবে এবং ইন্টারনেটে এমন তথ্যও ছড়িয়ে পড়ে যে ক্যান্সার আরোগ্যে গ্রাভিওলার ফলের ভূমিকা আছে। এমনকি সোশাল মিডিয়ার কিছু পোস্টে দাবি করা হয়, কেমোথেরাপির চেয়েও এই ফল দশ হাজার গুণ বেশি কার্যকর।
বিভিন্ন ক্যান্সার চ্যারিটি ও ফ্রেঞ্চ ক্যান্সার ইনস্টিটিউট বলছে, ক্যান্সার দূর করার কোনো 'মিরাকল ফুড' বা 'অলৌকিক খাবার' নেই।
চিকিৎসক ও ক্যান্সার দাতব্য সংস্থাগুলো কী বলছে?
এ ধরনের বিভিন্ন বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতিতে মারাত্মক বিপদ লুকিয়ে আছে বলে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন। এসব পদ্ধতি ব্যবহারে মূল চিকিৎসা বিঘ্নিত হওয়ার বা রোগীর বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে আসার বিষয়টি গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে।
ডক্টর রিয়োর্ডান বলেন, "মেডিক্যাল ট্রিটমেন্টের পাশাপাশি এ ধরনের পদ্ধতি কোনোটির প্রয়োগ ঠিক হতে পারে। সমস্যাটা হয় তখনই যখন শুধু এসব পদ্ধতিই অবলম্বন করা হয়। এক্ষেত্রে রোগীর মৃত্যুর ঝুঁকি দুই বা আড়াই গুণ বেড়ে যায়।"
ডক্টর গ্রিমস বলেন, শক্তিশালী গবেষণা ওপর ভিত্তি করে ক্যান্সার চিকিৎসা চলে।
"বিকল্প পদ্ধতিগুলোর কারণে নয়, বরং বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকদের কঠোর পরিশ্রমের কারণেই বিশ্বজুড়ে ক্যান্সার থেকে মানুষ সুস্থ হয়ে উঠছেন এবং তাদের বেঁচে যাওয়ার হার বাড়ছে", যোগ করেন তিনি।
ভারতের ম্যাক্স ইনস্টিটিউট অব ক্যান্সার কেয়ারের চেয়ারম্যান ডক্টর হারিত চতুর্বেদি বলেন, "ক্যান্সার এমন কোনো রোগ নয় যেটা কোনো জাদুকরি ফর্মুলায় দূর হয়ে যাবে।"
বরং আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রতিটি রোগীর জন্য তাদের ক্যান্সারের ধরন, জিনগত বিশেষ পরিবর্তন, যে অঙ্গ থেকে ক্যান্সার ছড়িয়েছে সেটাসহ নানা বিষয় অনুসন্ধান করে বিশেষ চিকিৎসা পরিকল্পনা দেওয়া হয়।
অসুস্থতায় একটু আরাম পাওয়া যাবে এরকম কোনো সহায়ক পদ্ধতি রোগীরা নিতে চাইলে চিকিৎৎসকরা সাধারণত তাদের সমর্থন দেন। কিন্তু তারা কখনই শুধু এসব পদ্ধতির ওপর নির্ভর করার কথা বলেন না।
শীতে ব্রণ বেড়ে গেলে কী করবেন
শীতকালে ত্বকে দেখা দেয় নানা ধরনের সমস্যা। বিশেষ করে শীতে ত্বক থেকে প্রাকৃতিক তেল কম নিঃসৃত হওয়ায় ব্রণ বেড়ে যায়। তাই ব্রণ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে শীতে বিশেষ যত্ন নেওয়া জরুরি।
শীতকালে ব্রণ কমানোর জন্য কিছু কার্যকরী টিপস জানিয়েছেন বিউটিএক্সাপার্ট পন্নি খান। চলুন জেনে নেওয়া যাক সে সম্পর্কে।
১. ত্বক পরিষ্কার রাখতে হবে-
শীতকালে ত্বক পরিষ্কার রাখতে হালকা, পিএইচ-ব্যালেন্সড ক্লিনজার ব্যবহার করা ভালো। এতে ত্বক অতিরিক্ত শুষ্ক হয় না এবং ব্রণ বাড়ার সম্ভাবনাও কমে।
২. ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার-
শীতে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার না করলে ত্বক অতিরিক্ত তেল উৎপন্ন করে, যা ব্রণের সৃষ্টি করতে পারে। একটি হালকা, অয়েল-ফ্রি ময়েশ্চারাইজার বেছে নিন যাতে ত্বক আর্দ্র থাকে এবং ব্রণ নিয়ন্ত্রণে থাকে।
৩. তেলযুক্ত প্রসাধনী থেকে দূরে থাকতে হবে-
শীতে ত্বকে অতিরিক্ত তেলযুক্ত পণ্য ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ অতিরিক্ত তেল ত্বকের পোর বন্ধ করে দেয় এবং ব্রণ সৃষ্টি করে। তেলের বদলে জলভিত্তিক বা অয়েল-ফ্রি প্রোডাক্ট ব্যবহার করুন।
৪. আর্দ্রতা বজায় রাখুন-
শীতকালে ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়ার কারণে ব্রণ বেড়ে যায়। এজন্য ঘরের আর্দ্রতা বজায় রাখা জরুরি। একটি হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করলে শুষ্কতা কমবে এবং ত্বক আর্দ্র থাকবে।
৫. সঠিক খাদ্যাভ্যাস এবং পানি পান
শীতে অনেকেই পানি কম পান করেন, কিন্তু শরীর ও ত্বকের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে পর্যাপ্ত পানি পান করা জরুরি। এছাড়া, পুষ্টিকর খাবার যেমন তাজা ফল, শাকসবজি এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য ত্বক সুস্থ রাখে এবং ব্রণ কমায়।
৬. ডাক্তারি পরামর্শ নিন-
ব্রণ যদি বেশি হয়ে থাকে এবং বাড়তে থাকে, তাহলে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। চিকিৎসক প্রয়োজনে সঠিক ক্রিম বা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট সাজেস্ট করতে পারেন যা শীতকালে ব্রণ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে।
মোজা পরে ঘুমানো স্বাস্থের জন্য ভালো
এবার বেশ খানিকটা আগেভাগেই চলে এসেছে শীত, ভালোই জেঁকে বসেছে। ভারি কাপড় পরে বাইরে বের হতে হচ্ছে। সেইসঙ্গে অনেকেই উষ্ণ থাকতে বাসার ভেতরে মোজা পরছেন, রাতে ঘুমাচ্ছেনও মোজা পরে। তবে অনেকেই জানেন না, মোজা পরে শোয়ার অভ্যাস স্বাস্থ্যকর নাকি ক্ষতিকর।
চিকিৎসকরা বলছেন, মানুষের হাত ও পা অতিমাত্রায় ঠান্ডা হয়ে যাওয়াকে রায়নাউড সিনড্রোম বলা হয়, যার ফলে পায়ে ভালোভাবে রক্ত পৌঁছাতে পারে না। এতে করে হাত ও পায়ে অসাড়তা তৈরি হয়। শীতের রাতে পায়ে মোজা পরলে এই সিনড্রোমের উপসর্গ কমে।
মোজা পরে ঘুমালে পা উষ্ণ থাকে, ফলে রক্ত সঞ্চালন ভালোভাবে হয়। এর ফলে শরীরে রক্ত প্রবাহ এবং অক্সিজেন প্রয়োজন মতো নির্দিষ্ট থাকে এবং হার্ট, ফুসফুস এবং পেশী তাদের সর্বোত্তম ক্ষমতাকে কাজ লাগাতে পারে।
নারীদের মেনোপজের সময় রাতে হট ফ্ল্যাশ দেখা দিলে অর্থাৎ আকস্মিকভাবে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি, শরীর গরম এবং ঘাম অনুভব হয়। মোজা পরলে পায়ের অংশ উষ্ণ থাকে যা শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আমাদের শরীরের সবচেয়ে সংবেদনশীল অঙ্গগুলোর মধ্যে পা একটি। যখন পা ঠান্ডা থাকে তখন স্বাভাবিকভাবেই ঘুমাতে অসুবিধা হতে পারে। দক্ষিণ কোরিয়ায় ছয়জন পুরুষ নিয়ে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, মোজা পরিহিত পুরুষরা ৩২ মিনিট বেশি এবং মোজা ছাড়া ব্যক্তিদের তুলনায় সাড়ে ৭ মিনিট পূর্বেই দ্রুত ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মোজা পরে ঘুমালে পা উষ্ণতা পায়, যা দ্রুত ঘুমিয়ে পড়তে এবং দীর্ঘক্ষণ ঘুমাতে সাহায্য করে।
তবে মোজা পরে ঘুমানোর কিছু ক্ষতিকর দিকও রয়েছে। মোজা পরে ঘুমালে শরীরের রক্ত সঞ্চালন ভালভাবে যেমন হয়, তেমনি মোজা বেশি টাইট হলে রক্ত চলাচল কমে যেতে পারে। মোজা যদি বাতাস চলাচলের উপযোগী না হয় তবে তাপকে শরীর থেকে বের হতে বাধা দেবে এবং শরীর অতিরিক্ত গরম হয়ে যেতে পারে। এছাড়াও মোজা যদি পরিষ্কার না হয় তবে পায়ে বিভিন্ন সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়।
শিশুরাও মোজা পরে ঘুমাতে পারে। তবে নরম, প্রাকৃতিক, বাতাস চলাচল করতে পারার মতো উপাদান যেমন তুলার ঢিলেঢালা মোজা দিতে হবে। টাইট ইলাস্টিক টপসসহ মোজা এড়িয়ে চলাই শ্রেয়, যেহেতু এটি শিশুর শরীরের রক্ত প্রবাহকে সীমাবদ্ধ করতে পারে।
যদি শরীরে রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা, পা ফুলে যাওয়া অথবা পায়ে রক্ত প্রবাহ সীমিত করে দেওয়ার মতো শারীরিক সমস্যা থাকে তবে মোজা পরে ঘুমানোর বিষয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে নিন।
মুড়ি খেলে ওজন কমবে
জলখাবার হিসেবে মুড়ি খেতে সবাই পছন্দ করেন। বিশেষ করে ডায়াবেটিসের রোগীদের কাছে মুড়ি খুব জনপ্রিয়। সকাল-বিকালের নাশতায় সেহজ উপায় হিসেবে তারা মুড়িকেই বেছে নেন। তবে মুখরোচক খাবারের পাশাপাশি মুড়িতে কতটা পুষ্টিগুণ রয়েছে, সে সম্পর্কে জানেন না অনেকেই।
মুড়ি সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়েছেন জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডা. শিমু আক্তার। চলুন জেনে নেই-
ওজন কমাতে: যারা ওজনের ব্যাপারে সচেতন, তাদের জন্য মুড়ি একটি ভালো খাবার হতে পারে। কারণ, মুড়ি কম ক্যালরি এবং কম চর্বিযুক্ত খাবার। ১৫ গ্রাম মুড়িতে মাত্র ৫৪ ক্যালরি আছে। শুধু তা–ই নয়, প্রচুর ফাইবার থাকার কারণে মুড়ি খেলে অনেক সময় পর্যন্ত পেট ভরা থাকে। মুড়িতে ভিটামিন বি, ম্যাগনেশিয়াম ও জিংক আছে।
গ্যাসের সমস্যায়: বিভিন্ন খাবার খাওয়ার কারণে অনেক সময় বুক জ্বালাপোড়াসহ গ্যাসের সমস্যা হয়। মুড়ি সেসব ক্ষেত্রে ভালো সমাধান হতে পারে। বিশেষ করে মুড়ি পানিতে ভিজিয়ে খেলে গ্যাসের সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়।
কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে: মুড়িতে প্রচুর ফাইবার আছে। সুতরাং যারা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছেন, তাদের জন্য মুড়ি খুব উপকারী।
হাড় শক্ত করে: মুড়িতে প্রচুর ক্যালসিয়াম, আয়রন ও অল্প পরিমাণ ‘ভিটামিন ডি’ বিদ্যমান, যা হাড় শক্ত করতে খুবই প্রয়োজনীয়।
ত্বকের যত্নে: বয়সের ছাপ নিয়ে কমবেশি সবাই চিন্তিত হয়। এ ক্ষেত্রে একটি উত্তম সমাধান হতে পারে মুড়ি। কারণ, মুড়িতে রয়েছে অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট, যার প্রভাবে আল্ট্রাভায়োলেটের কারণে ত্বকের যে ক্ষতি হয়, তা সহজেই রোধ করা যায়।
যাদের সতর্ক হতে হবে
ডায়াবেটিসের রোগী: অনেক ডায়াবেটিসের রোগীর কাছে নাশতা হিসেবে মুড়ি খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু অনেকেই জানেন না মুড়িতে বেশ শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট আছে। মুড়ির গ্লাইসেমিক ইনডেক্স বেশি ও মুড়ি রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বৃদ্ধি করতে পারে। তবে প্রচুর ফাইবার থাকায় এবং ক্যালরি কম থাকায় মুড়ি নাশতা হিসেবে অল্প পরিমাণে খাওয়া যেতে পারে। ব্রাউন মুড়ি বা লাল চালের মুড়ি অপেক্ষাকৃত ভালো।
কিডনিজনিত সমস্যা: ডায়াবেটিসের রোগীদের মতো যারা দীর্ঘদিন কিডনিজনিত রোগে আক্রান্ত, তারাও মুড়ি খাওয়া থেকে বিরত থাকবেন। কারণ, মুড়িতে প্রচুর পরিমাণ সোডিয়াম আছে, যা কিডনি রোগে আক্রান্ত রোগীর জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে।
উচ্চ রক্তচাপের রোগী: মুড়িতে প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম থাকায় রক্তচাপ বৃদ্ধি করে। এ কারণে যাদের উচ্চ রক্তচাপ আছে ও যারা হার্টের সমস্যায় ভুগছেন, তারা মুড়ি খাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবেন।
বাজারের মুড়িতে বিভিন্ন ক্ষতিকারক রাসায়নিক উপাদান, যেমন আর্সেনিক, ইউরিয়া মেশানো থাকে, যা নানান স্বাস্থ্য সমস্যাসহ রোগীর মৃত্যুর কারণও হতে পারে।
যে পানীয়গুলি আমাদের বয়স দ্রুত বাড়িয়ে দেয়
কে না চায় তারুণ্যের চেহারা আরও দীর্ঘ সময় ধরে উপভোগ করতে। তবে বার্ধক্য যেমন অবশ্যম্ভাবী, তেমনি আমাদের জেনেটিক্স, পরিবেশ, লাইফস্টাইল এবং ডায়েট এই প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষত ডায়েটের ক্ষেত্রে, প্রতিদিন যা খাই এবং পান করি, তা আমাদের চেহারায় প্রভাব ফেলতে পারে। চলুন জানি, কোন ৩টি পানীয় আপনার বয়স দ্রুত বাড়িয়ে দিতে পারে।
১. এনার্জি ড্রিংকস
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে এনার্জি ড্রিংকস ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে, বিশেষ করে শারীরিক ব্যায়ামের সময় শক্তি বাড়ানোর জন্য। যদিও এটি আপনার শরীরে তাত্ক্ষণিক শক্তি যোগাতে পারে, তবে আপনি কি জানেন এই পানীয়টি আপনার বার্ধক্য ত্বরান্বিত করতে পারে? হ্যাঁ, আপনি ঠিক পড়ছেন।
বিশেষজ্ঞদের মতে, এনার্জি ড্রিংকসে প্রচুর ক্যাফেইন থাকে, যা ত্বকের পানিশূন্যতা সৃষ্টি করে এবং ত্বককে নিস্তেজ করে তোলে। এছাড়াও, এনার্জি ড্রিংকসে অতিরিক্ত চিনি থাকে, যা শরীরে অক্সিডেটিভ স্ট্রেস বাড়াতে পারে। এই অবস্থায়, আপনার ত্বকে দ্রুত বয়সের ছাপ পড়বে। তাই, এনার্জি ড্রিংকসের বদলে আপনি ডিক্যাফ কফি বা চিনিমুক্ত চা খেতে পারেন।
২. অ্যালকোহল
যদি আপনি বার্ধক্য দূরে রাখতে চান, তবে অ্যালকোহল এড়িয়ে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টিবিদদের মতে, অ্যালকোহল প্রদাহজনক কোষের সংখ্যা বাড়িয়ে ত্বকের অবনতি ঘটাতে পারে। এছাড়া অ্যালকোহল শরীরকে ডিহাইড্রেট করে, যার ফলে ত্বক শুষ্ক এবং নিস্তেজ হয়ে পড়ে।
নর্থওয়েস্টার্ন মেডিসিনে প্রকাশিত একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, যদি পাঁচ বছর ধরে প্রতিদিন মদ পান করা হয়, তবে মাত্র চার মাসের মধ্যে এটি জৈবিক বার্ধক্য ত্বরান্বিত করে।
৩. কোমল পানীয়
অনেকের জন্য রেস্তোরাঁ বা গেট-টুগেদারে কোমল পানীয় একটি প্রিয় পানীয়, যা প্রথম চুমুকেই তৃপ্তি প্রদান করে। তবে, এটি মনে রাখতে হবে যে এই কোমল পানীয়তে প্রচুর চিনি থাকে। আমরা সবাই জানি, অতিরিক্ত চিনি আমাদের জন্য ক্ষতিকর। এই কোমল পানীয় পান করার ফলে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা এবং কোলাজেন উৎপাদন কমে যায়, যা আপনার বয়সকে দ্রুত বাড়িয়ে দিতে পারে। তাই যদি আপনি ত্বককে তরুণ রাখতে চান, এখনই কোমল পানীয় খাওয়া কমিয়ে দিন বা পরিহার করুন।
সেরা অ্যান্টি-এজিং খাবার কোনগুলো?
প্রচুর অ্যান্টি-এজিং খাবার রয়েছে, যা আপনার স্বপ্নের ত্বক অর্জনে সহায়তা করতে পারে এবং তারুণ্যের চেহারা দীর্ঘ সময় ধরে ধরে রাখতে সাহায্য করে। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এই ধরনের খাবার অন্তর্ভুক্ত করলে আপনার ত্বকের প্রয়োজনীয় পুষ্টি পাওয়া সহজ হবে, যা ত্বককে স্বাস্থ্যকর, উজ্জ্বল এবং তারুণ্যময় রাখতে সাহায্য করে।
সবুজ শাক-সবজি যেমন পালং শাক, ক্যাল শাক এবং ব্রকলিতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন সি, যা কোলাজেন উৎপাদন বাড়ায়, ত্বকের ভাঁজ কমায় এবং ফ্রি র্যাডিকাল থেকে ত্বককে রক্ষা করে। বাদাম, বিশেষত কাঠবাদাম এবং আখরোটে থাকা স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, ভিটামিন ই এবং সেলেনিয়াম ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা ধরে রাখতে এবং সূর্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে।
সবুজ চা (গ্রিন টি) অ্যান্টি-এজিং খাদ্যতালিকায় একটি শক্তিশালী উপাদান। এতে পলিফেনলস এবং ক্যাটেচিন রয়েছে, যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস কমাতে, প্রদাহ হ্রাস করতে এবং ত্বকের কোষ পুনর্গঠনে সাহায্য করে। কিউইয়ের মতো ফলগুলো অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং ভিটামিন সি-তে ভরপুর, যা ত্বকের গঠন উন্নত করতে এবং প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আনতে সাহায্য করে।
জিরা এবং হলুদের মতো মসলাগুলো বহু বছর ধরে ঐতিহ্যবাহী সৌন্দর্য রুটিনের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জিরা শরীরকে ডিটক্সিফাই করতে এবং অকাল বার্ধক্য রোধ করতে সহায়ক, আর হলুদে থাকা কারকিউমিন প্রদাহ কমায়, ত্বকের রং সমান করে এবং ত্বককে উজ্জ্বল করতে সহায়তা করে।
এই সুপারফুডগুলো খাদ্যতালিকায় যোগ করলে আপনার ত্বক ভেতর থেকে পুষ্টি পাবে, বার্ধক্যের লক্ষণ কমাতে সাহায্য করবে এবং প্রাকৃতিকভাবে উজ্জ্বল ও তারুণ্যময় ত্বক পেতে সহায়ক হবে। তবে, মনে রাখবেন, সুষম খাদ্য, পর্যাপ্ত পানি পান, নিয়মিত ব্যায়াম এবং সঠিক ত্বকের যত্নই দীর্ঘমেয়াদে ত্বকের স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য ধরে রাখার মূল চাবিকাঠি।
শিল্পকলা ও সংস্কৃতি উপভোগ স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য ভালো
শিল্পকলার সাথে জড়িত থাকা জীবনমান উন্নত করে, উৎপাদনশীলতা বাড়ায় এবং আর্থিক ‘লভ্যাংশ’ তৈরি করে। স্মরণীয় নাটক, চলচ্চিত্র, কনসার্ট বা শিল্প প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের যে আলোড়ন অনুভূত হয়, তা অনেকের কাছেই পরিচিত। এবার তা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে, সংস্কৃতি উপভোগ করা আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো এবং এটি মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বছরে ৮ বিলিয়ন পাউন্ডের আর্থিক সুফল সৃষ্টি করে।
শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রভাব এবং এর আর্থিক সুবিধাগুলো পরিমাপ করার জন্য প্রথমবারের মতো যুক্তরাজ্যে পরিচালিত একটি বড় গবেষণায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে।
গবেষণাটি পরিচালনা করেছে ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডনের ডিপার্টমেন্ট ফর কালচার, মিডিয়া অ্যান্ড স্পোর্ট (ডিসিএমএস)। এতে সহযোগী হিসেবে ছিল ফ্রন্টিয়ার এবং ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (ডব্লিওএইচও)।
ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকার কমিশনকৃত এই পর্যালোচনায় দেখা গেছে, মাঝে মাঝে, এমনকি কয়েক মাসে একবার হলেও শিল্পের কোনো ইভেন্টে অংশগ্রহণ বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়া বিভিন্ন ধরনের তাৎপর্যপূর্ণ সুবিধা দেয়। এতে ব্যাথা, দুর্বলতা, হতাশা কমানো এবং ওষুধের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাওয়ার মতো প্রভাব থাকতে পারে।
গবেষণার সহ-লেখক এবং ফ্রন্টিয়ার ইকোনমিক্সের ম্যাথিউ বেল বলেন, নাটক, মিউজিক্যাল এবং ব্যালে’র মতো পরিবেশনা-ভিত্তিক শিল্পে সম্পৃক্ত হওয়া, বিশেষত সংগীতে অংশগ্রহণ হতাশা এবং ব্যাথা হ্রাস এবং জীবনের মান উন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত।
গবেষণার সহ-লেখক এবং ডব্লিওএইচও কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ডেইজি ফ্যানকোর্ট বলেছেন, শিল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ততা স্বাস্থ্যগত ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় এবং বাস্তব প্রভাব সৃষ্টি করে, যেমন- জ্ঞানীয় বিকাশে সহায়তা করা এবং জ্ঞানীয় হ্রাস থেকে সুরক্ষা প্রদান, মানসিক অসুস্থতার উপসর্গ কমানো এবং সুস্থতা বৃদ্ধি, ব্যথা ও চাপ হ্রাস করা এবং ওষুধের মাধ্যমে সক্রিয় হওয়া স্নায়ুবিজ্ঞানের ও শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একই রকম সুবিধা প্রদান।
সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সমাজে যে সুবিধা নিয়ে আসে, তার মধ্যে ফ্রন্টিয়ার ৮ বিলিয়ন পাউন্ডের যে হিসাব করেছে, তার বেশিরভাগ (£৭ বিলিয়ন) আসে মানুষের জীবনের মান উন্নয়ন থেকে এবং বাকিটা কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি থেকে।
দিনে গরম, রাতে ঠান্ডা: শিশুর যত্ন
শীতের শুরুতে দিনের বেলা তাপমাত্রা বেশ গরম হলেও শেষ রাতে ঠান্ডা অনুভূত হয়। এ সময় শিশুরা বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। রাতে শিশুদের ঠান্ডা থেকে রক্ষা না করতে পারলে নানা ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিতে পারে। শিশুর বয়সভেদে কিছু বিশেষ যত্নের পরামর্শ জেনে রাখা ভালো।
১ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর যত্ন
উষ্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করুন: শিশুকে প্রয়োজন অনুযায়ী উষ্ণ রাখুন। ঠান্ডা বা স্যাঁতসেঁতে ঘরে রাখবেন না।
খাবারে উষ্ণতার দিকে খেয়াল রাখুন: শিশুকে বুকের দুধ নিয়মিত খাওয়ান। ফিডারে খাওয়ালে দুধ একটু গরম দিন। ঘুমের মধ্যে ঠান্ডা দুধ দেবেন না।
শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ান: ছয় মাসের বেশি বয়সী শিশুদের খিচুড়িতে ডিমের সাদা অংশ, লালশাক, কমলার রস, ইত্যাদি খেতে দিন। এতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
হামাগুড়ির জন্য নরম পরিবেশ: যেসব শিশু হামাগুড়ি দেয়, তারা যেন ঠান্ডা মেঝেতে না হামাগুড়ি দেয়। কার্পেট ব্যবহার না করে মাদুর বা ম্যাট ব্যবহার করা ভালো।
গোসল ও ত্বকের যত্ন: ঈষদুষ্ণ পানি দিয়ে এক দিন অন্তর গোসল করান। গোসলের পর বেবি লোশন লাগান, তেলজাতীয় কিছু না লাগানোই ভালো। নবজাতককে নিয়মিত গোসল না করালে ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে।
পোশাক ও মোজা: খুব গরম কাপড় পরানোর দরকার নেই, তবে মোটা সুতি কাপড় ও নরম কাপড়ের জুতা পরানোর অভ্যাস করান। রাতে শোয়ানোর সময় মোজা পরিয়ে দিন।
১ থেকে ৬ বছর বয়সী শিশুর যত্ন
খেলাধুলা ও স্কুলের সময় যত্ন: এ বয়সে শিশুরা খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকে, তাই খুব ভারী বা গরম কাপড় পরানো প্রয়োজন নেই। তবে সকালে স্কুলে বা বিকেলে খেলতে যাওয়ার সময় উষ্ণতা নিশ্চিত করুন।
ত্বকের যত্ন: শীতকালে কিছু ছোঁয়াচে চর্মরোগের ঝুঁকি থাকে। ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়া এড়াতে নিয়মিত লোশন ব্যবহার করুন।
গোসলের রুটিন: সরিষার তেলের বদলে জলপাই তেল ব্যবহার করাই ভালো। গোসলের পর বেবি লোশন লাগানো যেতে পারে। সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন সাবান ও এক দিন শ্যাম্পু ব্যবহার করুন।
শীতকালীন পুষ্টিকর খাবার: শাকসবজি ও ফল, যেমন কমলা, বরই বেশি করে খেতে দিন, যা শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।
শিশুর লেপ, তোশক ও চাদরের যত্ন: রোদে তুলে কম্বল, লেপ ইত্যাদি ঝেড়ে ধুলাবালি মুক্ত রাখুন। এগুলোর ওপর কাপড়ের কভার ব্যবহার করলে পরিষ্কার রাখা সহজ হয়।
এই শীতের শুরুতে শিশুর যত্নে এই পরামর্শগুলো অনুসরণ করলে শিশুরা ঠান্ডা থেকে রক্ষা পাবে এবং সুস্থ থাকবে।
স্ট্রোকের লক্ষণ ও কারণ, প্রতিরোধে যা করবেন
স্ট্রোক সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিন বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের নিউরোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সৈয়দা শাবনাম মালিকের কাছ থেকে।
স্ট্রোক একটি গুরুতর স্বাস্থ্যগত সমস্যা। যত অসংক্রামক রোগে মানুষের মৃত্যু হয় তার মধ্যে স্ট্রোক দ্বিতীয় প্রধান কারণ। অনেকের ধারণা স্ট্রোক এবং হার্ট অ্যাটাক একই বিষয়। এখানে মনে রাখতে হবে যে হার্ট অ্যাটাক আর স্ট্রোক সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইটি রোগ। এই বিষয়ে সচেতনতা জরুরি।
স্ট্রোক সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিন বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজের নিউরোলজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডা. সৈয়দা শাবনাম মালিকের কাছ থেকে।
স্ট্রোক কী ও কেন হয়
ডা. শাবনাম মালিক বলেন, স্ট্রোক মস্তিষ্কের একটি রোগ। এটা সাধারণত হয় কোনো কারণে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ যদি বন্ধ হয়ে যায়। সেটা মস্তিষ্কের রক্তনালি ব্লক হয়ে হতে পারে অথবা মস্তিষ্কের রক্তনালি ছিঁড়ে গিয়ে মস্তিষ্কের কোনো একটি অংশে রক্ত সরবরাহ ব্যাহত হতে পারে। এক্ষেত্রে সেই স্থানের কোষগুলো মৃত হয়ে যায়। যার ফলে স্ট্রোকের লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগীর মধ্যে যে লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় সেগুলো সাধারণত ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে প্রকাশিত হয়।
স্ট্রোকে সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ জানিয়ে ডা. শাবনাম মালিক বলেন, মাইল্ড স্ট্রোক বা মাইনর স্ট্রোক এরকম একটি কথা প্রচলিত আছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এটাকে ট্রানজিয়েন্ট স্কিমিক অ্যাটাক বলে। এক্ষেত্রেও স্ট্রোকের যে লক্ষণগুলো আছে রোগীর ক্ষেত্রে একই লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর এই লক্ষণগুলো আবার ঠিক হয়ে গিয়ে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এখানেই স্ট্রোক আর ট্রানজিয়েন্ট স্কিমিক অ্যাটাকের পার্থক্য।
স্ট্রোকের লক্ষণ ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে থাকবে আর ট্রানজিয়েন্ট স্কিমিক অ্যাটাক হলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ভালো হয়ে যায়। ট্রানজিয়েন্ট স্কিমিক অ্যাটাক মস্তিষ্কের সতর্কতামূলক সংকেত অর্থাৎ এটা একজন রোগীকে সতর্কতা দেয় যে পরে তার বড় ধরনের স্ট্রোক হতে পারে।
স্ট্রোক দুই ধরনের হয়। যেমন-
স্কিমিক স্ট্রোক: মস্তিষ্কের রক্তনালি কোনো কারণে ব্লক হয়ে যেতে পারে। সেটার পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে।
হেমোরেজিক স্ট্রোক: মস্তিষ্কের রক্তনালি যখন ছিঁড়ে যায় তখন তাকে হেমোরেজিক স্ট্রোক বলে।
অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ, অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, অনিয়ন্ত্রিত কোলেস্টেরল, ধূমপান ও মদ্যপান, অতিরিক্ত ওজন, অলস জীবনযাপন এবং হার্টের রোগ থেকেও স্ট্রোক হতে পারে। জন্ময়িনন্ত্রণ বড়ি খাওয়া নারীদের স্ট্রোকের কারণ হতে পারে। কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় বাবা-মা বা পরিবারে স্ট্রোকের ইতিহাস আছে। তাদেরও স্ট্রোক হতে পারে। এ ছাড়া ৫০ থেকে ৫৫ বছর বয়স এবং তার বেশি বয়সীদের স্ট্রোকের প্রবণতা বেশি। নারীদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে স্ট্রোক বেশি হয়।
স্ট্রোকের লক্ষণ
ডা. শাবনাম মালিক বলেন, নিউরোলজিস্টরা স্ট্রোকের লক্ষণ ও পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে বোঝার জন্য একটি শব্দ ব্যবহার করেন, সেই শব্দটি হলো- FAST (Face, Arm, Speech, Time)।
মূলত মস্তিষ্কের কোন রক্তনালিতে ব্লক হয়েছে সেটার উপর ভিত্তি করেই স্ট্রোকের লক্ষণ প্রকাশ পায়। তবে FAST এর লক্ষণগুলোই স্ট্রোকের প্রধান লক্ষণ।
১. মুখের কোনো এক অংশ বাঁকা হয়ে যাওয়া
২. শরীরের কোনো একটি দিক অর্থাৎ বাম অথবা ডান পাশ অবশ হয়ে যাওয়া, দুর্বল হয়ে যাওয়া, অনুভূতিহীন হয়ে যাওয়া।
৩. কথা জড়িয়ে যাওয়া বা অস্পষ্টতা।
৪. স্ট্রোকের ক্ষেত্রে সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিতে হবে রোগীকে।
এ ছাড়া ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা, মাথা ঝিমঝিম করা, প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, চোখে ঝাপসা বা অন্ধকার দেখা, বমি হওয়ার লক্ষণও থাকতে পারে রোগীর মধ্যে।
স্ট্রোকে সময়ের গুরুত্ব ও চিকিৎসা
ডা. শাবনাম মালিক বলেন, স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দেওয়ার পর থেকে সাড়ে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা সময় রোগীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ের মধ্যে রোগীকে চিকিৎসকের কাছে নেওয়া সম্ভব হলে ঝুঁকি কমানো সম্ভব। সিটি স্ক্যানসহ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসক যদি দেখেন রক্তনালিতে ব্লক হয়ে স্ট্রোক হয়েছে তাহলে শিরা পথে ইনজেকশন দেওয়া হয়, যেটাকে আই ভি থ্রম্বোলাইসিস বলা হয়। এতে রক্তনালির ব্লক ছুটে গিয়ে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল সচল হয়ে গেলে রোগীর মৃত্যু ঝুঁকি কমে আসে এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত হলো সেটার পরিমাণও কমে আসে। রোগী তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যান।
লক্ষণ দেখা দেওয়ার সাড়ে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টার পরিবর্তে যদি ৬ থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসকের কাছে নেওয়া যায় তাহলে মেকানিক্যাল থ্রম্বেকটমি চিকিৎসা দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে ক্যাথেটার নামক বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে রোগীর মস্তিষ্কে রক্তনালিতে যেখানে ব্লক আছে সেখানের জমাট বাঁধা রক্ত বের করে আনা হয়। ফলে রক্ত চলাচল পুনরায় সচল হয়ে যায়।
যেসব রোগীরা এই সময়ের ভেতরে চিকিৎসকের কাছে যেতে পারেন না তাদের ক্ষেত্রে কিছুই করার থাকে না। ধীরে ধীরে রক্ত জমাট বাঁধার যে প্রবণতা সেটি কম করার জন্য অ্যাসপিরিন বা ইকোস্প্রিন নামক ওষুধ দেওয়া হয়।
স্কিমিক স্ট্রোকের ক্ষেত্রে আই ভি থ্রম্বোলাইসিস এবং মেকানিক্যাল থ্রম্বেকটমি চিকিৎসা দেওয়া হয়।
হেমোরেজিক স্ট্রোকের চিকিৎসায় রক্তনালি ছিঁড়ে গিয়ে রক্তপাতের পরিমাণ বেশি হলে প্রয়োজনে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে মাথা থেকে রক্ত বের করা হয়। তবে মস্তিষ্কের কোন অংশে রক্তনালি ছিঁড়েছে, জমা রক্তপাতের পরিমাণ এবং রোগীর জ্ঞানের পরিমাণ কেমন এসবের উপর ভিত্তি করেই সার্জারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
এ ছাড়া স্কিমিক ও হেমোরেজিক স্ট্রোকের চিকিৎসা পদ্ধতির পাশাপাশি রোগীর যে ঝুঁকিগুলো আছে যেমন- উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয় তা নিয়ন্ত্রণে। স্ট্রোক পুর্নবাসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত তাদের ফিজিওথেরাপি দিতে হবে।
স্ট্রোক প্রতিরোধ
স্ট্রোক প্রতিরোধে উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কোলেস্টরেল নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। জীবনাচারে পরিবর্তন আনতে হবে, অ্যালকোহল ও ধূমপান পরিহার করতে হবে। কেউ যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি খায় সেটি বন্ধ করতে হবে। ভাতের সঙ্গে অতিরিক্ত লবণ খাওয়া যাবে না। প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ মিনিট হাঁটতে হবে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এর পাশাপাশি যাদের একবার স্ট্রোক বা ট্রানজিয়েন্ট স্কিমিক অ্যাটাক হয়েছে তাদের পরবর্তী স্ট্রোকের ঝুঁকি অনেক বেশি। সেজন্য তাদের ইকোস্প্রিন জাতীয় ওষুধ আজীবন চালিয়ে যেতে হয়।
আদাজল নাকি মেথিজল—ভুঁড়ি কমাতে কোনটি বেশি কার্যকর
আদাজল ও মেথিজল, দুটিতেই আছে এমন কিছু যৌগ ও অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট উপাদান, যা পেটের চর্বি বা ভুঁড়ি কমায়। তবে এর মধ্যে কোনটি তুলনামূলকভাবে বেশি কার্যকর?
ভুঁড়ি কমাতে আদাজলের ভূমিকা
ভুঁড়ি কমাতে চাইলে সকাল সকাল আদাজল পান করা ভালো। আদাজল ক্ষুধা নিবারণ ও ক্যালরি পোড়াতে সাহায্য করে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভূমিকা রাখে। এর ডাইইউরেটিক বা মূত্রবর্ধক গুণও আছে। মূত্রবর্ধক হওয়ায় আদাজল পান করলে শরীর থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশিত হয়ে শরীরের ফোলাভাব কমে। নিয়মিত আদাজল খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা অটুট থাকে, ডায়াবেটিস থাকে নিয়ন্ত্রণে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও আদাজলের সুনাম আছে। কোষ্টকাঠিন্য এবং শরীরের ফোলাভাব কমাতে আদার ব্যবহার বহু পুরোনো। আদায় এমন কিছু অ্যান্টি–অক্সিডেন্ট উপাদান আছে, যেসব কোষ ধ্বংসকারী ফ্রি-র্যাডিকেলগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ঠান্ডা, কাশি, জ্বর থেকে বাড়তি মেদ কমাতে তাই আদা বেশ কার্যকর নিঃসন্দেহে।
ক্যালরি পোড়ায়
গবেষণা বলছে, নিয়মিত আদাজল খেলে ক্যালরির দহন ও তৃপ্তির অনুভূতি বাড়ে। ফলে ক্ষুধা দূর হয়। আদার থার্মোজেনিক গুণ চর্বি কমাতে সাহায্য করে।
কোলেস্টেরল কমায়
একাধিক গবেষণায় জানা গেছে, আদা শরীরের কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডসের মাত্রা কমাতে সক্ষম। এটি শরীরের জন্য উপকারী হাই-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন বাড়িয়ে তুলনামূলক ক্ষতিকর লো-ডেনসিটি লিপোপ্রোটিন কমায়।
সঠিক মাত্রায় পানি ধারণে সাহায্য করে
পানির পরিমাণ বেড়ে শরীর ফুলে যাওয়াকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় বলে এডিমা। আদাজল প্রাকৃতিক ডাইইউরেটিক বা মূত্রবর্ধক। ফলে নিয়মিত আদাজল খেলে শরীর থেকে এই অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশিত হয়। তবে শরীরে তো নির্দিষ্ট মাত্রায় পানি ও সোডিয়ামও থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রেও আদাজল ভারসাম্য রক্ষা করে। আর এতেই পেট হয়ে ওঠে মেদহীন।
পরিপাক ভালো করে
আদায় থাকে ‘জিঞ্জেরল’ নামের এক প্রাকৃতিক উপাদান। এটি খাবারকে পরিপাক নালিতে দ্রুতগতিতে চালিত করে। ফলে খাবার অন্ত্রে দীর্ঘক্ষণ জমে থাকে না। খালি পেটে আদাজল খেলে পরিপাক ক্রিয়া বাড়ে। ফুড সায়েন্স অ্যান্ড নিউট্রিশনে প্রকাশিত এক পর্যালোচনা থেকে জানা যায়, আদায় থাকা এনজাইমগুলো শরীর থেকে গ্যাস বের করে দিয়ে হজমের জটিলতা দূর করে।
ভুঁড়ি কমাতে মেথিজলের ভূমিকা
মসলা হিসেবে তো বটেই, মেথি ভেষজ উপাদান হিসেবেও প্রাচীন। সারা রাত মেথির বীজ পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে খেলে ওজন কমে। মেথিতে থাকে গ্যালাক্টোম্যানান, যা ক্ষুধা নিবারণ করে এবং বিপাক বাড়ায়। মেথি পরিপাকে সাহায্য করে ভুঁড়ি কমাতে ভূমিকা রাখে। বেশি আঁচে দ্রুত ভেজে রান্না করা খাবার, বড়া, মুরগি, শাক, পরোটার মতো খাবারে মেথি দিতে পারেন অনায়াসে।
পেটফাঁপা এবং বদহজম কমায়
মেথিজল দ্রবণীয় আঁশসমৃদ্ধ বলে বদহজম, পেটফাঁপা ও কোষ্টকাঠিন্য দূর হয়। সকালে খালি পেটে মেথিজল খেলে শরীর থেকে দূর হয় বিষাক্ত উপাদান।
বিপাক ত্বরান্বিত করে
সকালে খালি পেটে মেথিজল খেলে ওজন এবং ভুঁড়িও কমে। মেথিজল বিপাক ত্বরান্বিত করে। ক্ষুধা কমিয়ে ওজন কমাতে ভূমিকা রাখে।
কোলেস্টেরল কমায়
মেথিজলে থাকা দ্রবণীয় আঁশ অপকারী কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদ্রোগসহ অনেক প্রাণঘাতী রোগের ঝুঁকি কমায়।
ক্যানসার জয় করতে দরকার প্রাথমিক পর্যায়ে রোগটি ধরতে পারা
‘বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, বাংলাদেশে ২০২২ সালে প্রায় দেড় লাখ মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছে, যার মধ্যে এক লাখের মৃত্যু হয়। আর বিশ্বে প্রতিবছর ক্যানসারে প্রায় দুই কোটি মানুষ আক্রান্ত হয়, যার মধ্যে মৃতের সংখ্যা প্রায় এক কোটি। বর্তমানে প্রোস্টেট ক্যানসারের ব্যাপকতা বেড়েছে। বিশ্বে প্রতিবছর আটজনের মধ্যে একজন পুরুষের প্রোস্টেট ক্যানসার হয়।’ এমনই সমীক্ষা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন উপস্থাপক নাসিহা তাহসিন।
সেপ্টেম্বর মাস, প্রোস্টেট ক্যানসার সচেতনতার বিশেষ মাস। এ উপলক্ষে এসকেএফ অনকোলজি আয়োজিতে অনুষ্ঠিত হয় ‘বিশ্বমানের ক্যানসার চিকিৎসা এখন বাংলাদেশেই সম্ভব’ শীর্ষক অনলাইন আলোচনা। অনুষ্ঠানে ক্যানসারের বর্তমান পরিস্থিতি, প্রতিরোধে করণীয় ও দেশের চিকিৎসা–সুবিধা নিয়ে আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানটি গতকাল মঙ্গলবার (৩ সেপ্টেম্বর) সরাসরি প্রচারিত হয় প্রথম আলো, এসকেএফ অনকোলজি ও এসকেএফের ফেসবুক পেজে। এতে অতিথি হিসেবে ছিলেন বিআরবি হাসপাতাল লিমিটেডের মেডিকেল অনকোলজি বিভাগের চিফ কনসালটেন্ট অধ্যাপক ডা. মো. মোফাজ্জেল হোসেন।
উপস্থাপক প্রথমেই জানতে চান, বাংলাদেশে কোন ক্যানসারের হার সবচেয়ে বেশি? সেখানে প্রোস্টেট ক্যানসারের অবস্থান কততম?
ডা. মো. মোফাজ্জেল হোসেন বলেন, ‘বাংলাদেশে প্রতিবছর সবচেয়ে বেশি মানুষ আক্রান্ত হয় খাদ্যনালির ক্যানসারে। এরপর ক্রমানুসারে রয়েছে মুখগহ্বর ক্যানসার, স্তন ক্যানসার, ফুসফুসের ক্যানসার, সারভাইকেল ক্যানসার ও প্রোস্টেট ক্যানসার।’
প্রোস্টেট ও স্তন লিঙ্গভিত্তিক ক্যানসার। এমন রোগের ঝুঁকি সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘ডোন্ট বার্গেইন উইথ ইয়োর প্রোস্টেট—প্রোস্টেটের সঙ্গে কোনো দরাদরি নেই। ফুসফুস বা লাং ক্যানসারের তুলনায়ও এর মৃত্যুর হার কম। সুতরাং এটি নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।’
প্রোস্টেট ও স্তন ক্যানসারের ঝুঁকিতে কারা এবং কেন এটি হয়—এই প্রশ্নের জবাবে ডা. মো. মোফাজ্জেল হোসেন জানান, প্রোস্টেট ক্যানসারের ঝুঁকিতে থাকে প্রথমত পুরুষ, যাঁদের বয়স পঞ্চাশের বেশি। স্বাভাবিকভাবে ৭০ থেকে ৮০ বছরের পুরুষেরা আক্রান্ত হন। অর্থাৎ ৩৫ থেকে ৪০–এর আগে সাধারণত হয় না। এটি মেইল সেক্স হরমোনের ওপর নির্ভর করে। অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যভ্যাসের কারণে এ রোগের ঝুঁকি বাড়ে। যেমন সবজি কম, ফ্যাট বেশি খাওয়া। তাই ফল, সবজি, মাছ পর্যাপ্ত পরিমাণে খেতে হবে। টমেটো প্রোস্টেট ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। এ ছাড়া সূর্যরশ্মি ও রেডিয়েশন প্রোস্টেট ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়। ধূমপান ও মদ্যপানের কারণেও এটি হতে পারে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বংশগতভাবেও এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। আর স্তন ক্যানসার হয় ৯৯ দশমিক ৯৯ শতাংশ নারীদের, যাঁদের বয়স ৪০–এর বেশি। এটি ফিমেইল হরমোনের ওপর নির্ভর করে। ঋতুস্রাব বেশি দিন পর্যন্ত হওয়া, সন্তান না নেওয়া, শিশুকে স্তন্যপান না করানো এবং বংশগত—এসব কারণে নারীদের স্তন ক্যানসার হয়ে থাকে।
প্রোস্টেট ক্যানসারের লক্ষণগুলো সম্পর্কে উপস্থাপক জানতে চাইলে ডা. মো. মোফাজ্জেল হোসেন বলেন, ‘অনেকেই প্রোস্টেট ক্যানসার ও বিনাইন হাইপার ট্রপি অব প্রস্ট এনলার্জমেন্ট অব প্রোস্টেট (বিইপি)—এ দুয়ের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন। কারণ, দুটি রোগের লক্ষণ প্রায় একই। সেগুলো হলো, ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, প্রস্রাব আটকে রাখতে না পারা, প্রস্রাব আটকে যাওয়া, প্রস্রাবের সঙ্গে রক্ত যাওয়া, প্রায়ই ইউরিন অ্যাটাক ইনফেকশন হওয়া এবং যৌনক্ষমতা হ্রাস পাওয়া।’
এ সংশয় দূর করার উপায় সম্পর্কে ডা. মো. মোফাজ্জেল হোসেন জানান, সাধারণত প্রোস্টেট ক্যানসার চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে শনাক্ত হয়। যখন সেটা ছড়িয়ে পড়ে মেরুদণ্ডের হাড়ে চলে যায়। ফলে কোমরে ব্যথা হয়। এটা প্রোস্টেট ক্যানসারেরই লক্ষণ। তাই সংশয় দূর করতে প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডটাকে মূল্যায়ন ও পিএসএ টেস্ট করতে হবে।
এরপর উপস্থাপক বলেন, এ রকম পরিস্থিতিতে রোগী কখন চিকিৎসকের কাছে যাবে এবং পিএসএ টেস্টটা সম্পর্কে যদি আরেকটু বলতেন।
ডা. মো. মোফাজ্জেল হোসেন বলেন, লক্ষণ বোঝার সঙ্গে সঙ্গে তো বটেই এমনকি পরিণত বয়সেও যদি কোমরে ব্যথা হয়, তাহলেও যেতে হবে। তখন চিকিৎসক ডিজিটাল রেক্টল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে দুটি বিষয় বুঝতে পারবেন। একটি হলো, প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডটা বড় কি না; অন্যটি হলো, এটার গঠন কেমন? আর পিএসএ হলো—প্রোস্টেট স্পেসিফিক অ্যান্টিজেন। এটি বাড়লেই ক্যানসার হবে না। এর সঙ্গে আলট্রাসোনো, এমআরআই ও বায়োপসি করতে হয়। বায়োপসির মাধ্যমে ক্যানসারের ঝুঁকির স্তর সম্পর্কে বুঝতে পারা যায়।
ক্যানসার নিরাময়ে দেশের চিকিৎসাপদ্ধতি কতটা আধুনিক, উপস্থাপকের এমন প্রশ্নের জবাবে ডা. মো. মোফাজ্জেল হোসেন বলেন, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি, আমাদের বাংলাদেশেই বিশ্বমানের ক্যানসার চিকিৎসা রয়েছে। ক্যানসার চিকিৎসায় বিভিন্ন মডালিটির মধ্যে সার্জারিটাই বেশি ফলপ্রসূ। এরপর আছে কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি, অ্যান্টিবডি ট্রিটমেন্ট ও ইমিউনোথেরাপি। তবে অনেক ক্ষেত্রে কিছুই লাগে না, শুধু হরমোন–চিকিৎসাতেই ভালো ফল হয়।
এ পর্যায়ে উপস্থাপক জানতে চান, বাংলাদেশে বিশ্বমানের আধুনিক চিকিৎসা থাকা সত্ত্বেও ক্যানসারের চিকিৎসার জন্য অনেকে বিদেশে যান কেন? আর বিদেশ ও দেশের চিকিৎসার মধ্যে পার্থক্যটা কী?
এ প্রসঙ্গে ডা. মো. মোফাজ্জেল হোসেন বলেন, উন্নত ক্যানসার চিকিৎসায় আমেরিকা–সিঙ্গাপুর–ভারতের মতো আমাদেরও তত্ত্বীয় জ্ঞান আছে। চিকিৎসাব্যবস্থারও ঘাটতি নেই। ডায়াগনোসিসটা ৯৯ শতাংশ আর ইনভেস্টিগেশন ৯০ শতাংশ রয়েছে। ক্যানসার চিকিৎসার মডালিটিগুলোসহ পেট সিটিস্ক্যানও আমাদের এখানে হয়। তাই আমি সবাইকে বলব, আপনারা দেশেই বিশ্বমানের ক্যানসার চিকিৎসা করাতে পারেন। এর সঙ্গে যুক্ত করে উপস্থাপক জানান, বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র ইউজিএমপি এবং অ্যানভিজা ব্রাজিল অনুমোদিত প্ল্যান্ট হলো ‘এসকেএফ অনকোলজি’।
দেশে ক্যানসার চিকিৎসা নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা ও প্রতিবন্ধকতাগুলো কী এবং এর থেকে উত্তরণের উপায় কী—এমন প্রশ্নের উত্তরে ডা. মো. মোফাজ্জেল হোসেন বলেন, সামাজিক ভ্রান্ত ধারণা হলো, স্তন ক্যানসার হলে নারীরা পুরুষ ডাক্তারকে দেখাতে চান না। এখানে লজ্জা পাওয়া যাবে না। তারপর রয়েছে ধর্মান্ধতা, কবিরাজি চিকিৎসা এবং অশিক্ষা–অসচেতনতা। এসব থেকে উত্তরণ পেলে এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যানসার শনাক্ত করতে পারলে ক্যানসারকে জয় করা সম্ভব হবে। আর রোগীদের কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, সেগুলো হলো, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা। আরেকটি বিষয় হচ্ছে, অনেকেরই স্বাস্থ্যবিমা নেই। এটি থাকলেও চিকিৎসা–ব্যয় বহনে কিছুটা চিন্তামুক্ত হওয়া যায়।
কেমোথেরাপি চলাকালে রোগীর করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে ডা. মো. মোফাজ্জেল হোসেন বলেন, ‘কোনো কিছুই নিষেধ নেই। তবে শারীরিক ফিটনেসভেদে রোগীদের কিছু বিষয় মেনে চলতে হয়। যেমন সিদ্ধ খাবার খেতে হবে। কাঁচা সবজি, সালাদ, ফ্রিজের ও বাইরের খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। কেমোথেরাপি চলাকালে মাঝের সপ্তাহে জনসমাগম এড়িয়ে চলতে হবে। কারণ, এ সময় শরীরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কম থাকে বলে সহজেই আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। বাসায় তৈরি খাবার খাওয়া এবং আঙুর ও চিনি না খাওয়াই ভালো। সহজে হজম হয় এবং অল্পতে বেশি ক্যালোরি পাওয়া যায়, এ রকম প্রোটিনযুক্ত খাবার খাওয়া উচিত।
শিশুজন্মে অস্ত্রোপচারে বছরে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় প্রায় ২৯০০ কোটি টাকা
শিশুজন্মে অস্ত্রোপচার বাবদ দেশে প্রতিবছর ৩ হাজার ৮৪৬ কোটি টাকা খরচ হয়। এর মধ্যে প্রায় ২ হাজার ৯০০ কোটি টাকা ব্যয় হয় অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারে। বিশেষজ্ঞরা বলেন, প্রসবের সময় অস্ত্রোপচার মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ায়।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর ব্যানবেইস মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপের (২০২২) চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের সময় দেশে শিশুজন্মে অস্ত্রোপচারে বিপুল খরচের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়। জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা প্রতিষ্ঠান (নিপোর্ট), আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআরবি) এবং যুক্তরাষ্ট্রের দাতা সংস্থা ইউএসএআইডি যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
স্বাস্থ্য খাতের গ্রহণযোগ্য তথ্য ও পরিসংখ্যানের উৎস জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ। জাতীয়ভিত্তিক এই জরিপের তথ্য নীতিনির্ধারক, গবেষক, চিকিৎসক, দাতা সংস্থা ও সাংবাদিকেরা নিয়মিত ব্যবহার করেন। ১৯৯৪ সালের পর থেকে দু–তিন বছর পরপর এই প্রতিবেদন নিয়মিত বের হচ্ছে। সর্বশেষ অর্থাৎ ২০২২ সালের জরিপের প্রাথমিক প্রতিবেদন ২০২৩ সালের এপ্রিলে প্রকাশ করা হয়েছিল। গতকাল ৫০২ পৃষ্ঠার চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। জরিপের বিভিন্ন বিষয় একাধিক গবেষক পৃথকভাবে উপস্থাপন করেন।
জন্ম ও জন্মের পেছনে ব্যয়
প্রতিবেদনের শিশুজন্মের স্থান, স্বাভাবিক প্রসব, অস্ত্রোপচারে শিশুজন্মবিষয়ক অংশটি উপস্থাপন করেন আইসিডিডিআরবির বিজ্ঞানী আহমদ এহসানূর রহমান। তিনি বলেন, দেশে বছরে ৩৬ লাখ শিশুর জন্ম হয়। এর মধ্যে ২০ লাখ প্রসব হয় স্বাভাবিক; বাকি ১৬ লাখ প্রসব হয় অস্ত্রোপচারে। অস্ত্রোপচারের ৮০ শতাংশই ঘটে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে।
অনুষ্ঠানের স্বাভাবিক প্রসব ও অস্ত্রোপচারে গড়ে কত খরচ হয়, তার একটি হিসাব দেওয়া হয়। তাতে দেখা যায়, প্রতিটি স্বাভাবিক প্রসবে ৭ হাজার ৭৬৫ টাকা খরচ হয়। অন্যদিকে প্রতিটি অস্ত্রোপচারে খরচ হয় ২৩ হাজার ৯৪৪ টাকা।
আহমদ এহসানূর রহমান বলেন, শিশুজন্মে অস্ত্রোপচারের জন্য বছরে ৩ হাজার ৮৪৬ কোটি টাকা খরচ হয়। এর মধ্যে তিন–চতুর্থাংশ অস্ত্রোপচারের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। অর্থাৎ ২ হাজার ৮৮৪ কোটি টাকা ব্যয় হয় অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারে। এমন অস্ত্রোপচারের ব্যয়ের ৮৭ শতাংশ হয় বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে।
মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, অস্ত্রোপচার একটি জীবনদায়ী ব্যবস্থা। গর্ভধারণ ও প্রসবে জটিলতার কারণে সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশ প্রসবের ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচার লাগতে পারে; কিন্তু এর কিছু ক্ষতিকর দিকও আছে। যেমন অস্ত্রোপচারে মায়ের শরীরে ক্ষতস্থানে সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে, অনেক সময় প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। ভবিষ্যতে মা হওয়ার ক্ষেত্রে জটিলতার ঝুঁকি থাকে। অন্যদিকে নবজাতকের শ্বাস নেওয়ার ও রক্তে শর্করা কম হওয়ার ঝুঁকি থাকে।
জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপে দেখা যাচ্ছে, দেশে হাসপাতালে বা ক্লিনিকে প্রসব বাড়ছে। ২০১৭–১৮ সালের জরিপে দেখা গিয়েছিল ৩৯ শতাংশ প্রসব বাড়িতে আর ৫১ শতাংশ প্রসব হাসপাতাল বা ক্লিনিকে হয়। এখন হাসপাতাল বা ক্লিনিকে প্রসবের হার বেড়েছে। ৬৫ শতাংশ প্রসব হচ্ছে হাসপাতাল বা ক্লিনিকে। এর মধ্যে বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিকে জন্ম হচ্ছে বেশি।
সিলেট পিছিয়ে
নিপোর্টের পরিচালক (গবেষণা) মোহাম্মদ আহছানুল আলম ১৫টি স্বাস্থ্য সূচকে বাংলাদেশের অবস্থা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, দেশের ৬৪ শতাংশ দম্পতি জন্মনিয়ন্ত্রণের সামগ্রী ব্যবহার করেন। বিভাগগুলোর মধ্যে সিলেটে এই হার সবচেয়ে কম। সিলেট বিভাগের ৪৪ শতাংশ দম্পতি জন্মনিয়ন্ত্রণের সামগ্রী ব্যবহার করেন। জন্মনিয়ন্ত্রণের সামগ্রী ব্যবহারের হার সবচেয়ে বেশি রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে। এই দুটি বিভাগে ৬১ শতাংশ করে দম্পতি জন্মনিয়ন্ত্রণের সামগ্রী ব্যবহার করেন।
জরিপে দেখা যাচ্ছে, প্রসবপূর্ব সেবা চারবার পান দেশের ৪১ শতাংশ গর্ভবতী, প্রসবের সময় প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর সহায়তা পান ৭০ শতাংশ মা, ৬৫ শতাংশ প্রসব হয় হাসপাতাল বা ক্লিনিকে, অত্যাবশ্যকীয় সেবা পায় মাত্র ৩ শতাংশ নবজাতক।
অনুষ্ঠানে জ্যেষ্ঠ স্বাস্থ্যসচিব এম এ আকমল হোসেন আজাদ, ব্যানবেইসের মহাপরিচালক মো. মজিবুর রহমান, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নাজমুল হোসেন প্রমুখ বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিপোর্টের মহাপরিচালক আশরাফী আহমদ।
ডার্ক সার্কেল কেন হয়, প্রতিরোধে কী করবেন
জীবনে ব্যস্ততা যেমন বাড়ছে, তেমনই স্ট্রেসের (চাপ) মাত্রাও বাড়ছে। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিদ্রাহীনতা। এ সবকিছুর যোগফল চোখের চারদিকে ডার্ক সার্কেল বা কালো দাগ। বিশেষ করে চোখের নিচের এ কালো দাগ নিয়ে অনেকেই বিড়ম্বনায় ভোগেন, করেন সংকোচবোধও। স্বাস্থ্যকর ও চিন্তামুক্ত জীবনযাপনে ডার্ক সার্কেল প্রতিরোধ করা যায়।
কেন হয়
চোখের চারদিকের অতি সূক্ষ্ম রক্তনালি সরু হয়ে যাওয়া ও কোলাজেন টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এ সমস্যার মূল কারণ।
কম ঘুম বা মাত্রাতিরিক্ত ঘুমেও এমনটা হতে পারে।
পানিশূন্যতা, রক্তশূন্যতা, হরমোনজনিত সমস্যা (থাইরয়েড), চোখের কিছু ওষুধ দীর্ঘদিন ব্যবহার, দীর্ঘদিনের এলার্জি, বংশপরম্পরা বা জিনগত কারণ।
যেকোনো বয়সেই ডার্ক সার্কেল দেখা দিতে পারে। বার্ধক্যে মুখের ফ্যাট ও কোলাজেন টিস্যু কমে যাওয়ায় বেশির ভাগ মানুষের এ সময় ডার্ক সার্কেল বেশি হয়।
চিকিৎসা
রেটিনয়েড ক্রিম ব্যবহার করা যায়। এটি চোখের নিচের ত্বক সুস্থ রাখে ও কোলাজেন উৎপাদন বাড়ায়। পিগমেন্টেশন কমাতেও সাহায্য করে এটি।
লাইটেনিং এজেন্ট, যেমন হাইড্রোকুইনোন, কোজিক অ্যাসিড বা ভিটামিন সি-এর মতো উপাদান ধারণকারী টপিক্যাল এজেন্টগুলো হাইপারপিগমেন্টেড জায়গাগুলো হালকা করে ডার্ক সার্কেল কমায়।
হায়ালুরোনিক অ্যাসিডের মতো ইনজেকশনযোগ্য ফিলারগুলো চোখের নিচের অংশের ফাঁপা ভাব বা ভলিউম কমায়।
আইপিএল থেরাপি রক্তনালি ও পিগমেন্টেশন কমায় এবং চোখের নিচে লাল ভাব, ডার্ক সার্কেল দূর করে।
লেজার চিকিৎসা কোলাজেন উৎপাদনকে উদ্দীপিত করতে পারে, ত্বকের গঠন উন্নত করে ও পিগমেন্টেশন কমায়।
প্লাজমা থেরাপিতে রোগীর রক্তের সামান্য নিয়ে প্লাটিলেটকে ঘনীভূত করে চোখের নিচের অংশে পিআরপি ইনজেকশন দেওয়া হয়।
চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ অ্যান্টিহিস্টামাইন বা টপিক্যাল স্টেরয়েডের মতো ওষুধ দিতে পারেন ডার্ক সার্কেল প্রতিকারে।
প্রতিরোধ
জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ডার্ক সার্কেল কমাতে সহায়তা করে। নিয়মিত ছয় থেকে আট ঘণ্টা ঘুম, হালকা শারীরিক ব্যায়াম, খাদ্যাভ্যাসে প্রচুর শাকসবজি ও ফলমূল রাখা জরুরি।
ঘরোয়া কিছু পদ্ধতিতে যত্ন নিতে পারেন, যেমন চোখের চারদিকে ঠান্ডা সেক নেওয়া, নিয়মিত ম্যাসাজ, ঠান্ডা আলু বা শসার প্যাক ব্যবহার করা।
দিনে তিন থেকে চার লিটার পানি পান করতে হবে।
বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী রক্তের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক করা, হরমোন সমস্যার সমাধান করা এবং কিছু মলম যেমন হাইড্রোকুইনন, গ্লাইকোকোলিক অ্যাসিডের ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।
গরমে এসি ছাড়া ঘর ঠান্ডা রাখার ১৫টি টিপস
আপনি যদি বড় অঙ্কের টাকা খরচ না করে এসি ছাড়া ঘর ঠান্ডা রাখতে চান, তাহলে এই নিবন্ধটি আপনার জন্য। বিশেষজ্ঞরাও এসি বসানোর চেয়ে বরং এই টিপসগুলো মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন; যেগুলো কার্যকর এবং একইসাথে পরিবেশ বান্ধব।
১. জানালা কখন খুলবেন কখন বন্ধ থাকবে?
ঘরের জন্য প্রাকৃতিক আলো জরুরি হলেও গরমকালে ঘরে যত সূর্যের আলো ঢুকবে, ঘর তত গরম হয়ে উঠবে।
তাই দিনের বেলায় জানালা বন্ধ রাখুন। বিশেষ করে পশ্চিম ও উত্তরমুখী জানালাগুলো।
জানালাগুলোয় হালকা রঙের, মোটা, সূতির পর্দা টেনে দিন। পর্দাটি এমন পুরু হবে যা ঘর অন্ধকার করে দেবে।
পর্দার বাইরের দিকে, অর্থাৎ যে অংশ সূর্যের দিকে থাকে সেদিকে সাদা কাপড় সেলাই করা থাকলে বা আরেকটি সাদা পর্দা থাকলে সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে ঘর ঠান্ডা থাকবে।
পর্দায় ঠান্ডা পানি স্প্রে করলে বা পর্দার উপর ভেজা চাদর ঝুলিয়ে দিলে সেই পানি বাষ্পীভূত হয়ে ঘর কিছুটা শীতল হবে।
সম্ভব হলে জানালাগুলো পানিতে ধুয়ে নিতে পারেন।
যতক্ষণ সূর্য প্রখর থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত জানালা-দরজা বন্ধ রাখবেন। তবে সূর্যাস্তের পর যখন পরিবেশ কিছুটা ঠান্ডা হতে শুরু করবে, তখন পর্দা সরিয়ে ঘরের সব দরজা জানালা খুলে দেবেন যাতে শীতল বাতাস ঢুকতে পারে৷
ঘরের গরম তাপ বাইরে বের করে দিতে যে ঘরে আপনি থাকবেন, তার জানালা খুলে বাতাস ঢুকতে দিন। তার বিপরীত কোনে থাকা অপর ঘরের জানালা খুলে বাইরের দিকে মুখ করে ফ্যান বসিয়ে দিন। এতে ঘরের গরম বাতাস বাইরে বেরিয়ে যাবে।
একে বলা হয় ক্রস ভেন্টিলেশন যা ঘর দ্রুত ঠান্ডা করে। তবে সকালে কড়া রোদ ওঠার আগেই সব দরজা জানালা আবার বন্ধ করে দিতে হবে।
২. জানালা, দেয়াল ও ছাদে প্রলেপ
জানালায় যদি হিট প্রোটেক্টিভ উইন্ডো ফিল্ম লাগানো হয় তাহলে সেটা ৭৮ শতাংশ সৌর তাপ এবং ৯৯ শতাংশ ক্ষতিকারক ইউভি রশ্মি আটকে দিতে পারে। যার ফলে ঘর গরম হওয়া অনেকটা ঠেকানো যায়।
উইন্ডো ফিল্ম হলো রঙিন স্টিকারের মতো আবরণ যেটা জানালার কাঁচের উপর বসানো হয়। এটা বিভিন্ন অনলাইন মার্কেটে পাওয়া যায়।
তবে উইন্ডো ফিল্ম না পেলে জানালার বাইরের কাঁচ সাদা রঙ করে বা সাদা কাগজ লাগিয়ে দিলেও হবে।
এছাড়া দু'টি স্তর বিশিষ্ট কাঁচের জানালা সাধারণ জানালার চেয়ে অনেক ভালো তাপ নিরোধক হিসেবে কাজ করে।
এসব কাঁচ তিন থেকে ১০ মিলিমিটার পুরু হয়, যা প্রচন্ড তাপ থেকে রক্ষা করে।
অন্যদিকে, ঘরের ছাদে ও দেয়ালে ইনসুলেশন করলে গরমকালে ঘর ঠান্ডা থাকে আবার শীতকালে ঘর গরম থাকে। এই ইনসুলেশন হলো এক ধরনের মোটা প্রলেপ।
এক্ষেত্রে কন্সট্রাকশন বা ইন্টেরিয়র নিয়ে যারা কাজ করেন তাদের সেবা ক্রয় করতে পারেন।
আপনার ঘরে কোন ইন্সুলেশন সবচেয়ে ভালো কাজ করবে সেটা তারাই বলে দেবেন।
৩. ছাউনি
জানালার উপরে বিশেষ করে পূর্ব পশ্চিমের জানালায় সানশেড থাকলে তা রোদের তাপ অনেকটাই আটকে দেয়।
সানশেড না থাকলে জানালার ওপর হালকা রঙের ছাউনি টানিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করতে পারেন।
যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যুৎ বিভাগের তথ্যমতে, জানালার উপর ছাউনি বসালে সূর্যের তাপ ৭৭ শতাংশ পর্যন্ত আটকানো যায়।
৪. দেয়াল, মেঝে, আসবাবপত্র
ঘরের দেয়াল, মেঝে, আসবাবপত্রের রঙ যত গাঢ় হয় তত বেশি আলো শোষণ করে এবং তাপমাত্রা বাড়ে।
আর রঙ যত হালকা হয়, আলো তত কম শোষণ হয়, প্রতিফলিত হয় বেশি এতে তাপমাত্রা তেমন বাড়ে না। তাই ঘরের দেয়াল, মেঝে ও আসবাবপত্রের রঙ হালকা রাখার চেষ্টা করা যেতে পারে।
এক্ষেত্রে দেয়ালে তাপনিরোধী পেইন্ট ব্যবহার করা যায়।
এছাড়া মেঝে ঠান্ডা রাখার ক্ষেত্রে মার্বেল, স্যান্ডস্টোন বা গ্রানাইটের টাইলস খুব ভালো। তবে এগুলো অনেক দামি।
এক্ষেত্রে কাঠ, ভিনাইল প্ল্যাঙ্ক, সাদা রঙের সিরামিকের টাইলস বা পোরসেলিন টাইলস ব্যবহার করলে ঘর ও আশেপাশের তাপমাত্রা অনেক কমে আসবে।
মাটির ঘর হলে মাটি নতুন করে লেপে দিলেও ঘরে ঠান্ডা ভাব থাকবে।
এছাড়া আসবাবপত্র কাঠের হলে হালকা রঙের বার্নিশ করিয়ে নেয়া যেতে পারে।
সবকিছু হালকা রঙ হলে দিনের আলো চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘর ঠান্ডা হতে শুরু করবে।
আরেকটি বিষয়; ঘরের ভেতর আসবাবপত্র যতটা সম্ভব কম রাখলে তাপ শোষণও কম হবে।
৫. ছাদ
কারও ছাদ যদি গাঢ় রঙের হয় তাহলে ওই বাড়ির তাপমাত্রা অনেকটা বেড়ে যায়।
অন্যদিকে, বাড়ির ছাদ যদি সাদা রঙে ছেয়ে দেয়া যায় সেটা টিনের ছাদ হোক বা কংক্রিটের, সূর্যের আলোর বেশিরভাগই প্রতিফলিত হবে। এতে বাড়ি ঠান্ডা থাকবে।
দেখা গিয়েছে সাদা রঙ ৮৫ শতাংশ আলো প্রতিফলিত করতে পারে যেখানে গাঢ় রঙ প্রতিফলন করে মাত্র ২০ শতাংশ।
সাদা রঙ করা ছাদের বাড়িগুলো দ্বিগুণেরও বেশি ঠান্ডা থাকে।
অনেকে আছেন বাড়ির ছাদে ও আশেপাশে কংক্রিট পেভমেন্ট ব্লক বসান। কিন্তু এই ব্লকগুলো গরম ধরে রাখে।
এতে দিন ও রাত দুই সময়ে পরিবেশ প্রচণ্ড গরম থাকে। এক্ষেত্রে সাদা টাইলস বিকল্প সমাধান হতে পারে।
ছাদ ঠান্ডা রাখার আরেকটি ভালো উপায় ছাদে বাগান করা। আবার ঘাসও বিছিয়ে দেয়া যায়। এক্ষেত্রে ছাদটি ওয়াটার প্রুফ বা পানি নিরােধক হতে হবে।
এছাড়া ছাউনি লাগিয়ে বা ছাদে সোলার প্যানেল বসিয়েও সমস্যার সমাধান করা যায়।
৬. সিলিং ফ্যান
কখনও কখনও আপনার মনে হতে পারে সিলিং ফ্যান ঘর তো ঠান্ডা করছেই না বরং গরম বাড়াচ্ছে।
এমনটা হওয়ার কারণ ফ্যানটি ঠিক দিকে ঘুরছে না। ফ্যানের পাখাগুলো ঘড়ির কাঁটার গতিতে ঘুরলে ছাদের গরম বাতাস চারিদিকে ছড়িয়ে যায়।
কিন্তু পাখাগুলো ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরলে সেটা গরম বাতাস ঠেলে বের করে দিয়ে ঘর ঠান্ডা করতে পারে।
তাই খেয়াল করে দেখুন আপনার ফ্যান ঠিক দিকে ঘুরছে কি না। সিলিং ফ্যান সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে। অপরিষ্কার ফ্যান থেকে ঠিকঠাক বাতাস পাওয়া যায় না।
৭. ঠান্ডা বাতাস
ঘরের ফ্যান থেকে এয়ার কুলারের মতো ঠান্ডা বাতাস পেতে একটি প্লেটের উপর বড় বেশ খানিকটা বরফ রেখে সেই বরাবর টেবিল ফ্যান ছেড়ে দিন।
সিলিং ফ্যানের সরাসরি নীচে রাখলেও হবে। এতে ঘরের বাতাস দ্রুত ঠান্ডা হয়ে আসবে। তবে বরফ রাখার পাত্রটি অগভীর হলেই ভালো।
বরফ না থাকলে ফ্যানের সরাসরি নীচে ঠান্ডা পানির বালতি রাখলেও কাজে দেবে।
এছাড়া ঘর ঝাড়ু দেয়ার পর দিনে কয়েকবার বরফ ঠান্ডা পানিতে ঘর ভেজা ভেজা করে ঘর মুছে নিলে তা ঘর ঠান্ডা রাখতে বেশ কার্যকর উপায়।
৮. এক্সস্ট ফ্যান
ঘর ঠান্ডা রাখতে বিশেষ করে ঘরের ভেতরের তাপ বাইরে বের করে দিয়ে এবং বাইরের ঠান্ডা বাতাস ভেতরে টেনে আনতে এক্সস্ট ফ্যান একটি ভালো সমাধান।
এটি মূলত দেয়ালের উপরের দিকে বসানো বৈদ্যুতিক পাখা।
এটি রান্নাঘর ও টয়লেটসহ যেকোনও ঘরেই বসানো যেতে পারে।
রান্নাঘরে যতক্ষণ রান্না করবেন ততোক্ষণ ফ্যানটি চালিয়ে রাখতে হবে।
এই পদ্ধতিটি তখনই ভালো কাজ করে যখন ভিতরের তাপমাত্রা বাইরের থেকে বেশি হয়।
৯. বিছানা তোশক বালিশ
বিছানা, বালিশ, তোষকের জন্য ১০০ শতাংশ পাতলা সুতির কাপড়ের বিকল্প নেই। কারণ সিল্ক বা পলেস্টার জাতীয় কাপড় তাপ ধরে রাখে, যেটা সুতিতে হয় না।
বিছানার চাদরের ক্ষেত্রে হালকা রঙ বিশেষ করে সাদা একরঙা চাদর বেছে নেয়া যেতে পারে। বেশি রঙিন ও নকশাদার চাদর তাপ শোষণ করে থাকে।
এছাড়া আমরা সচরাচর বিছানায় যেমন তুলার তোশক, জাজিম ব্যবহার করি বা সোফায় যেসব গদি বসাই তা শরীর এবং আশেপাশের থেকে প্রচুর তাপ শোষণ করে।
এক্ষেত্রে বাঁশ বা অন্যান্য প্রাকৃতিক ফাইবারের তোশক, জাজিম ও গদি ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো উপায়।
সেটা সম্ভব না হলে বিছানা বা সোফায় সুতি চাদর বিছিয়ে দিলেও কিছুটা কাজে দেবে।
এছাড়া বালিশের ক্ষেত্রে চিলো নামের বালিশগুলো বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে যা গরমের সময়েও মাথা ঠান্ডা রাখে।
এছাড়া বরফ জমানো পানির বোতল বিছানার পায়ের কাছে রাখলেও ঠান্ডার অনুভূতি পাবেন, তবে এতে বিছানা ভিজে যাওয়ার শঙ্কা থাকে।
আপনি যদি দোতলা বাসায় থাকেন, তাহলে খেয়াল করে দেখবেন, নিচতলা অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা। তাই মেঝেতে যদি মাদুর, চাটাই বা শীতলপাটি বিছিয়ে ঘুমান তাহলে বিছানার চাইতে আরাম লাগতে পারে।
১০. বাতি পরিবর্তন
আপনি ঘরে কী ধরনের বাতি জ্বালান তার সাথে তাপমাত্রার বড় যোগ আছে। বাংলাদেশে একসময় হলদে আলোর হ্যালোজেন বাতি ব্যবহৃত হতো, যা প্রচুর তাপ উৎপন্ন করে।
কিন্তু গত দুই দশক ধরে এলইডি লাইটের মতো বিদ্যুৎ-সাশ্রয়ী বাতির ব্যবহার বেড়েছে।
যার বড় সুবিধা এতে তাপ উৎপন্ন হয় খুব কম।
একটি বৈদ্যুতিক বাতি খুব সামান্য হলেও তাপ উৎপন্ন করে থাকে। তাই যেসব বাতির প্রয়োজন নেই সেগুলো বন্ধ রাখা দরকার।
১১. রান্না
আপনি কখন ও কতক্ষণ ধরে রান্না করছেন সেটিও বেশ জরুরি।
কেননা রান্না অনেক তাপ উৎপন্ন করে এবং আপনার বাড়ির তাপমাত্রা অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়।
তাই গরমে এমন খাবার খাওয়া যেতে পারে, যেগুলো অল্প সময়ে রান্না হয়ে যায় বা যেগুলো রান্নার প্রয়োজন নেই।
এতে চুলা বা ওভেন অল্প সময় চালু থাকে, ফলে উত্তাপ কম ছড়ায়।
তবে যাদের রান্নাঘর মূল ঘরের বাইরে তাদের ঘর অনেকটা ঠান্ডা থাকে।
১২. বৈদ্যুতিক যন্ত্র
আপনার ঘরে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেমন মোবাইল, চার্জার, ল্যাপটপ, কম্পিউটার, ওভেন, আয়রন, হেয়ার ড্রায়ার, প্রতিনিয়ত তাপ উৎপন্ন করে।
আপনি যন্ত্রটি চালাচ্ছেন না কিন্তু প্লাগ ইন করে রেখেছেন, এতেও তাপ উৎপন্ন হয়। তাই যন্ত্র ব্যবহার শেষে প্লাগের সংযোগ খুলে ফেলাই ভালাে।
গরমকালে ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস যতটা কম ব্যবহার করা যায়, এতে বিদ্যুৎ খরচ কম আসবে, ঘরও ঠান্ডা থাকবে।
১৩. গাছ
যদি আপনার বাড়ির আঙিনায় খোলা জায়গা থাকে তাহলে সেখানে ছায়া দেয়ার মতো বড় গাছ লাগাতে পারেন।
গাছ বড় করে তুলতে সময় ও ধৈয্যের দরকার কিন্তু এর ফলাফল খুবই কার্যকর। কারণ একটি ছায়া দেয়া বড় গাছ ৭০ শতাংশ রোদ ঠেকাতে সক্ষম।
এক্ষেত্রে জরুরি হলো সঠিক গাছ বাছাই করা যা আপনার ঘরকে আসলেও ঠান্ডা রাখবে, বাতাস বিশুদ্ধ রাখবে, ছায়া দেবে।
এটা ফুল গাছ বা ফল গাছ কিংবা অন্য গাছও পারে, নির্ভর করবে মাটি ও জায়গার পরিধির ওপর।
এছাড়া ঘরে গাছ থাকলে ভিতরে জমা হওয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষে নেয়, ফলে ঘরের তাপমাত্রা তুলনামূলক কম থাকে।
এক্ষেত্রে মানিপ্ল্যান্ট, অ্যালোভেরা, অ্যারিকা পাম-জাতীয় গাছ বেছে নিতে পারেন। ঘরের বাইরে ঘাসজাতীয় গাছ লাগালে কিংবা বাগান বিলাস গাছ লাগালেও ঘর ঠান্ডা থাকবে।
১৪. ডিহিউমিডিফায়ার
আপনি যদি এসি কিনতে না চান সেক্ষেত্রে ডিহিউমিডিফায়ার কিনতে পারেন।
এর কাজ হলো ঘরের আর্দ্রতা শোষণ করা। বাংলাদেশের জলবায়ুতে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকায় গরম বেশি অনুভূত হয় এবং অস্বস্তি লাগে।
তবে ডিহিউমিডিফায়ারের সাহায্যে আর্দ্রতা বের করে দিতে পারলে অনেকটাই ঠান্ডা আর আরামদায়ক লাগে।
১৫. শরীর ঠান্ডা রাখা
ঘর ঠান্ডার রাখার ক্ষেত্রে জরুরি হলো ঘরে থাকা মানুষদের শরীর ঠান্ডা রাখা।
আর এজন্য তাদের পর্যাপ্ত পানি খেতে হবে, সহজে হজম হয় এমন খাবার খেতে হবে, দিনে অন্তত একবার বা দু'বার ঠান্ডা পানিতে গোসল করতে হবে এবং সুতির হালকা রঙের পাতলা ঢিলেঢালা পোশাক পরতে হবে।
প্রয়োজনে গায়ে পানি ছিটিয়ে ফ্যানের বাতাসে শরীর ঠান্ডা করতে হবে।
এই ১৫টি পদক্ষেপ নিলে আপনার ঘর এসির মতো না হোক, আগের চাইতে অনেকটাই ঠান্ডা থাকবে, সেটা বলা যেতে পারে।
নারীদের শরীরের চামড়া ঝুলে যায় যে রোগে
লাইপেডিমা একটা অপরিচিত রোগ, যেটিকে প্রায়ই স্থূলতার (ওবেসিটি) সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়। প্রধানত নারীদেরই এই রোগ হয়ে থাকে। এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা হিসেবে তাদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনার পরামর্শ দেওয়া হয়।
যদিও লাইপেডিমা স্থূলতার থেকেও অনেক বেশি গুরুতর রোগ। শুধুমাত্র ওজন কমিয়ে এই রোগ থেকে মুক্তি মেলে না।
এই রোগ সম্পর্কে এখনও পর্যন্ত আমরা কী জানি? কীভাবে এই রোগ মোকাবেলা করা সম্ভব?
রোগবিদ্যা বা প্যাথলজিতে এটি লাইপোডিসট্রফিস নামে পরিচিত।
লাইপেডিমায় শরীরের চর্বির ভারসাম্য পরিবর্তন হয়। একইভাবে তা ফ্যাটি টিস্যুর ব্যাপক অসামঞ্জস্যপূর্ণ বৃদ্ধি ঘটায়।
যদিও এটা সচরাচর পায়ে হয়, এ রোগে নিতম্ব এবং বাহুও আক্রান্ত হতে পারে। এর ফলে কোমর এবং অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়।
বর্তমানে এই রোগ নির্ণয়ের জন্য কোন অভ্রান্ত পরীক্ষা নেই। অর্থাৎ এই রোগ নিশ্চিতভাবে নির্ণয় করা যাবে, এমন কোনও পরীক্ষা নেই।
রোগীর চিকিৎসার ইতিহাস, শারীরিক পরীক্ষার ফলাফল, যে কোনও ধরনের ক্লিনিক্যাল উপসর্গ এবং একই সাথে রোগীর শরীরে একটি বা দুইটি রোগের উপস্থিতি অথবা এর সাথে জড়িত যে কোনও উপসর্গ - সব কিছুর উপর ভিত্তি করে এই রোগ নির্ণয়ের জন্য একটি মূল্যায়ন করতে হয়।
২০১৮ সাল পর্যন্ত চিহ্নিতই করা হয়নি!
যদিও ১৯৪০ সালে এই রোগটি সম্পর্কে প্রথম জানা যায়, কিন্তু তারপরও বিগত দশকগুলোতে এই রোগটি সবার অগোচরে রয়ে গেছে।
সত্যিকার অর্থে ২০১৮ সালের মে মাস পর্যন্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই রোগটিকে রোগের আন্তর্জাতিক শ্রেণী বিভাজনে অন্তর্ভুক্ত করেনি।
ওই বছরই স্পেনে প্রথম সর্বসম্মতভাবে লাইপেডিমা রোগের নথি তৈরি করা হয়।
প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছিল এ রোগের কারণে শরীরে ফ্লুইড তৈরি হয়। অথবা শরীরের টিস্যুতে তরল জমা হয়ে ফুলে ভারি হয়ে যায়, যেটি ফোলা রোগ নামে পরিচিত।
তবে এখনও পর্যন্ত এ রোগের কারণে শরীরের টিস্যুতে তরল জমে ভারি হওয়ার কারণে বিভিন্ন অঙ্গের বৃদ্ধি অথবা ব্যথা বা অন্য উপসর্গ দেখা দেওয়ার কোনও প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি।
এই কারণে ‘লাইপেডিমা’ টার্মটিকে ‘লিপালজিয়া সিনড্রোম’-এ (অস্বাভাবিক ফ্যাটি টিস্যু জমে ব্যথা হওয়া) রূপান্তর করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।
লাইপেডিমা রোগের একটি বৈশিষ্ট্য হল টিস্যুর যেখানেই স্পর্শ করা হয় সেখানেই ব্যথা বোধ হয়।
স্বাস্থ্যের অন্যান্য সমস্যার সাথেও এই রোগটি হয়। যেমন, শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টে অত্যধিক গতিশীলতা, পেশী শক্তি হ্রাস এবং ঘুমের ব্যাঘাত হলেও লাইপেডিমা রোগের উপসর্গগুলি দেখা দেয়।
এছাড়াও এ রোগ শিরা, ধমনী বা লসিকা তন্ত্রের (লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম) পরিবর্তনের মতো অবস্থাতেও একই সাথে হতে পারে।
২০১৮ সাল পর্যন্ত চিহ্নিতই করা হয়নি!
যদিও ১৯৪০ সালে এই রোগটি সম্পর্কে প্রথম জানা যায়, কিন্তু তারপরও বিগত দশকগুলোতে এই রোগটি সবার অগোচরে রয়ে গেছে।
সত্যিকার অর্থে ২০১৮ সালের মে মাস পর্যন্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই রোগটিকে রোগের আন্তর্জাতিক শ্রেণী বিভাজনে অন্তর্ভুক্ত করেনি।
ওই বছরই স্পেনে প্রথম সর্বসম্মতভাবে লাইপেডিমা রোগের নথি তৈরি করা হয়।
প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হয়েছিল এ রোগের কারণে শরীরে ফ্লুইড তৈরি হয়। অথবা শরীরের টিস্যুতে তরল জমা হয়ে ফুলে ভারি হয়ে যায়, যেটি ফোলা রোগ নামে পরিচিত।
তবে এখনও পর্যন্ত এ রোগের কারণে শরীরের টিস্যুতে তরল জমে ভারি হওয়ার কারণে বিভিন্ন অঙ্গের বৃদ্ধি অথবা ব্যথা বা অন্য উপসর্গ দেখা দেওয়ার কোনও প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি।
এই কারণে ‘লাইপেডিমা’ টার্মটিকে ‘লিপালজিয়া সিনড্রোম’-এ (অস্বাভাবিক ফ্যাটি টিস্যু জমে ব্যথা হওয়া) রূপান্তর করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।
লাইপেডিমা রোগের একটি বৈশিষ্ট্য হল টিস্যুর যেখানেই স্পর্শ করা হয় সেখানেই ব্যথা বোধ হয়।
স্বাস্থ্যের অন্যান্য সমস্যার সাথেও এই রোগটি হয়। যেমন, শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টে অত্যধিক গতিশীলতা, পেশী শক্তি হ্রাস এবং ঘুমের ব্যাঘাত হলেও লাইপেডিমা রোগের উপসর্গগুলি দেখা দেয়।
এছাড়াও এ রোগ শিরা, ধমনী বা লসিকা তন্ত্রের (লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম) পরিবর্তনের মতো অবস্থাতেও একই সাথে হতে পারে।
সক্রিয় ভূমিকা
এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, রোগীকে নিজের চিকিৎসার জন্য অতি আগ্রহী হতে হবে।
যে সব রোগের প্রতিকার নেই এমন অন্যান্য অসুস্থতার জন্য এটা সাধারণ যে রোগী নিজেই অভ্যাস গড়ে তুলবে।
একই সাথে কিছু অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন, যাতে দীর্ঘমেয়াদে রোগের লক্ষণ এবং স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নতি হবে।
ফিজিওথেরাপি
এ রোগে আক্রান্ত রোগীদের স্ট্রেচার প্রয়োজন হতে পারে।
লাইপেডিমায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা যাতে স্বাধীনভাবে চলাচল করতে পারে সে লক্ষ্যে ফিজিওথেরাপিস্টরা কাজ করেন।
উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এ রোগে আক্রান্ত রোগীদের শিক্ষিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাতে তারা রোগটি সম্পর্কে জানে যে এটা কী এবং কী নয়।
একইসাথে কোন অভ্যাসগুলো উপকারী এটাও জানা তাদের জন্য জরুরি।
ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে রোগী তার দৈনন্দিন জীবনে ধীরে ধীরে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অভ্যাস গড়ে তোলে।
একই সাথে তাদের বৈশিষ্ট্যের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার মত ব্যায়ামের নির্দেশিকা তৈরি করা হয়।
কমপ্রেশন থেরাপি
এই কমপ্রেশন থেরাপির মাধ্যমে পায়ে রক্তপ্রবাহ বাড়ানোর জন্য নিয়ন্ত্রিত চাপ প্রবাহের কৌশল ব্যবহার করা হয়।
কমপ্রেশন মোজা পরলে এই ফ্যাটি টিস্যু কমবে না। অথবা আপনার ওজন বাড়লেও পায়ে চর্বি বৃদ্ধি রোধ করবে না।
যাই হোক, সুস্থ ব্যক্তিদের উপর গবেষণায় দেখা গেছে যে ত্বকের নিচের টিস্যুতে প্রদাহজনক প্রক্রিয়ার উপর এই নিয়ন্ত্রিত চাপ প্রবাহের থেরাপি বেশ উপকারী প্রভাব ফেলে।
এই ধরনের মোজা অবশ্যই চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ রোগীর চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসক পরামর্শ দিলেই কেবল এটি ব্যবহার করা যাবে।
ওজন ব্যবস্থাপনা
যদিও লাইপেডিমা নিজেই একটি রোগ, তবুও এ রোগের একটা বিশাল অংশের রোগীরা এমনিতে আগে থেকেই অনেক মোটা হয়। এবং আরো ওজন বৃদ্ধি হলে লাইপেডিমার খারাপ অবস্থা হয়।
যদিও ওজন কমানো এই রোগের চিকিৎসায় প্রাধান্য পায় না। এটা স্থূলতা বা অন্য গুরুতর রোগের রোগীদের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা উচিত।
মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা
সৌন্দর্যের যে প্রচলিত আদর্শ সেটি অনুযায়ী অনেক রোগীরই তাদের শরীর, শারীরিক গঠন নিয়ে সামাজিক চাপের কারণে হতাশায় ভুগতে পারে।
অন্যান্য রোগীরাও অতি মাত্রায় মানসিক চাপে ভুগতে পারে। যেটা ব্যথার উপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
কোন রোগীরা এই মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে উপকৃত হতে পারে সেটা চিহ্নিত করা স্বাস্থ্যসেবা দানকারী চিকিৎসকদের উপর নির্ভর করে।
পুষ্টি
এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করা জরুরি।
একই সাথে তাদের খাদ্যাভ্যাসের প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রদাহজনক ও প্রদাহবিরোধী প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে তাদের।
একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারার জন্য এক্ষেত্রে পুষ্টিবিদদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ স্বাস্থ্যসম্মত খাবারের পছন্দের জন্য দিকনির্দেশনা তারা দিয়ে থাকেন।
শেষ পর্যন্ত এই রোগ নির্ণয়ের প্রক্রিয়া খুবই জটিল।
কারণ এখনো অনেক চিকিৎসকই এই লাইপেডিমা রোগ সম্পর্কে জানেন না। অন্য রোগীদের সাথে যোগাযোগ করে অভিজ্ঞতা ভাগ করা একটি প্রথম ধাপ হতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, স্পেনে লাইপেডিমা আক্রান্ত ব্যক্তিদের সংগঠন ‘এডালাইপে’ অথবা স্প্যানিশ ফেডারেশন অফ লিম্ফেডিমা এবং লাইপেডিমা অ্যাসোসিয়েশনে মানুষ অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন।
রোগী সনাক্ত করা এবং তাদের সর্বোত্তম চিকিৎসা দেওয়ার জন্য এ রোগের কারণ এবং রোগ নির্ণয়ের জন্য অনুসন্ধান চালিয়ে যাওয়া অবশ্যই বৈজ্ঞানিকদের উপর নির্ভর করে।
ইয়োগা বা যোগব্যায়াম নিয়ে কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর
ইয়োগা প্রশিক্ষকদের মুখে একটি কথা সবসময় শোনা যায় - ইয়োগা কেবল ব্যায়াম না, এটি সাধনা। সাধারণ দৃষ্টিতে ইয়োগাকে শারীরিক ব্যায়াম বা কসরত মনে হলেও বিষয়টি প্রকৃত অর্থে সে রকম নয়। এর সাথে মানসিক যোগসূত্র প্রবল বলে মনে করেন ইয়োগা প্রশিক্ষক ও বিশেষজ্ঞরা।
এই বক্তব্যের পেছনে তাদের যুক্তি হল, ব্যায়াম মানে মোটাদাগে শরীরচর্চাকেই বোঝায়। কিন্তু ইয়োগা শুধু শরীর না, মনকেও স্থির করতে সাহায্য করে।
সেই সাথে, নিয়মিত ইয়োগা মানুষক বিভিন্ন রোগ থেকে আরোগ্য পেতেও সহায়তা করে।
এই ইয়োগা নিয়ে অনেকের কৌতুহল রয়েছে। তারা বুঝতে চান, ইয়োগা আসলে কী? জিমনেশিয়ামে ব্যায়াম করা ও ইয়োগার মাঝে মৌলিক পার্থক্য কোথায়? কিংবা ইয়োগা করলে আসলেই ওজন কমে কিনা।
প্রতিবছর ২১শে জুন বিশ্ব ইয়োগা দিবস পালন করা হয়। জাতিসংঘ কর্তৃক একটি স্বীকৃত দিবস, যার সূচনা হয়েছিল ২০১৫ সালে।
এই ১০তম ইয়োগা দিবসের প্রতিপাদ্য হল, ‘ইয়োগা ফর সেলফ অ্যান্ড সোসাইটি’, অর্থাৎ ‘নিজের ও সমাজের জন্য যোগব্যায়াম।’
ইয়োগা আসলে কী?
‘ইয়োগা’ মূলত সংস্কৃত শব্দ। বাংলায় যার অর্থ ‘যোগ’, এর অর্থ সমন্বয় সাধন করা বা গ্রন্থিভুক্ত করা।
কিন্তু কিসের সমন্বয় সাধন? বাংলাদেশি লেখক রণদীপম বসু তার ‘ইয়োগা সুস্থতায় যোগচর্চা’ বইতে এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এভাবে— দেহযন্ত্রগুলোর কর্মক্ষমতাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করে স্নায়ুতন্ত্রের পূর্ণ পরিচর্যার মাধ্যমে মনোদৈহিক সম্পর্কসূত্রগুলোকে প্রকৃতিগতভাবেই একাত্ম করাই হল সমন্বয় সাধন।
এই পুরো বিষয়টিকে যদি আরও সহজভাবে বলি, তাহলে যা দাঁড়ায়— ব্যক্তির মন ও শরীরকে শরীরচর্চার মাধ্যমে একসূত্রে গাঁথা বা যুক্ত করাকেই বলে যোগ বা ইয়োগা।
ইয়োগা আরও দু’টি নামে বহুল পরিচিত। যথা: যোগাসন ও যোগব্যায়াম।
কিন্তু “ইয়োগা'কে খণ্ডিত অর্থে শুধুমাত্র যোগ-ব্যায়াম না বলে একটি অতি বাস্তব ও প্রায়োগিক দর্শন হিসেবে দেখাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত” বলে মনে করেন লেখক রণদীপম বসু।
“যোগ-ব্যায়াম হচ্ছে তার (দর্শনের) একটা অংশ মাত্র। তাই বলা যায়, সব যোগ-ব্যায়ামই মূলত ইয়োগা, কিন্তু ইয়োগা মাত্রেই যোগ-ব্যায়াম নয়, আরও বেশি কিছু,” বইতে তিনি লেখেন।
আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে দ্বিতীয় খ্রীষ্ট শতকের মধ্যবর্তী কোনও এক সময়ে ভারতীয় আর্যঋষি পতঞ্জলিকে আধুনিক যোগশাস্ত্রের জনক বলে ধরা হয়।
তার মতে, “ইয়োগা বা যোগসাধনা প্রচলিত বা উদ্দেশ্যহীন জাগতিক কর্মপ্রবাহে নিজেকে নিয়োজিত করতে প্রয়োজনীয় সামর্থ অর্জনের লক্ষ্যে গুরুগৃহে শুধুমাত্র কিছুক্ষণ আসন বা শরীরচর্চা করা নয়। বরং তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। ইয়োগা হচ্ছে নিহিত লক্ষ্য নিয়ে দেহ মন ও আত্মশক্তিকে উৎকর্ষতায় উন্নীত করার একটি কার্যকর মাধ্যম।”
পতঞ্জলি যোগসাধনাকে মোট আটটি ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেছেন, যেগুলোর পর্যায়ক্রমিক অনুশীলন করলে একটি উন্নত জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো সম্ভব বলে তিনি প্রস্তাব করেন।
ইয়োগা’র উদ্ভব কোথায়?
রণদীপম বসু তার বইতে লিখেছেন, আনুমানিক পাঁচ হাজার বছর আগে সিন্ধু নদীর তীরবর্তী ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতায় বা তারও আগে থেকে ইয়োগার অস্তিত্ব ছিল।
এই বিষটি আরও নিশ্চিত হওয়া যায় ওই সময়ের ইয়োগা-আসনের প্রত্ন-নিদর্শন থেকে।
সেই সাথে প্রাচীন গ্রন্থ বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতার মতো শাস্ত্রীয় পুরাণগুলোতেও এর উল্লেখ আছে।
তবে এই সাধনার সূত্রপাত প্রাচীন ভারতে হলেও সময়ের বিবর্তনে এর চর্চা ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে বহুবিধ ধারায় বিভক্ত হয়ে গোটা বিশ্বে পৌঁছে গেছে। সাথে যোগ হয়েছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও সূত্র।
যেমন: জুডো, ক্যারাটে, সু, জুজুৎসু, কুংফু, মার্শাল আর্ট বা সম্মোহন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, মেডিটেশন, হিলিং, কোয়ান্টাম মেথড, যোগব্যায়াম ইত্যাদি।
আসলে এই সবকিছুরই মূল লক্ষ্য— শরীর, মন ও শক্তির মাঝে ভারসাম্য রাখা।
ইয়োগা করে কী কী লাভ হয়?
ইয়োগা প্রশিক্ষকরা বলে থাকেন, ইয়োগা করলে নানা ধরনের রোগ-বালাই থেকে নিরাপদ থাকা যায়।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা’র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক ড. পুনম খেত্রাপাল সিং-এর ডব্লিউএইচও-তে প্রকাশিত একটি নিবন্ধেও এ বিষয়টির উল্লেখ আছে।
তিনি লেখেন, “ইয়োগা অনুশীলন করলে দেহ ও মন, এমনকি মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে এক ধরনের সংযোগ স্থাপিত হয়। এটি মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা অর্জনে সাহায্য করে।”
বাংলাদেশি ইয়োগা প্রশিক্ষক নায়লা বাশার জানান, ইয়োগা করলে হজমশক্তি বাড়ে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, শরীরে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং বিক্ষিপ্ত মনকে শান্ত করে তোলে।
“দেহের সব অংশে এটি কার্যকর। তবে কেউ যদি মনে করে, আজকেই ইয়োগা করে সব এচিভ করে ফেলবো, কিচ্ছু হবে না। কারণ এটা সাধনার ব্যাপার,” তিনি বলেন।
তার মতে, কেউ যদি ধৈর্য ধরে এবং মন থেকে নিয়মিত ইয়োগা অনুশীলন করেন, তাহলে তাদেরকে বিষন্নতা ততটা ছুঁতে পারে না। সেইসাথে, শরীরের বিভিন্ন ব্যথারও উপশম করা সম্ভব।
বাংলাদেশের আরেক ইয়োগা প্রশিক্ষক আনিকা রাব্বানিও একই কথা বলেন। তার ভাষায়, “আমাদের দেহ একটা মেশিনের মতো। তাকে মুভমেন্টের মাঝে রাখলে সে ভালো থাকে।”
এক্ষেত্রে তারা দু’জনই বিশেষভাবে নারী স্বাস্থ্যের কথা উল্লেখ করেছেন।
নায়লা বাশার বলেন, “মেনোপজ শুরু হলে অনেক অসুবিধা শুরু হয়, যা ছেলেরা বুঝে না। আমরা মনে করি, আমি মনে হয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। আর হয়তো কোনোদিন আমায় আমার হাজব্যান্ডের সাথে ভালো লাগবে না। আমি বাইরে যেতে পারবো না। তখন ঘুম আসে, শুয়ে বসে দিন কাটিয়ে দেই।”
কিন্তু নিয়মিত ইয়োগা অনুশীলনে সেটি অনেকাংশেই কেটে যায় ও রাগ নিয়ন্ত্রণে থাকে, তিনি জানান।
এর বাইরে অনেক নারীই আছেন, যারা পিরিয়ডের সমস্যায় ভুগেন। এ বিষয়ে এই প্রশিক্ষকের বক্তব্য, “একটু ধৈর্য্য ধরে আসনগুলো করলে পিরিয়ডের সমস্যাগুলো ঠিক হয়ে যায়, ঔষধ ছাড়াই।”
এর বাইরে নিয়মিত এই চর্চার সাথে জীবন-যাপন করলে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুসসহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গের কর্মক্ষমতা বাড়ে। মোট কথা, “শরীরের ইমিউন সিস্টেম অনেক স্ট্রং থাকে,” বলেন মিজ রাব্বানি।
ইয়োগা ও জিমের মাঝে প্রধান পার্থক্য কী?
আমাদের চারপাশের অনেকে ধারণা, ইয়োগা ও জিম পরস্পরের প্রতিপক্ষ। কিন্তু বিষয়টি আদতে তেমন?
ইয়োগা প্রশিক্ষকদের মতে, একদমই না। বরং, এই দু’টোকেই পাশাপাশি করার পরামর্শ দেন তারা।
তবে ইয়োগা ও জিমের কিছু সুবিধা-অসুবিধা আছে। জিম করলে দ্রুত ওজন ঝরিয়ে ফেলা যায়। “কিন্তু জিম আপনার শরীরকে যত তাড়াতাড়ি কমাবে, তত তাড়াতাড়ি ফ্যাটও করবে। ইয়োগা ছেড়ে দিলে মোটা হয় না,” বলেন মিজ বাশার।
জিমের পাশাপাশি ইয়োগাও করা উচিৎ উল্লেখ করে তিনি বলেন, ইগোয়া মনের শান্তি আনে এবং “ফিটনেস ও গ্লোয়িং ফেইস” ধরে রাখতে সাহায্য করে।
তবে মিজ রাব্বানি বলেন, “জিম ও ইয়োগা, দু’টোই শরীরের জন্য ভালো। কারণ একটি জিনিস করতে করতে শরীর অভ্যস্ত হয়ে যায়। শরীর সাড়া দেয় না।”
“নারীদের বয়স চল্লিশের বেশি হলে মাংসপেশী ক্ষয় হওয়া শুরু হয়। মেনোপজে গেলে হাড়ের ঘনত্ব কমে যায় এবং আরও বেশি ‘মাসল লস হয়’। সেজন্য মেয়েদের জন্য জিম করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এতে আমাদের হাড় মজবুত থাকে,” তিনি যোগ করেন।
তবে জিমের ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা আছে। অনেকে আছেন, যারা হার্টের রোগী। তাদের জন্য জিমের ভারী ব্যায়াম করাটা হিতে বিপরীত হতে পারে।
“সেজন্য সবার জন্য জিম না। জিমে লাফালাফি করতে গেলে হার্টে চাপ দেয়। কিন্তু ইয়োগা একটু ধীর, স্থির গতি মেনে করা হয় বলে এটা তাদের জন্য ভালো,” বলেন মিজ বাশার।
ইয়োগা’র কোনও বয়স বা সময় আছে?
১০ বছর বয়সী শিশু থেকে শুরু করে পঞ্চাশোর্ধ নারী-পুরুষ, কেউ চাইলেই ইয়োগা শুরু করতে পারেন।
ইয়োগা শুরু করার জন্য যা লাগে, তা হল- ইচ্ছাশক্তি, ধৈর্য, অধ্যাবসায় ও একাগ্রতা।
দৈনিক এক ঘণ্টা করে ইয়োগা করা শরীরের জন্য ভালো এবং ভোরবেলার ইয়োগা খুব বেশি উপকারী।
“ঘরের মাঝে ইয়োগা না করে বাইরে করা ভালো, এটা প্রাকৃতিক। সকালের ঐ প্রাকৃতিক বাতাস মুখে লাগলে যে উপকারিতা পাওয়া যাবে, তা অন্যকিছুতে পাওয়া যাবে না,” মিজ বাশার অলেন।
কিন্তু বর্তমান সময়ে, বিশেষ করে ঢাকায় খোলা স্থানে শরীরচর্চা করাটা বেশ কঠিন। তাছাড়া, অনেকেই আছেন, যাদের সকালে অফিস থাকে এবং অফিস শেষ করে এসে বাইরে বের হতে পারেন না।
তাদের কথা ভেবে আনিকা রাব্বানি জানান, যেকোনও সময় ইয়োগা অনুশীলন করা যায়।
“কিন্তু আইডিয়ালি খালি পেটে ইয়োগা করা বেটার,” যোগ করেন তিনি।
তাদের মতে, দৈনিক একাধিকবারও ইয়োগা অনুশীলন করা যায়।
ইয়োগা করলে ওজন কমে?
ওজন কমানোর উপায় জানা নিয়ে মানুষের আগ্রহের কমতি নেই এবং অনেকে মনে করেন, ইয়োগা অনুশীলন করে ওজন কমানো যায় না।
তবে বাস্তবে এই ধারণা সঠিক নয়। ইয়োগা প্রশিক্ষক আনিকা রাব্বানি বলেন, “ইয়োগা করে ওজন কমানো যাবে। কিন্তু একটা বার্গার, এক বাটি পোলাও খেতে পারবেন না।”
“বেশি খেলে ওজন কমবে না, পাঁচ ঘণ্টা ব্যায়াম করলেও না। সেক্ষেত্রে জিম নাকি ইয়োগা, সেটার ওপর এটি নির্ভর করবে না। ওজন কমানো নির্ভর করে ৭০% ডায়েট, ৩০% ব্যায়ামের ওপর,” তিনি বলেন।
এ বিষয়ে নায়লা বাশারও বলেন যে “বাইরে পোলাও খেয়ে যদি বলে ওজন কমছে না, তাহলে লাভ নাই। ইয়োগার জন্য শ্রম দিতে হয়, ইয়োগা জিমের থেকে টাফ।”
তিনি মনে করেন, কেউ যদি ইয়োগা অনুশীলনের মাধ্যমে ওজন কমাতে চায়, তাহলে তাকে অন্তত ছয় মাসের লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হবে এবং সেক্ষেত্রে সুষম ও পরিমাণমাফিক খাবার খুব গুরুত্বপূর্ণ।
ইয়োগা’র জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ?
অনেকে সময়ের অভাবে বা টাকার কথা বিবেচনা করে ইয়োগাশালায় গিয়ে ইয়োগা করেন না।
তারা হয় ইউটিউব দেখে দেখে একা একা ইয়োগা করেন। অথবা, অনলাইনে কোনও ইয়োগা সেন্টারের সাথে জুমে সেশন করেন।
কিন্তু এর কোনোটাতেই খুব বেশি মাত্রায় উপকার হয় না। ইয়োগা প্রশিক্ষকরা বলেন, ইয়োগা আসলে গুরুমুখী শিক্ষা।
অনেকটা ঐ নাচ শেখার মতো। একবার আয়ত্বে এসে গেলে একা একা ঘরে বসে অনুশীলন করা যায়।
ইয়োগাকে আনিকা রাব্বানি বলেন, “ইয়োগা গুরু-শিষ্য পরম্পরা।”
“একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধায়নে থেকে ইয়োগা শেখা উচিৎ। নিজে নিজে ইউটিউব দেখে ইয়োগা শেখা হয় না। আমি আমার জুমের শিক্ষার্থীদের বলি, ইয়োগা শেখা হচ্ছে না,” তিনি যোগ করেন।
“আমি এনাটমি শিখেছি। ফিমেল পেলভিস যে কতটা জটিল, সেটাও শিখেছি। এগুলো যদি ঠিকভাবে না বুঝে, তাহলে সমস্যা হয়।”
তিনি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেন এভাবে, “একজন গর্ভবতী নারী যদি প্রশিক্ষকের কাছে না গিয়ে নিজে নিজে ইউটিউব দেখে ইয়োগা করার সিদ্ধান্ত নেয়, সেক্ষেত্রে সবসময় একটা ঝুঁকি থেকে যায়।”
“স্কুলে না গিয়ে পড়াশুনা করা যায়? হয়তো করে অনেকে। কিন্তু স্কুলের মতো ইয়োগাশালাতে গিয়ে ইয়োগা শেখাটা পুরোপুরি ভিন্ন।”
ইয়োগা কিভাবে জনপ্রিয় হচ্ছে?
বিশ্বের বিভিন্ন দেশর সংস্কৃতিতে ইয়োগা অনেক আগেই মিশে গেলেও এটি আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছে খুব বেশিদিন হয়নি।
মূলত, ২০১৪ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে ২১শে জুনকে আন্তর্জাতিক ইয়োগা দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেন।
জাতিসংঘের সেই অধিবেশনে নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, “আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের এক অমূল্য উপুহার হল ইয়োগা। এটি আমাদের দেহ, মন ও কর্মকে সমন্বয় করে…এটি এমন এক পদ্ধতি, যা আমাদের শরীর ও আমাদের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য মূল্যবান।
ওই সময় যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চীনসহ মোট ১৭৫টি দেশের সমর্থনে তার দেয়া প্রস্তাবটি পাশ হয়ে যায়।
মেয়েদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে কি আইভিএফ পদ্ধতিতে সন্তান ধারণ কঠিন হয়ে যায়?
"এটি একটি অলৌকিক ঘটনা।"
সত্তর বছর বয়সী সাফিনা নামুকওয়ায়ার আইভিএফ প্রযুক্তির সাহায্যে যমজ সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর তার মুখ থেকে এই কথাটি বেরিয়ে আসে।
এর আগে ২০২২ সালের ২৯শে নভেম্বর উগান্ডার রাজধানী কাম্পালায় ওই সন্তানদের প্রসব করেন তিনি।
আফ্রিকার ওই দেশটিতে সন্তান প্রসব করা সবচেয়ে বয়স্ক নারীদের একজন সাফিনা।
ওমেন্স হসপিটাল ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড ফার্টিলিটি সেন্টারে অস্ত্রপচারের মাধ্যমে তিনি একটি মেয়ে ও একটি ছেলে সন্তানের জন্ম দেন।
ওই হাসপাতালের ফার্টিলিটি বিশেষজ্ঞ ড. এডওয়ার্ড তামালে সালি বিবিসিকে বলেছেন, সাফিনা একজন ডোনারের (দাতা) ডিম্বাণু এবং তার স্বামীর শুক্রাণুর সাহায্যে এই শিশুদের জন্ম দেন।
সাফিনা নামুকওয়ায়া তিন বছর আগে ২০২০ সালে একইভাবে একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন।
এত বয়সে মা হওয়ার একমাত্র কারণ ছিল নিঃসন্তান হওয়ায় মানুষের কটূক্তি তিনি আর নিতে পারছিলেন না।
সাফিনার মতো, ভারতের গুজরাট রাজ্যের বানাসকাঁথা জেলার বাসিন্দা গীতা বেনকেও (ছদ্মনাম) সন্তান না হওয়ায় সমাজের কাছ থেকে ব্যাপক কটূক্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল।
অবশেষে, তিনি আইভিএফ পদ্ধতি বেছে নেন এবং ২০১৬ সালে এক সন্তানের মা হন।
সন্তান না হওয়ার যন্ত্রণা দূর করছে প্রযুক্তি
গীতা বেন বিবিসির সংবাদদাতা আর দ্বিভেদিকে জানান, বিয়ের ২৫ বছর পর যখন তিনি মা হয়েছেন, তখন তার বয়স ছিল প্রায় ৪২ বছর।
এখন তিনি ও তার স্বামী মনোজ কুমার (ছদ্মনাম) তাদের সাত বছরের ছেলেকে নিয়ে খুব খুশি।
মনোজ কুমার জানান, বিয়ের এত বছর পরেও সন্তান না হওয়ায় বহুবার মানুষের কটূক্তি শুনেছেন তিনি।
এতে বিরক্ত হয়ে তারা পরিচিতজন ও আত্মীয়দের সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেন, এমনকি তাদের বিয়ের দাওয়াতে যাওয়াও বন্ধ করে দেন।
আইভিএফ পদ্ধতি কী?
ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (আইভিএফ) হচ্ছে প্রজনন সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সন্তান জন্মদানে সহায়তা করার জন্য প্রচলিত বেশ কয়েকটি কৌশলের মধ্যে একটি।
আইভিএফ পদ্ধতিতে, নারীদের ডিম্বাশয় থেকে একটি ডিম্বাণু অপসারণ করা হয় এবং পরীক্ষাগারে সেটি শুক্রাণু দিয়ে নিষিক্ত করা হয়।
নিষিক্ত ডিম্বাণু, যাকে ভ্রূণ বলা হয়, সেটিকে নারীর গর্ভে প্রবেশ করানো হয়, যেন সেটি মায়ের গর্ভে বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করতে পারে।
এই পদ্ধতিতে দম্পতিরা নিজেদের ডিম্বাণু ও শুত্রাণু ব্যবহার করতে পারে কিংবা ডোনারের ডিম্বাণু ও শুক্রাণু ব্যবহার করতে পারে।
আইভিএফ পদ্ধতি কাদের জন্য?
আইভিএফ পদ্ধতিতে বাচ্চা ধারণ শুরু হয়েছিল ১৯৭৮ সাল থেকে। সেসময় লেসলি ব্রাউন নামে একজন নারী বিশ্বে প্রথমবারের মতো টেস্টটিউব শিশুর জন্ম দেন।
গুজরাট রাজ্যের আনান্দ জেলার আকাঙ্ক্ষা হাসপাতাল ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মেডিকেল পরিচালক, ডা. নেয়না প্যাটেল, বিবিসিকে বলেছেন, "আইভিএফ পদ্ধতি মূলত নারীদের উপর প্রয়োগ করা হয়। বিশেষ করে, যেসব নারীর ফেলোপিয়ান টিউব (গর্ভনালী) সংক্রমণ বা অন্য কোনও কারণে নষ্ট হয়ে যায়।"
তিনি আরও ব্যাখ্যা করে বলেন, “এই পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা ল্যাবে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু নিষিক্ত করি। এরপর ভ্রূণ প্রস্তুত হলে, সেটি নারীর জরায়ুতে ঢোকানো হয়।"
"এই প্রযুক্তি অনেক দম্পতিকে বাবা-মা হওয়ার সুখ দিয়েছে এবং নারীদের বন্ধ্যাত্ব দূর করেছে," তিনি বলেন।
তিনি ১৯৯১ সালে প্রবর্তিত ইন্ট্রাসাইটোপ্লাজমিক স্পার্ম ইনজেকশন (আইসিএসআই) কৌশলকে এই বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায় হিসাবে বর্ণনা করেন।
তার মতে, "আইসিএসআই সেইসব দম্পতিকে বাবা-মা হতে সাহায্য করেছে, যেখানে পুরুষের শুক্রাণুর মান খুব দুর্বল ছিল এবং এ কারণে যারা সন্তান নিতে পারছিলেন না।"
"এই পদ্ধতি ডোনারের শুক্রাণুর প্রয়োজনীয়তাও দূর করেছে।" এ কারণেই মানুষ এখন বিনা দ্বিধায় একে গ্রহণ করছে।
আইভিএফ কীভাবে কাজ করে?
এই পদ্ধতি ছয়টি ধাপে সম্পন্ন হয়।
সবার আগে নারীর প্রাকৃতিক মাসিক চক্র ওষুধ দিয়ে বন্ধ করা হয়।
এরপর নারীর ডিম্বাশয়ে যেন একাধিক ডিম উৎপাদন হতে পারে, এজন্য ওষুধ দেওয়া হয়।
এই প্রক্রিয়া কতটা কাজ করছে অর্থাৎ ডিম পরিপক্ক হচ্ছে কিনা, সেটা আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যান করে পর্যবেক্ষণ করা হয়। চিকিৎসকরা প্রয়োজনীয়তা বুঝে ডিম পরিপক্ক হতে ওষুধ দিতে পারে।
নারীর যোনিপথ দিয়ে ডিম্বাশয়ের মধ্যে একটি সুই ঢুকিয়ে ডিম সংগ্রহ করা হয়।
ওই ডিমগুলোকে কয়েক দিনের জন্য শুক্রাণুর সাথে মেশানো হয় যাতে সেগুলো নিষিক্ত হতে পারে।
এরপর একটি বা দু'টি নিষিক্ত ডিম (ভ্রূণ) নারীর গর্ভে স্থাপন করা হয়।
একবার ভ্রূণ ওই নারীর গর্ভে স্থানান্তর হয়ে গেলে, দুই সপ্তাহ পর্যবেক্ষণ করা হয় যে, এই পদ্ধতি কাজ করেছে কী-না।
তারপর নিয়মিত গর্ভাবস্থা পরীক্ষা করা হয়।
আইভিএফ কোন বয়সে ভালো কাজ করবে?
আইভিএফ পদ্ধতি কতটা সফলভাবে কাজ করবে তা নির্ভর করে নারীর বয়স ও তার বন্ধ্যাত্বের কারণের উপর।
অল্পবয়সী নারীদের সফল গর্ভধারণের সম্ভাবনা বেশি। আইভিএফ পদ্ধতি সাধারণত ৪৩ বছরের বেশি বয়সী নারীদের জন্য সুপারিশ করা হয় না।
কারণ ওই বয়সের পরে সফল গর্ভাবস্থার সম্ভাবনা খুব কম থাকে বলে মনে করা হয়।
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর হেলথ অ্যান্ড কেয়ার এক্সিলেন্সের (এনআইসিই) ফার্টিলিটি নির্দেশিকা অনুযায়ী ৪৩ বছরের কম বয়সী নারীদের আইভিএফ দেয়া উচিত।
বিশেষ করে যারা দুই বছর ধরে নিয়মিত অরক্ষিত যৌন মিলনের মাধ্যমে গর্ভ ধারণের চেষ্টা করছেন।
অথবা যারা কৃত্রিমভাবে গর্ভধারণের জন্য ইন্ট্রাইউটেরাইন ইনসেমিনাইজেশন বা আইইউআই পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।
যেখানে কিনা বিশেষভাবে প্রস্তুত শুক্রাণু সরাসরি জরায়ুতে স্থাপন করা হয়।
কেউ যদি একাধিকবার এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেও সন্তান ধারণ করতে না পারেন তারা আইভিএফ পদ্ধতি বেছে নিতে পারেন।
২০১৯ সালে ব্রিটেনে আইভিএফ পদ্ধতি সফল হওয়া অর্থাৎ জীবিত সন্তান প্রসবের শতকরা হার হল:
৩৫ বছরের কম বয়সী নারীদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ
৩৫ থেকে ৩৭ বছর বয়সী নারীদের ক্ষেত্রে ২৫ শতাংশ
৩৮ থেকে ৩৯ বছর বয়সী নারীদের ক্ষেত্রে ১৯ শতাংশ
৪০ থেকে ৪২ বছর বয়সী নারীদের ক্ষেত্রে ১১ শতাংশ
৪৩ থেকে ৪৪ বছর বয়সী নারীদের ক্ষেত্রে পাঁচ শতাংশ
৪৪ বছরের বেশি বয়সী নারীদের ক্ষেত্রে চার শতাংশ
মূলত যেসব নারী তাদের নিজস্ব ডিম এবং তাদের সঙ্গীর শুক্রাণু ব্যবহার করেছে, তাদের প্রতিটি ভ্রূণ স্থানান্তরের হার পরিমাপ করে এই পরিসংখ্যান করা হয়েছে।
সেইসাথে স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা এবং চিকিৎসা চলাকালীন মদ, ধূমপান এবং ক্যাফেইন এড়িয়ে চলা আইভিএফ-এর মাধ্যমে সন্তান প্রসবের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দিতে পারে।
আইভিএফ এর ঝুঁকি
আইভিএফ সবসময় কাজ নাও করতে পারে। অর্থাৎ গর্ভাবস্থায় ভ্রূণ পরিণত নাও হতে পারে।
এক্ষেত্রে মায়ের শারীরিক সুস্থতা যেমন জরুরি, তেমনি মানসিকভাবে সজীব থাকা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
এ কারণে যাদের আইভিএফ দেওয়া হয়, তাদের এই প্রক্রিয়া চলাকালীন কাউন্সেলিং করা হয়ে থাকে।
আইভিএফ পদ্ধতি চলার সময় যেসব ওষুধ দেওয়া হয়, সেগুলোর কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রয়েছে, যেমন - হটফ্লাশ হতে পারে অর্থাৎ নারীর শরীরে গরম হলকা বয়ে যেতে পারে। সেইসাথে মাথাব্যথা হতে পারে।
আবার এই পদ্ধতিতে যারা সন্তান নেন তাদের অনেক সময় একাধিক বাচ্চা অর্থাৎ যমজ বা তিনটি শিশু প্রসব হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যা মা ও সন্তান উভয়ের জন্যই বিপজ্জনক হতে পারে।
একটি অ্যাক্টোপিক গর্ভাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, যেখানে ভ্রূণ গর্ভের পরিবর্তে ফেলোপিয়ান টিউব অর্থাৎ গর্ভনালীতে রোপণ হয়ে যেতে পারে।
এছাড়া ওভারিয়ান হাইপারস্টিমুলেশন সিন্ড্রোম (ওএইচএসএস) দেখা দিতে পারে, যেখানে আইভিএফ চলার সময় ব্যবহৃত ওষুধের প্রতি ডিম্বাশয় অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখায়।
এমপক্স কী? এটা কীভাবে ছড়ায়? এ রোগের লক্ষণগুলো কী?
আন্তর্জাতিক উদ্বেগ থেকে আফ্রিকার কিছু অংশে এমপক্সের প্রাদুর্ভাবকে জরুরি জনস্বাস্থ্য অবস্থা ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডব্লিউএইচও।
আগে মাঙ্কিপক্স নামে পরিচিত অত্যন্ত সংক্রামক এই রোগে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে অন্তত ৪৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে।
এমপক্স কী এবং এর লক্ষণগুলো কী?
গুটিবসন্তের একই গোত্রীয় ভাইরাস হলেও এমপক্স সাধারণত অনেক কম ক্ষতিকারক।
প্রথমে এটি প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু এখন এটি মানুষ থেকে মানুষেও ছড়ায়।
এই রোগে আক্রান্তদের প্রাথমিক লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে জ্বর, মাথাব্যথা, ফোলা, পিঠে এবং পেশিতে ব্যথা।
আক্রান্ত ব্যক্তির একবার জ্বর উঠলে গায়ে ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে। সাধারণত মুখ থেকে শুরু হয়ে পরে হাতের তালু এবং পায়ের তলদেশসহ শরীরের অন্যান্য অংশে তা ছড়িয়ে পড়ে।
অত্যন্ত চুলকানো বা ব্যথাদায়ক এই ফুসকুড়িগুলো পরিবর্তন হয় এবং বিভিন্ন ধাপ পেরিয়ে স্ক্যাব বা গোল গোল পুরু আস্তরে পরিণত হয়ে শেষে পড়ে যায়। এর ফলে দাগ সৃষ্টি হতে পারে।
সংক্রমণের ১৪ থেকে ২১ দিনের মধ্যে এটি নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যেতে পারে।
তবে ছোট শিশুসহ ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীর জন্য কিছু ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত মারাত্মক।
এর আক্রমণের কারণে গুরুতর ক্ষেত্রে মুখ, চোখ এবং যৌনাঙ্গসহ পুরো শরীরে ক্ষত তৈরি হতে পারে।
কোন কোন দেশে এমপক্স ছড়িয়ে পড়েছে?
গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের মতো পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকার গ্রীষ্মমন্ডলীয় রেইনফরেস্ট সমৃদ্ধ দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে এমপক্স সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।
এই অঞ্চলগুলোতে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ এতে আক্রান্ত হয় আর শত শত মানুষের মৃত্যু হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুরা।
বর্তমানে অনেকগুলো দেশে বিভিন্ন প্রাদুর্ভাব একইসঙ্গে দেখা যাচ্ছে- বিশেষ করে কঙ্গো এবং এর প্রতিবেশী দেশগুলোতে।
রোগটি সম্প্রতি বুরুন্ডি, রুয়ান্ডা, উগান্ডা এবং কেনিয়াতে দেখা গেছে যা সাধারণত সেখানে দেখা যায় না।
মোটাদাগে এমপক্সের দুটি ধরন রয়েছে - ক্লেড ১, যা সাধারণত আরও গুরুতর হয় এবং ক্লেড ২।
ক্লেড ১ ভাইরাস – কয়েক দশক ধরে কঙ্গোতে বিক্ষিপ্ত প্রাদুর্ভাবের কারণ ছিল এবং এখন ছড়িয়ে পড়া ধরনটিও এটি।
ক্লেড ১’র কিছু ধরনে প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুরা বেশি আক্রান্ত হবার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে।
গত বছরে সংক্রামিত অনেকের তুলনামূলকভাবে নতুন ও আরও গুরুতর ধরনের এমপক্স ক্লেড ১বি হওয়ায় এনিয়ে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ক্লেড ১বি সম্পর্কে অনেক কিছু জানা বাকি। তবে ধারণা করা হচ্ছে এটি সম্ভবত আগের ধরনের চেয়ে আরও সহজে ছড়িয়ে পড়তে পারে, একইসঙ্গে আরও গুরুতর রোগের কারণ হতে পারে।
আফ্রিকা সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) বলছে ২০২৪ সালের শুরু থেকে জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত সাড়ে ১৪ হাজারেরও বেশি মানুষ এমপক্সে আক্রান্ত হয়েছে আর এতে ৪৫০’রও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে।
এই সংখ্যা ২০২৩ সালের একই সময়ের তুলনায় সংক্রমণের ক্ষেত্রে ১৬০ শতাংশ এবং মৃত্যুর ক্ষেত্রে ১৯ শতাংশ বেশি।
এর আগে ২০২২ সালে এমপক্সের মৃদু ধরন ক্লেড ২’র কারণে জরুরি জনস্বাস্থ্য অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিল।
এশিয়া এবং আফ্রিকার মতো যে দেশগুলোতে সাধারণত এই ভাইরাস দেখা যায় না এমন প্রায় ১০০টি দেশে এটি ছড়িয়ে পড়ে। তবে ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলিকে টিকা দেওয়ার মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
এমপক্স কীভাবে ছড়ায়?
এমপক্স সংক্রমিত ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সম্পর্ক, সরাসরি সংস্পর্শ কিংবা আক্রান্ত ব্যক্তির কাছাকাছি এসে কথা বলা বা শ্বাস নেয়ার মতো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে এটি একজনের থেকে অন্যজনে ছড়িয়ে পড়ে।
ভাইরাসটি ফাটা চামড়া, শ্বাসতন্ত্র বা চোখ, নাক বা মুখ দিয়ে শরীরে প্রবেশ করতে পারে।
ভাইরাসে দূষিত হয়েছে এমন জিনিস যেমন বিছানা, পোশাক এবং তোয়ালে স্পর্শের মাধ্যমেও এটি ছড়াতে পারে।
বানর, ইঁদুর এবং কাঠবিড়ালির মতো কোনো প্রাণী যদি এতে সংক্রমিত হয় আর কেউ যদি ওই সংক্রমিত প্রাণীর সঙ্গে বেশি কাছাকাছি আসে তবে তিনি এতে আক্রান্ত হতে পারেন।
২০২২ সালের বৈশ্বিক প্রাদুর্ভাবের সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ে।
কঙ্গোর বর্তমান প্রাদুর্ভাবের বড় একটি কারণ আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যৌন সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ।
ছোট শিশুসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এমপক্স পাওয়া গেছে।